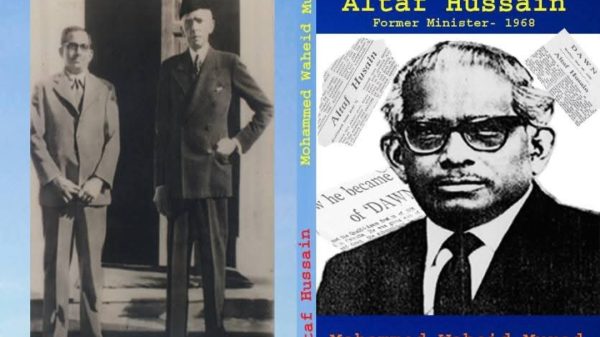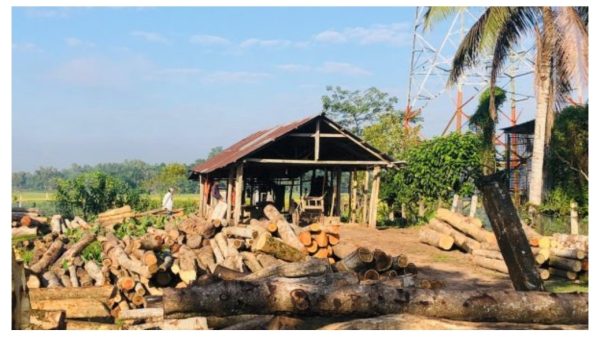৭১ এর স্মৃতি – কুলাউড়া-সৈয়দ শাকিল আহাদ
- প্রকাশিত: শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
- ৮৭ বার পড়া হয়েছে


৭১ এর স্মৃতি – ১ সৈয়দ শাকিল আহাদ
১৯৭১ সালে আমি অনেক ছোট , তবে কয়েকটি ঘটনা এত স্পষ্ট মনে আছে যা স্মৃতিতে দাগ কেটে আছে ।আমি তখন নানা বাড়ীতে সিলেট জেলার অন্তর্গত , বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার ঊছলাপারা এলাকায় ,কুলাউড়া শহরের দক্ষিন দিকে স্কুল চৌমুহনী থেকে শুরু করে উত্তরে রেলক্রসিং পর্যন্ত এক রাস্তার শহর কুলাউড়া ,তার ঠিক মাঝামাঝি তেই আমাদের ঐ নানাবাড়ী , বিরাট দীঘিওয়ালা ঐতিহ্য মন্ডিত খান বাহাদুর মৌলভী আমজদ আলীর বাড়ি । বাড়ীর পূর্ব পাশ্বেই বড় রাস্তা , রাস্তার একপাশ্বে শহরের একমাত্র ফুটবল খেলার মাঠ অন্যপাশ্বে আমাদের বাড়ি ।
১৯৭১ সালে মার্চে ঢাকায় গন্ডোগোল শুরু হয়, ঢাকাতে পাকিস্তানি মিলিটারীদের হামলায় জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল , নিরাপদ মনে না হওয়াতে আত্বীয় স্বজনেরা গ্রামের বাড়ীতে নিরাপদ মনে করেই ছুটে আসছিলেন প্রত্যন্ত অন্চল গুলোতে ,যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল ট্রেন , ঢাকার সাথে যোগাযোগ হতো ঐ মেইল ট্রেনের মাধ্যমে , হাতে গোনা কয়েকটি টেলিফোন ও ছিল ,সবাই তখন তাজা খবর পেতেন রেডিওর বদৌলতে , এবং ঢাকা থেকে আসা ট্রেন যাত্রীদের মাধ্যমে ।
তা ছাড়া রেডিও ছিলই অন্যতম সর্বশেষ খবর পাওয়ার বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম ।
আমাদের বাড়িতেও একটি রেডিও ছিল , তা দিয়েই সবাই জানতে পারতাম দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা ।বাড়ির সামনে বড় রাস্তা হওয়াতে রাসতায় চলাচল রত যানবাহনের কথা ও মনে আছে ,কুলাউড়া মৌলভীবাজার সড়ক পথে বাস চলাচল করতো , এবং কুলাউড়া থেকে জুড়ি হয়ে বড়লেখা বাড়ইপাড়া সড়কেও দু একটি বাস চলাচল করতো তা ও দিনের আলোতে , সন্ধার পর সড়কে তেমন একটা গাড়ী চলাচল করতে দেখা যেতো না , রেলওয়ে জংশন হওয়াতে কুলাউড়ার গুরুত্ব ছিল অনেক , সিলেট আখাউড়া রেল লাইন ছাড়া ও কুলাউড়া থেকে একটি রেল পথ ,দক্ষিন ভাগ , কাঁঠালতলি , ফুলতলা, লাতু , শাহবাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তখন ঐ পথে ট্রেনই ছিল একমাত্র বাহন , বর্তমানে রাস্তাঘাট উন্নত হওয়াতে সড়কপথে যোগাযোগ সহজ তাই ট্রেনের গুরুত্ব কমে গিয়েছে ।
স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনটির কথা মে মাসের ৭ তা এ সকাল ১০ টা সাড়ে দশটা হবে ,
হটাৎ ফাঁকা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম এবং রাস্তা দিয়ে কয়েকটি জীপের আনাগোনা দেখতে পেলাম , বড় মামা এসে জানালেন সময় খুউব কম , জান বাঁচাতে চাইলে এক্ষুনি পালাতে হবে , মিলিটারীরা যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে , আর যারা অবাধ্য হচ্ছে তাদের গুলি করে মারছে , আশে পাশের সব বাড়ীঘরের লোকজনেরা যে যেভাবে পারছে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ,বুঝতে পারলাম মিলিটারীরা এসেছে , আর রক্ষা নেই, নানা জানালেন তিনি অবসর প্রাপ্ত সরকারি অফিসার , তিনি কোথাও যাবেন না ,থাকবেন তার বাড়ীতেই , নানী বললেন তিনিও যাবেন না থাকবেন বাড়ীতে তবে মৃত্যু ভয় সকলেরই ছিল ,সিদ্ধান্ত হলো , ঐ দিন আমরা ছোটরা সহ আম্মাকে নিয়ে বড়মামা , ছোটমামা , আমরা বাড়ীর পশ্চিম দিক দিয়ে মনসুর , আমতৈল , কাদিপুর, ভাগমতপুর পেকুরবাজার পেড়িয়ে ,পালিয়ে যাবো হাসিমপুর গ্রামে আমাদের এক আত্বীয় মকবুল আলী নানার বাড়ীতে । সেখানেই নিরাপদ থাকবো , ঐ মোতাবেক যাত্রার প্রস্তুতি চলছিল ।
হটাৎ খেয়াল করলাম ছোটমামা সম্ভবত দক্ষিন বাজার থেকে একটা রিক্সা নিয়ে এসেছেন , ঐ রিক্সায় করেই তিনটি ট্রাংকের ভিতর রক্ষিত বাড়ীর মুল্যবান সামগ্রী দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি নিয়ে ট্রাংক তিনটি সহ রিক্সাটি নিয়ে ছোট মামার সাথে রিক্সার পিছনে পিছনে ছুটলাম , ছোটমামা কোনদিন রিক্সা চালিয়েছেন বলে মনে হয়নি , সেদিনই টেনে টেনে নিয়ে যাচছিলেন ।মক্তদির নানার রেশন দোকানের বিপরিতের মাগুরা মুখী ইটসুরকির পথ ধরে আমাদের রিক্সাটি এগিয়ে চলছিল , বি এইচ স্কুলের সামনে আসতেই পিছন থেকে একটি খোলা জীপ এসে থামলো, জীপ চালাচছিল ছোট মামার ই এক আত্বীয় বন্ধু , সাথে আরো কয়েকজন , ওরাও মিলিটারীর ভয়ে কুলাউড়া থেকে পালাচ্ছিল , ওদের কাছ থেকেই খবর পেলাম , মিলিটারী রা কুলাউড়া হাসপাতালে অস্থায়ী ক্যাম্প করেছে , ওখানে একটি কোয়ার্টার কে ‘যমঘর ‘ বানিয়ে সেখানে সকল পুরুষদের বন্দি করে রাখছে , এবং নির্যাতন করছে ইত্যাদি ,
কে ,কোথায় যাচ্ছে বলার পর মামার অনুরোধে , আমাকে জীপে তুলে দিলো যাতে আমি ছোট মানুষ এবং আমার কষ্ট একটু কম হয় , সম্ভবত জীপে চড়ার সেটাই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা , মাটির রাস্তা দিয়ে সেই জীপটি চললো , কয়েক টি গ্রাম পেরিয়ে প্রায় চার মাইল পরে এক সময় একটি তিন রাস্তার মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিল । ঐ মামা টি ,যে কে ছিল তা আজো জানিনা , তবে তিনি আমায় বলেছিলেন ,খোকা তুমি এখানেই অপেক্ষা করো , তোমার ছোট মামা পিছনে আছে , আমরা ব্রাম্মনবাজার হয়ে টেংরা যাবো , আর তোমাদের যেতে হবে ঐ পথে ,কিছুক্ষন পরেই চলে আসবে তোমার মামা , আমি তার কথা মত নেমে পরলাম এবং অপেক্ষা করতে থাকলাম , একটি আমগাছের নিচে বসে ,অপেক্ষা তো আর শেষ হয়না , কয় ঘন্টা যে পেরিয়েছিল তা বলতে পারবো না , তবে মনে আছে অপরিচিত কৌতুহলী কিছু পথচারী আমার পরিচয় ইত্যাদি জেনেছিল , কেউ আবার তাদের বাড়িতেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল , আমি যাইনি ।
অনেক ক্ষন পর ছোট মামা আসছে না দেখে আমি সাহস করে ঐ পথ ধরেই কুলাউড়া ফেরত আসতে শুরু করলাম ।কিছুদুর আসার পর দেখলাম ছোটমামা রিক্সাটি টেনে টেনে আসছেন ভারী ঐ ট্রাংক তিনটি সহ ।
মামা ভাইগনাার মিলন হওয়াতে যেন স্বস্তির আনন্দ হয়েছিল তাৎক্ষনিক ভাবে ।
আস্তে আস্তে আমরা মামা ভাগিনা মিলে প্রায় সন্ধায় ,কাংখিত গন্তব্য হাসিমপুরের মকবুল আলী নানার বাড়ীতে পৌঁছাই , পৌঁছেই আমি কান্না কাটি শুরু করে দিয়েছিলাম । বাড়ী যাবো , বাড়ি যাবো ,আম্মার কাছে যাবো , ইত্যাদি বলে কারন আমি পালানোটা খুউব আনন্দের মনে করেই ছোট মামার সাথে কিছু না ভেবেই রওয়ানা হয়েছিলাম ।পালানোর মানে কি এবং তা যে অনেক কষ্টের সেটা বুঝতে পারিনি তখন আমার বয়স মাত্র ৫ বছর , ঐ টুকু শিশুর তো কিছুই বোঝার কথা নয় ।তবে হাসিমপুরের মামা খালারা আমাকে আদর সোহাগ দিয়ে আপন করে নিয়ে ছিলেন বলে পরবর্তীতে তেমন কষ্ট হয়নি ।
চলছিল দিনগুলি আনন্দেই ।কয়েকদিন পরে কাউকে না জানিয়ে একা একা হাটতে হাটতে ঐ মাটির সড়ক দিয়ে কুলাউড়ার উদ্দেশ্য রওয়ানা দেই , কিছুদুর পাড়ি দিয়ে কাদিপুর গ্রাম পেরিয়ে পেকুর বাজার এসে রাস্তা হারিয়ে কাঁদতে থাকি , তখন ঐ বাজারে আমি কে ? কোথায় যাবো ? ঐখানে কিভাবে এলাম ? এত লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি সঠিক জবাব দিতে পারি নাই , শুধু বলছিলাম , কুলাউড়া যাবো , সেখানে কেউ একজন হিন্দু ভাল লোক বুঝতে পেরেছিল যে আমি হারিয়ে গেছি , তাই আমাকে যতদুর মনে পরে জিলাপি , পানি খাইয়ে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল । এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি ।
সন্ধায় ঘুম থেকে উঠে দেখি মকবুল আলী নানা , আমাকে খুঁজে বের করে পেয়েছেন এবং ঐ বাড়ীর সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন ।
ভীষন ক্ষেপে ছিলেন আমার প্রতি , বলেছিলেন , তোমার মাকে দেখার জন্য ইচ্ছে হচ্ছিল তো আমাকে বলতে পারতে , আমি তোমাকে নিয়ে যেতাম তোমার মায়ের কাছে , এভাবে না জানিয়ে কি কেউ একা একা যায় ? আজ যদি ছেলেধরারা তোমাকে ধরে নিয়ে যেতো তো কোথায় পেতাম তোমাকে ? অনেক আদর করতেন তিনি শুনেছিলাম সেদিন আমাকে না পেয়ে পুকুরে জাল ফেলেছিলেন ডুবে গেছি কিনা তা দেখার জন্য ? সেখানে সাইফুল মামা , কয়েস মামা , সুরাইয়া খালা , রাজিয়া খালা, নুর মামা,শিপলু মামা , জাকারিয়া মামা সহ সবাই আমাদেরকে তাদের সাথে এক করে নিয়ে ছিলেন , নানী ও অনেক আদর করতেন ।
মকবুল আলী নানা ছিলেন অত্যান্ত পরোপোকারী ও অতিথী বান্ধব এবং শুধু আমাদেরকে নয় উনার বাড়ীতে তখন বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবার ও আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করেছিল ।
যতদুর মনে আছে সেখানে ছিল ছকাপনের বিনষ ভুষন দেব
তিলক পুরের ধীরু বাবু সহ আরো বেশ কয়েক জন ।
কয়েক দিন পর একদিন ভোরেই ঘুন থেকে উঠে দেখি ঐ বাড়ীতে আম্মা , নানী , নানা সবাই এসেছেন । কুলাউড়াতে অবস্তা খারাপ হওয়াতে এবং আমাদের বাড়ির সামনেই সড়কের উত্তর পুর্ব পাশ্বে গার্লস স্কুলে মিলিটারীরা ক্যাম্প করাতে বাড়িঘর ফেলে সবাই হাসিমপুর চলে এসে কিছু দিন ছিলাম , পাকিস্তানিরা কুলাউড়ার ক্যাম্প ছাড়ার পর আমরা সবাই আবার উছলাপারায় চলে আসি । যুদ্ধ তখনও চলছিল ।
মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ সময়ের কথা অনেকই মনে হচ্ছে ,তবুও তখনকার সেই সহযোগীতাকারী দের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি ।ইতি মধ্যে অনেকেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন । আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাদের জান্নাত নসীব করুন ।
৭১ এর স্মৃতি —( ২)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
১৯৭১ সনে আমি ছিলাম কুলাউড়ায় ,
উছলাপাড়া খান সাহেবের বাড়ীতে ।
খান সাহেব এ এম আশরাফ আলী ছিলেন আমার নানা , নানার বাবা ছিলেন আমতৈল নিবাসী মৌলবী আমজদ আলী , মৌলবী আমজদ আলী ছিলেন তৎকালিন সময়ের , আই জি পি ( ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পোস্টেজ ) ব্রিটিশরা উনাকে খান বাহাদুর উপাধিতে ভুষিত করেছিল এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে তিনি ইংরেজদের তাবেদার হয়ে থাকবেন না তার পরও লোকেমুখে তা রয়ে যায় এবং তার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল ,সবাই তাকে খান বাহাদুরই ডাকতো ,তিনি ১৯২৩ সালে হিন্দু জমিদার ভারত চন্দ্র দাস এর কাছ থেকে জমি কিনে এই উছলাপারা এলাকায় খান সাহেবের বাড়ীটি তৈরী করেন ।
ঐ এলাকায় তিনিই প্রথম পাকা দালান ( ১৯২৩ সালে )তৈরী করেন , যা আজও কালের স্বাক্ষী বহন করে আছে , মৌলবী আমজদ আলীকেই সকলে খান সাহেব বলেই ডাকতো , পরবর্তীতে তার বড় ছেলে আমার নানাকেও এ এম আশরাফ আলীকে সবাই খান সাহেব হিসাবে জানতো , যদিও , তিনি সাব রেজিষ্টার সাহেব হিসাবেই বেশি পরিচিতি ছিল , যেহেতু পেশায় তিনি ছিলেন সাব রেজিষ্টার , কর্মপরিচালনা ও সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়েছে এবং তিনি অবসরের আগে পদোন্নতি পেয়ে জেলা রেজিষ্টার হয়েছিলেন বরিশাল জেলায় ।উনারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন ।
নানা বাড়ীর সামনে বিরাট পুকুর ও পিছনেও পুকুর ছিল ।
বলছিলাম ১৯৭১ সালের কথা ,
আমি আমি তখন নিতান্তই শিশু। তারপরেও আমার কিছু স্মৃতি মনে আছে যেগুলো সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করে। আমার স্পষ্ট খেয়াল আছে সে বছর বর্ষার সময়ে আমাদের পরিবারের সাথে আশ্রয় নিয়েছিলো
হিন্দু এক পরিবার ,তাদের কথা না বললেই নয় ,
পাকিস্তানি মিলিটারীরা এবং এই এলাকার কিছু চিন্হিত রাজাকারেরা যখন হিন্দুদের ধরে ধরে এনে নির্যাতন করতো কুলাউড়া হাসপাতালের ক্যাম্পের যমঘরে এবং কুলাউড়া গার্লস স্কুলের ক্যম্পে , পরবর্তীতে চোখ বেধে হত্যা করতো রেল লাইনের পূর্বপাশ্বে , সিগনাল পয়েন্টে নিয়ে , তখন কোন এক রাতে ,ভয়ে বাড়ীঘর , গরুছাগল , জরুরী জিনিষপত্র যেটা যেখানে ছিল তা ফেলে রেখে , তারা হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে প্রাণ বাচানোর জন্য পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে চলে এসেছিল আমাদের মুসলমান বাড়ীতে ,সম্প্রিতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন উনারা , তাদের ধারনা ছিল যে এই বাড়ীটি যেহেতু মুসলমানদের সুতরাং এই বাড়িতে আসলে কোন বিপদ হবে না , খান সাহেব অত্যান্ত ভাল লোক এবং সত্বিকার অর্থে তখন কোন বিপদই হয়নি তাদের পরিবারের । সেদিন আমি ও আমার বড় বোন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের বাড়িতে অনেক অচেনা লোক , বিস্মিত হই , তখন
এই পরিবারের সাথে এসেছিল কয়েকজন সদ্য কিশোর ও কিশোরী যাদের সাথে আমি অনেক খেলাখুলা করেছি , বড় বড় তিন ভাইয়ের কথা মনে আছে , রামব্রীজ ভাল নাম চন্দন ঘোষ বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত , সাদাব্রীজ ( বর্তমানে প্রয়াত )
ও সুন্দর ,ছোট ছোট দুইটি ভাই ও ছিল , নাম প্রবির ও সুবীর , তিনটি বোনের নামও মনে আছে , সুন্দরী, চম্পা ও মেরী ।অদের সাথে আমরা দুই ভাই বোন দৌড়ানো দৌড়ানো খেলতাম , কার আগে কে যেতে পারে ?
একদিনের ঘটনা ,আমরা খেলার ছলে মাঠ পেরিয়ে
রেল লাইন পর্যন্ত গিয়েছিলাম , তখন সাদাব্রীজ দাদা আমাদের সাথে ছিল , ওর প্রস্তাবেই রেল লাইন ধরে আমরা কজন চলে গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি ঠিক ঠাক আছে কিনা দেখার জন্য , ওদের বাড়িটা ছিল দক্ষিন দিকের নবীন চন্দ্র স্কুলের চৌরাস্তা সংলগ্ন রেল ক্রসিংয়ে পেরিয়ে যে রাস্তাটি গাজিপুর বাগানের দিকে গেছে , সেই খানেই , অর্থাৎ রেল লাইন সংলগ্ন পুর্ব দিকের বাড়িটি , সেদিন সবাই মিলে বাড়িটি দেখেও এসেছিলাম , আসার পথে গাড়ি দেখার জন্য সড়ক পথ বেছে নেই , হাফিজ সাহেবের বাড়ি ও সালাম মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি পেরিয়ে একটি উচু কালভার্ট ছিল , কালভার্ট পেরিয়েই ছিল ছত্তার মিয়ার বাড়ি , পেট্রল পাম্প , হাসিম ডাক্তার এর বাড়ি ঐ বাড়ির সামনে হ্যানিম্যান ফার্মেসি নামে একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ছিল ও তার বিপরিতে ইদ্রিস মিয়ার বাড়ি ।
সেই দিন অনেক ক্ষন পরে বাড়ি ফিরে এসে অনেক বকাও খেয়েছিলাম নানী সহ অন্যান্য মুরববী দের কাছ থেকে ,আমাদের কে কড়া শাসনে রাখতেন বড় মামা আমির আলী , ভয় দেখাতেন ,বাড়ীর পুর্বদিকে , বড় রাস্তায় যাওয়া নিষেধ ছিল আমাদের জন্য, কারন রাস্তায় মিলিটারীরা বন্দুকের নল উঁচু করে টহল দেয় , যে কোন সময় ঘটতে পারে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ,গুলি করে হত্যাও করে ফেলতে পারে ।হত্যা কি আর মেরে ফেলা কি এগুলি কি আর কিছু বুঝি ?
কে শোনে কার কথা ?
সুযোগ পেলেই ছুটতাম বড় রাস্তায় , গাড়ি ছুটতে দেখলেই ভাল লাগতো , গাড়ি ছুটতো রাস্তা দিয়ে , আমরা দৌড়াতাম পুকুর পাড় দিয়ে , বটগাছ পর্যন্ত , গাড়ি ছুটে চলে যেতো উত্তর দিকে আর আমরা উল্টা দৌড়ে ফিরে আসতাম ফটিকের ( বৈঠক খানা) সামনে ।
আমার স্পষ্ট মনে আছে আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে উত্তরদিকে থানার একটু আগেই ছিল দক্ষিন বাজার , থানার আগে যে রাস্তা পেকুর বাজার , বরম চাল ও ব্রাম্মন বাজার গিয়েছে ,একটু এগুলেই
বি ,এইচ প্রাইমারি স্কুলের যাবার পথে এক পাশে দুইটা মুদীর দোকান ছিল , একটিতে ভীর থাকতো অনেক বেশি , সেটিকে সম্ভবত সবাই মোমিনের দোকান বলতো ,তিনি ছিলেন নোয়াখালীর লোক , অনেক ভাল একজন লোক , সর্বদা সাদা পান্জাবী পরতেন ও মাথায় থাকতো সাদা কিস্তি টুপি ,যুদ্ধের সময় তিনি সমগ্র কুলাউড়ার জনগনকে যথাসাধ্য বাকিতে পন্য সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন ,
১৯৭১ সালে এই অন্চলে বিদ্যুৎ ছিল না , রাতের অন্ধকারে আলোর জন্য অন্যতম ভরসা ছিল
হারিকেন ও কুপি বাতি , যা কেরোসিন দিয়ে জ্বলতো , কেরোসিন তেলও তখন ১২ আনা আশি পয়সা সের দরে বিক্রি হতো ।সেই দক্ষিন বাজার যাবার বিপরিতে ছিল একটি গলি ঐ গলিটি দিয়ে রেলওয়ে কলোনি পেরিয়ে , রেলওয়ে ডাক্তার সাহেবের বাসা ও রেলওয়ে স্কুল পেরিয়ে রেল স্টেশনে যাবার পথটি ছিল সকলের পরিচিত স্টেশনে যেতে হলে সকলেই এই পথটি বেছে নিতেন , সেই গলির মুখে ছিল মক্তোদির মিয়ার রেশনের দোকান এবং এই দোকানের সামনেই রাস্তায় বসে বিক্রি হতো চারকোনা টিনের তবে উপরের অংশের কিছুটা কাটা পাশা পাশি রক্ষিত দুটি কেরোসিন ভরা তেলের দোকান থেকে কেরোসিন তেল , যা কুলাউড়া ও আশে পাশের বাড়ীঘরের আলো জানানোর জন্য এই দোকান থেকেই কেরোসিন নেয়া হতো বেশি ।
কুলাউড়ায় নামাজ পড়ার জন্য সবাই মসজিদে যেত ,কুলাউড়া জামে মসজিদ টি ছিল দক্ষিন বাজারের বড় মসজিদ , লম্বা পাগড়ীওয়ালা ইমাম সাহেব ছিলেন যার নাম সম্ভবত ছিল সৈয়দ ওবায়েদউললাহ ,মসজিদের পাশেই ছিল রামগোপাল ফার্মেসি ঐ বিল্ডিং এর উপরেই ছিল মুক্তিযোদধা সংগঠক জুবেদ চৌধুরীর সাহেবের অফিস , সেখানে জুবেদ চৌধুরী,আবুল চৌধুরী ,জব্বার মামা, সৈয়দ আকমল হোসেন ও সৈয়দ জামালের মত লোকেরা বসে নিয়মিত ঐ সময় কি করে মুক্তিযোদধাদের সংগঠিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতেন ।
তার উল্টা দিকেই ছিল আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি আর উত্তর বাজারের মসজিদটিও ছিল বড় সেই মসজিদ পেরিয়ে একটু সামনে গেলেই ছিল উত্তর বাজার যা প্রতিদিন বিকালে বসতো এবং পাসেই ছিল কয়েকটি দলিল লেখকের দোকান , যাদের মধ্যে হাসিমপুরের মকবুল আলি মহরী যিনি সম্পর্কে আমার নানা হন এবং যুদ্ধচলাকালিন সময়ে আমরা তার হাসিমপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম,কাদিপুরের সিতাব মহরীর নাম মনে পড়ছে , তাদের দোকানের বিপরীতেই ছিল লাল একটি বিল্ডিং “ সাব রেজিষ্টারের অফিস “একটু সামনে ই ছিল লংলা প্রেস ,এর একটু উল্টা দিকে ছিল আলাউদ্দিন হাজি নানার পরিপাটি সুন্দর বাড়ি , একটু সামনে গেলেই ছিল ডান দিকে হাসপাতাল , বহুদিন সেই হাসপাতালে ডাঃ হিসাবে ছিলেন ডা: আজহারুন্নেছা যার অকৃত্তিম স্নেহের কথা সবসময় মনে হয় এবং
ষ্টেশন রোডে ষ্টেশনের পাশে রেলওয়ে মসজিদের কথাও বেশ মনে আছে , প্রতিটি মসজিদের পাশ্বেই ছিল অযু করার জন্য পুকুর , যা এখন কোন মসজিদের সাথেই নেই ।আর দক্ষিন দিকে হাফিজ সাহেবের বাড়ির সামনে কবরস্থান সংলগ্ন আরেকটি মসজিদের কথা মনে আছে ।
কোন একদিনের কথা বিশেষ করে বার বার মনে পড়ে , সেদিন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন দাউদ এর নির্দেশে , মিলিটারীরা একটি জীপের পিছনে সিরাজুল ইসলাম সিরাজ নামের এক ছেলেকে বেধে সারা কুলাউড়া শহর ঘুরিয়েছে বার বার ,সিরাজের বাবা আবুল কালাম পাটোয়ারী চাঁদপুর থেকে এসে উত্তর বাজারে টেইলারিং দোকান খুলে সুখের সংসার চালাচ্ছিলেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বহমান যখন কুলাউড়া সফরে আসেন তখন এই সিরাজ সুরেলা কন্ঠে“ মজিব বাইয়া যাওরে “ গানটি গেয়ে বঙ্গবন্ধুর মনজয় করেন , বঙ্গবন্ধু তার গলাথেকে খুলে একটি ফুলের মালা উপহার দেন সিরাজের গলায় , এই মাল্যদানের একটি ছবি ছিল মোবারক আলির আজম বোডিং এক কাউন্টারে ,মিলিটারীরা কুলাউড়ায় এলে আজম বোডিং এ এই ছবিটি দেখে , ছবির পাত্রের খুঁজে বের করে , তাদের ধরে এনে নির্যাতন করে , তাদের কাছ থেকে মুক্তিবাহিনীর খোজ জানতে চায় ,
সিরাজ ছিল তেমনি এক নির্যাতনের স্বীকার ,
মুক্তি বাহিনীতে যারা গেছে তাদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে আসে এবং কারো কারো বাড়ি ঘরে আগুন দেয়।
প্রচুর ঘটনা রয়েছে কুলাউড়ার যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয় । ভবিষ্যতে বড় পরিষরে লেখার ইচ্ছা রাখি ।
৭১ এর স্মৃতি -২২ (কানিহাটি)
সৈয়দ শাকিল আহাদ ।।
আমার নানী ছিলেন প্রচন্ড সাহসী, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কুলাউড়ার উছলাপাড়া খান সাহেবের বাড়িতে নানা এ এম আশরাফ আলী সাহেব যখন বললেন “ আমি সরকারী অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা আমি বাড়িঘর ছেড়ে অন্যবাড়ীতে যাবো না , অন্যদেশে রিফুজী হবো না , মরতে হলে নিজের মাটিতে , নিজের দেশেই মরবো , তুমরা যদি যেতে চাও , যাও “। তিনি যান নি , সাথে নানীও নানাকে ফেলে অন্য কোথাও যাননি ।
নানীকে সর্বদা বড়াই করে বলতে শুনতাম-
“ আমি ভানু নারায়নের বংশধর ,এই তল্লাটে আমার গুষটি গাড়া ভরা , কথায় কথায় তিনি , কৌলা, ইটা,পাল্লাকান্দি,ঘরগাও,পৃথ্বিমপাশা, তরফীবাড়ী,কানিহাটি ইত্যাদিতে তার আত্বীয় জমিদার দের , চৌধুরীদের উদাহরণ দিতেন , অনেকের কথা বলতেন , ভানু নারায়নের কথা বলতেন ,তখন বুঝিনি ,কে এই ভানু নারায়ন ?
পরবর্তীতে জেনেছি , বিশেষ করে এই কুলাউড়ার একজন গবেষক মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ এর লেখা বই থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি , শ্রদ্ধা জানাই তাকে কুলাউড়ার অতীত ইতিহাস নিয়ে উনি অনেক কাজ করেছেন ।যিনি তার লেখা ‘ইতিহাসের দর্পনে কুলাউড়া”বইতে উল্লেখ করেছেন –
ভানু নারায়ন ছিলেন একজন প্রতাপশালী রাজা , তিনি এওলাতলীর কাছে রাজধানী স্থাপন করে তার নাম রাখেন “রাজনগর”।তিনি ১৫৪৪ খৃষটাব্দ থেকে ১৫৮০ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছর রাজত্ব করেন ।তার মৃত্যুর পর তার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বড় ছেলে সুবিদ নারায়ন রাজা হন ।সুবিদ নারায়ন সুশিক্ষিত , সংস্কারপন্থী ও সাহসী রাজা ছিলেন , ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য বাহাদুর রাজা সুবিদ নারায়ণকে চৌধুরী উপাধীতে ভুষিত করেন । রাজা সুবিদ নারায়ণ ১৫৮০ থেকে ১৫৯৮ খৃষটাব্দ পর্যন্ত ইটা রাজ্যের রাজা ছিলেন । তিনি ইটা রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা । পরবর্তীতে তার বংশের চৌধুরীগন বিভিন্ন এলাকায় ছরিয়ে পড়েন । এই বংশের অন্যতম ভানুগাছের করিম পুর চৌধুরী বাড়ীর কমরুল হাসান চৌধুরীর মেয়ে মনিরুন্নেছা খাতুন কুটি বিবি ই হলেন আমার নানী ।
নানীর সাথে যুদ্ধের সময় বেশ অনেক গুলো জমিদার বাড়ীতে গিয়েছি , তাদের মধ্যে অন্যতম , কানিহাটী চৌধুরী বাড়ী , এই ঐতিয্যবাহী কানিহাটী সম্পর্কে অনেক তথ্য দেওয়ার আছে , কিছু তথ্য না দিয়ে এগুতে পারছি না ।
সুদুর ইয়েমেন থেকে আগত হযরত শাহজালাল (রঃ) সিলেট জয়ের সময় তার সাথে সফরসঙ্গী ছিলেন আরো ৩৬০ জন আওলীয়া ।
তার নির্দেশে বেশ কিছু আওলিয়া ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন সিলেটের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েন ।
এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন -হযরত শাহ হেলিমউদ্দিন নারলুলী।তিনি ভারতের মধ্যপ্রদেশের মুসলমান অধ্যুস্বিত নারউলী অন্চল থেকে আগত সাথীদের একজন ।
‘ তোয়ারিখ হেলিমী ও জালালাবাদের কথা ‘ এবং ‘হযরত শাহ হেলীম উদ্দিন নারলুলী‘ নামের দুইটি বই থেকে জানা যায় ভারতের মধ্যপ্রদেশের নারলুল অন্চলের বাসিন্দা ছিলেন হযরত শাহ হেলিমউদ্দিন (রঃ) তিনি হযরত শাহ জালালের নির্দেশে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজের নিকটাত্নীয় ও সামন্ত রাজা অসম রায়ের রাজ্যে এসে হাজির হন ।অসম রাজ্যের কাছাকাছি বর্তমান ‘ অসম রায়ের বেরী’ নামক জায়গায় আস্তানা গাড়েন ।কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মধ্যে রয়েছে ,
রাজা অসম রায় খুউব বাঘ শিকার পছন্দ করতেন , একবার বাঘ শিকারের উদ্দেশ্য বহু লোক ল্ষকর সাথে নিয়ে গহীন জংগলের অনেকটা অংশে জাল দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করে বাঘ শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন ।
অনেক ক্ষন অপেক্ষা ও দিন ব্যাপী চেষ্টা করেও বাঘের দেখা না পাওয়াতে রাজা অসম রায় ভীষন
মর্মাহত হন এবং আক্ষেপরত অবস্থায় ছিলেন এমন সময় বনের মাঝথেকে দরবেশরুপী ফকির শাহ হেলীমউদ্দিন নারলুলী বেরিয়ে এসে রাজাকে বললেন ,
“ যে পশুকে রিক্ত হস্তে ধরা যেতে পারে রাজা হয়ে তুমি তাকে অস্ত্রের সাহায্যে শিকার করতে পারলেনা ?”এই কথা বলেই ফকির বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন ।কিছুক্ষন পরে খালি হাতে একটি বাঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সবার সামনে আসেন ।
পোষা কুকুরের মত বাঘকে সবার সামনে বসিয়ে বাঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন “ আর কখনও এদিকে এসোনা ।” বলে বাঘকে তাড়িয়ে দিলেন ।অসম রায় দরবেশের এহেন কান্ড দেখে অভিভুত হয়ে দরবেশকে তার রাজ্য দিতে চাইলেন ।
দরবেশ রাজ্য গ্রহনে অসম্মতি জানালে রাজা অনেক অনুনয় , বিনয় করতে থাকলে একপর্যায়ে এক তীর পরিমান জমি গ্রহন করতে সম্মত হন ।’অসম রায়ের বেরী’ নামক স্থান থেকে তীর নিঃক্ষেপ করা হইলে তীরটি অনেক দুর গিয়ে একটি গাছের মধ্যে আটকে যায় ।যে স্থানে ঐ তীরটি আটকে যায় ঐ স্থানটিই ‘তীরপাশা ‘বা ‘তেরাপাশা’ নামে খ্যাতি পায় ।
ঐ সময়ে ফকির বাবাজি বা দরবেশকে দান করা সম্পত্তির
মধ্যেই রাজা অসম রায় একটি ঘর তৈরী করে দেন যাকে ,ঐ অন্চলে ‘হুজরা’ বলা হয়ে থাকে ।
হুজুর হযরত শাহ হেলিমউদ্দিন নারলুলী (রঃ) সেই হুজরায় বসেই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী , জিকির আসগার ও ইসলাম প্রচারে মগ্ন থাকতেন ,তখন ঐ অন্চলের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মগ্রহন করতে আরাম্ভ করে সেখানে প্রতিরাতেই দরবেশের হুজরার পাশ্বে লাল লাল বাঘকে বসে থাকতে দেখা যেত ।
সংগত কারনেই ঐ এলাকাটি ‘লালবাঘ ‘নামে পরিচিতি পায় ।একদিন রাতে রাজা অসম রায় একটি প্রদীপ কে দেখেন আপন গতিতে চলতে চলতে হুজুরের হুজরায় চলে আসে এবং এখানে এসে স্থিত হয় , তিনি দরবেশ হুজুরকে আল্লাহর আরাধনায় ধ্যানমগ্ন দেখে অপেক্ষা করতে থাকেন ।দরবেশের ধ্যান ভাঙ্গলে রাজা দরবেশকে বলেন “হে মহান হুজুর ,আমি আর এই রাজ্যে থাকবোনা , আমি আজ ঘুমের মধ্যে দেখলাম আমার লক্ষ্মীর প্রদীপটাকে বেরিয়ে যেতে ,ঘুম ভাংলে দেখি সত্বিই প্রদীপটি স্বগতিতে হেটে যাচ্ছে আমার ঘর ছেড়ে , আমিও তার পিছু নেই , পিছু পিছু আসতে থাকি , এতদুর এসে আপনার আস্তানায় পৌঁছেই সেটি নিভে যায় ।আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি আমার লক্ষ্মীর প্রদীপ আজ আপনার ঘরে , আজ থেকে আপনি এই রাজ্যের রাজা , বলেই তখন তিনি ঐ দরবেশ হুজুরকে পূ্র্বে মনু নদী,পস্চিমে লাঘাটা নদী ,উত্তরে মনু নদী ও তীর পাশা এবং দক্ষিনে কৈলাশহর এই সীমানার মধ্যবর্তী স্থান সমুহকে দান করে নিজে সংসার ত্যাগী হন ।উল্লেখ্য পরবর্তীতে রাজার স্ত্রী কনক রানী ও রাজকন্যা কমলা দেবী ও ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন ।দরবেশ হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন নারলুলী (রঃ) কনক রানী ও তার মেয়ে কমলার সুন্দর সচ্ছল জীবন যাপনের জন্য কিছু জমি আলাদা করে দেন যা কনক হাটী বা কানিহাটী নামে পরিচিত । ইতিহাস ঘেটে নিশ্চিত হয়েছি কানিহাটী পরগনাটি এই কনকরানীর নামেই নামকরন করা হয়েছে ।
উল্লেখ্য হযরত শাহ হেলীমউদ্দিন নারলুলী (রঃ) তার পরিবারের কাউকে না জানিয়েই হযরত শাহাজালাল ( রঃ) এর সাথে চলে আসেন ।পরবর্তীতে তার ছেলে দৌলত মালিক পিতার সন্ধানে অসম রাজ্যের লালবাঘে এসে পিতার সাথে দেখা হবার পর তিনিও দেশের কথা ভুলে এখানেই ইসলাম ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন ।কিছুদিন পর দৌলত মালিকের সাথে কনক রানীর মেয়ে কমলার দেখা হলে তিনি তার রুপে মুগ্ধ হয়ে তার পিতার সম্মতিতে কমলা কে বিয়ে করেন । হুজুরের নির্দেশে দৌলত মালিক কনকরাণীর বাড়ির উত্তর পশ্চিমে বাড়ি তৈরী করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন ।
তাদের বংশের পরবর্তী পুরুষ সুলতানের নাম অনুসারে সুলতানপুর,ভুঁই মিয়ার নাম অনুসারে ভুইগাও ,দাউদের নাম অনুসারে দাউদপুর,হাজী মিয়ার নাম অনুসারে হাজীপুর ইত্যাদি গ্রামের নামকরন হয়েছে বলে প্রাচীন জনশ্রুতি রয়েছে ।
শাহ হেলিম উদ্দিন নারলুলী (রঃ) হাজীপুরের পরবর্তী বংশধরদের কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহন করেছেন , তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েক জনের বর্ননা দিচ্ছি ঃ-
তজম্মুল আলী চৌধুরী ছিলেন বৃটিশ আমলে ডি. সি ।
তার ছেলে ব্যারিষ্টার আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরী ছিলেন পাকিস্তান আমলে এম . এল.এ ,তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভুয়সী ভুমিকা পালন করেন , দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশ আমলে তিনি ছিলেন এম.পি ।পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গুরু দায়িত্ব পালন করেন ।
তজম্মুল আলী চৌধুরী রা ছিলেন পাঁচ ভাই , তার অপর ভাইয়ের ছেলে আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের সচীব , বিভিন্ন প্রতিষঠানের উচ্চপদে দায়িত্ব পালন এবং তত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত উপদেষ্টা ছিলেন ।একই পরিবারের আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও তুফেল হায়দার চৌধুরী ও রাষ্ট্রদুতের দায়িত্ব পালন করেন ।এই পরিবারের অন্যতম বংশধর আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী দীর্ঘদিন হাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন ।
তজম্মুল আলী চৌধুরীর অপর ভাই মকবুলুর রহমান চৌধুরীর ছেলে ছিলেন আব্দুল মান্নান চৌধুরী তার ছেলে জুনেদ চৌধুরী , মুক্তাদির চৌধুরী ও আবেদ চৌধুরী যিনি অন্যতম জিন বিজ্ঞানী হিসাবে ধানের নতুন নতুন উদ্ভাবনী গবেষনার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী বিশাল সারা ফেলেছেন ।মুক্তাদির চৌধুরী বা জুবেদ চৌধুরী ছিলেন সংগ্রামী স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যতম সংগঠক । তার ছেলেদের মধ্যে রাশেদ চৌধুরী হেশাম বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্তান করছেন এবং কুলাউড়ায় হাজীপুর সোসাইটি নামক সংগঠনের পরিচালনায় ন্যাস্ত রয়েছেন । অপর ছেলে এমদাদুল চৌধুরী তাহরাম যুক্তরাজ্যে অবস্তান করেও স্থানীয় ক্রীড়াঙ্গনে বিশাল ভুমিকা পালন করছেন , তিনি” জুবেদ চৌধুরী ফুটবল একাডেমী” গঠন করে ঝিমিয়ে পড়া কুলাউড়ার ক্রীড়াঙ্গনে গতির সন্চার করে চলেছেন , তার অপর ভাই সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত মেজর নুরুল মান্নান চৌধুরী হাজীপুর সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি একজন লেখক, কবি ও মুক্তিযুদধ গবেষক ।এই বংশের অন্যতম আত্বীয় শফিউল আলম চৌধুরী বা নাদেল চৌধুরীর নাম ও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য , তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন , এই বংশের আরো অনেক অগনিত পুরুষ এবং অনেক মেয়েরাও দেশেবিদেশে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন, আগামীতে তাদের নিয়েও আলোচনা করার আশা রাখি ।
৭১ এর স্মৃতি -পর্ব ২০ ( গাজিপুর)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কুলাউড়া শহরের প্রবেশমুখেই উছলাপারায় হাতের ডানদিকে নবীনচন্দ্র হাই স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠ এবং বামদিকে খান বাহাদুর মৌলবী আমজদ আলীর বাড়ি , বিশাল এক পুকুর নিয়ে তৈরী সেই বাড়িতেই টুক টুক করে বেড়ে উঠেছি আমি ,সেই পুকুরের পানি আজও স্বচ্ছ টলটলে , ছোটবেলায় এই পুকুরের পানি খেয়ে বড় হয়েছি ,দক্ষিন দিকে পাড়ের মাঝবরাবর গাছগাছালীর মাঝে কয়েকটি মনগাছ বা মাকালফল গাছ ও পেয়ারা গাছ ছিল ,
আজও সেখানে অর্থাৎ সেই পুকুরে মাছেরা , হাসেরা-সাঁতার কাটে ,আজও মনে আছে সেই মধুর স্মৃতি , পাড়ের গাছ গাছালী্র পাতার ভিড়ে চুপটি করে বসে থাকতো মাছরাঙ্গা ,ডানা শুকাতো পানকৌড়ি, ফিঙে দোল খেতো পেয়ারা গাছের মগডালে , দুপুরের রোদ গায়ে মেখে খোলা আকাশে উড়ে বেড়াতো চিল ,পুকুরের জলভরা বুকে সেই চিলের ছায়া ভেসে বেড়াতো আর বিষন্ন কন্ঠের ডাক মধ্যান্হের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে মনকে উদাস করে তুলতো ,শরৎ এলেই শাপলা ফুটতো,
,জৈষ্ঠ্য মাসে পশ্চিম পাড়ের আম গাছের নিচ থেকে আম কুড়ানোর সুখ আজও উপলব্ধি করি নিরবে নিভৃতে , তার পিছনেই বাড়ীর দেওয়াড়ে বিশাল বড় লাল টুকটুকে কৃষ্নচুড়ার গাছ ও সাথে তেতুল ও খেজুর গাছের অস্তিত্ব কখনই ভোলার মত নয় , আষাঢ়ে টুপটাপ ঝড়ে পড়া বৃষ্টির ফোটাগুলোকে গায়ে মেখে ঐ পুকুরে সাঁতার কেটেছি অনেক – অনেক ,
আহারে সেই বর্ষাকালের কি দারুন উপলব্ধি !!
স্মৃতিচারণমুলক লিখা লিখতে বসে যখন অনেক কিছুই মাথায়। আসে ,তখন বিষয় গুলোকে জরুরী , কম জরুরী , গুরূত্বপূর্ন , কমগুরুত্বপূর্ন মনে করে ঐ বিষয়গুলোর মাঝখান থেকে কোন একটা বিষয় বাছাই করে লিখবো ভেবে বসে আছি , অথচ মন মানছে না , কিন্তু মনকে যতই বুঝাচ্ছি কিছুতেই মানছে না ,
মনকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে ,
হটাৎ মনে হলো দ্বিধা দন্দে না থেকে একটু আগ বারিয়ে সামনে এসে কুলাউড়া শহরের দক্ষিন দিকে আগাই ।
মনটা চাইছে রবির বাজারের দিকে যেতে ,তাইতো স্কুল চৌমুহনী পর্যন্ত এসে বামে পুর্বদিকে রেলক্রসিং পাড় হয়ে কলেজ রোড ধরে
গাজিপুরের দিকে ছুটলাম ।
রেললাইনের পুর্বদিকের গ্রামগুলোর মধ্যে ,কয়েকটি গ্রাম ও এলাকার কথা বেশ বেশি মনে হচ্ছে যেমন ঃ-দানাপুর,দতরমুরি,লষ্করপুর ,
ঘাঘটিয়া , কামারকান্দি,জয়চন্ডী,রামপাশা,
দিলদারপুর,দুর্গাপুর,মিঠিপুর,আবুতালিবপুর,বেগবানপুর,গিয়াসনগর,গোপালীছড়া,মেরিনা,মীরশংকর,পাঁচপীর ,রসুলপুর,পোষাইনগর,
হরিহরপুর ,লৈয়ারহাই,গৌরীশংকর,রঙ্গীরকুল,সাদেকপুর,মীরবকসপুর,রাজাপুর,কুটাগাও ,গাজিপুর ইত্যাদি তাদের মধ্যে অন্যতম ।
কুলাউড়ায় পাক বাহিনী এসে বিভিন্ন জায়গায় আস্তানা তৈরী করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে , তাদের সাথে যুদ্ধ ও হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা , মিত্রবাহিনীর সমন্নয়ে ,তেমনি দু একটি যুদ্ধের বর্ননা না দিলেই নয় ,
আমি যু্দধকালিন ঘটে যাওয়া
ঘটনাসমুহের সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী নই , তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ননায় ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে ছি যেহেতু আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম তাই নানাজনে , নানামতে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন জাগতে পারে ,
প্রশ্ন জায়গাটা খুবই স্বাভাবিক ,তখনকার যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী কয়েকজন প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিতে ঐ ঘটনা সমুহের যতেষ্ট মিল খুঁজে পেয়ে লিখে যাচ্ছি কিছু স্মৃতি যা অনেক মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও কবি লেখকেরা তাদের লেখনিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তুলে এনেছেন ।বিশেষ ভাবে এই অন্চলের মুক্তিযুদ্ধ গবেষক তাজুল মোহাম্মদ ,মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ তাদের মধ্যে অন্যতম কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের প্রচেষটা কে ।
কুলাউড়ার আশে পাশের কিছু যুদ্ধের কথা , কিছু সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার কথা বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাদের কথা , কুলাউড়া অন্চলের সাহসী সূর্যসন্তান দের কথা ,বীরাঙ্গনাদের কথা ,অনেক বেশী মনে হচ্ছে যা বহুভাবে বিভিন্ন জনের আলোচনায় এসেছে ,
ঃ-পাকিস্তানি মিলিটারীদের উপর হামলা চালিয়েছিল কুলাউড়ার সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে ভারতে ট্রনিংপ্রাপ্ত বাঙ্গালী বীরযোদ্ধারা ,বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাতের বেলা চলতো ঐ সকল অপারেশন ।যুদ্ধের পরিকল্পনা এ আক্রমনের স্থান ঠিক করে দিতো ৪ নং সেক্টরের কর্মকর্তারা , এই কুলাউড়া তখন ৪ নং সেক্টরের আওতাধীন ছিল ঃ-
বিশিষ্ট গবেষক রফিকুল ইসলামের রচনায় গ্রন্থ “ লক্ষ্য প্রানের বিনিময়ে “র ৩১৯ নং পৃষ্টার বর্ননায় স্পষ্ট জানা যায় ঃ-
৪ নং সেক্টরের সাথে যে সব সেনা কর্মকর্তারা যুক্ত ছিলেন , তারা হলেন ঃ-
১) মেজর জেনারেল সি আর দত্ত
২)কর্নেল আব্দুর রব
৩)লেঃ কর্নেল শরিফুল হক বীর উত্তম ( অব:)
৪) স্কোয়ার্ডন লিডার নুরুল কাদির ( অবঃ)
৫) লেঃ কর্নেল খায়রুল আনাম (অব)
৬)লেঃ কর্নেল এম এ রাশেদ চৌধুরী বীর প্রতিক (অবঃ)
৭) লেঃ কর্নেল সাজ্জাদ আলি
বীর প্রতিক (অবঃ)
৮) লেঃ কর্নেল এস.এ. হেলাল উদ্দিন, পি.এস.সি (অবঃ)
৯)মেজর আব্দুল জলিল (অবঃ)
১০) লেঃ কর্নেল এ. কে.এম. জালালাবাদী
১১) লেঃ কর্নেল নিরন্জন ভট্টাচার্য
১২) মেজর জহিরুল হক ,
বীর প্রতিক (অবঃ)
১৩) মেজর ওয়াকিউজ্জামান ।
১৪) লেঃআতাউর রহমান
১৫) মেজর দোস্ত মোহাম্মদ সিকদার ( অবঃ)
১৬) লেঃ কর্নেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী
১৭) মেজর মুক্তাদির আলী
১৮) লেঃ কর্নেল চন্দ্র কান্ত দাস
১৯) লেঃ কর্নেল জীবন কানাই দাস
যুদ্ধ হয়েছিল , দত্তগ্রামে,জুড়িবাজারে,শরীফপুর ইউনিয়নের চাতলাপুরে,পৃথিমপাশা নবাববাড়ির ডাকঘরে,আলীনগর বিওপিতে ,সাগরনালে, নিশ্চিন্তপুরে ,মুরইছড়াতে,পাবই রেলসেতুতে ,দিলদারপুরে,দিলকুশা চা বাগান এলাকায়,মনু নদীর উপর পল্কী ব্রিজ এলাকায়,ফুলতলা বাজারে,কর্মধা ইউনিয়নের কালাইগীরি ক্যাম্পে ,গাজিপুর চা বাগান সহ উল্লেখ যোগ্য স্থানে।
বিখ্যাত সেই গাজীপুরের যুদ্ধ ছিল তেমনি একটি স্বরনীয় যুদ্ধ যা
১৯ ৭১ সালের ৪ এবং ৫ ডিসেম্বর
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পরিচালিত একটি সামরিক অভিযান।
এটি সংঘটিত হয়েছিল কুলাউড়ার কাছে গাজীপুর টি ষ্টেটে।
যেটি পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট জেলায় অবস্থিত।
অগ্রসরমান মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের উপর আক্রমণ করেছিলো।
কেউ কেউ এই যুদ্ধকে সিলেটের যুদ্ধ নামেও পরিচিতি দিয়েছেন ।
এই যুদ্ধে ১১ জন নিহত হয়েছিল, ৬১ আহত হয়েছিল ।
উল্লেখ্য ২৭ নভেম্বর ১৯৭১ বিকালে ৪/৫ গোরখা রাইফেলস কদমতলার দিকে অগ্রসর হয়।
এটি পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট বিভাগের সীমান্তের কাছাকাছি কুলাউড়া -মৌলভীবাজার সেক্টরের উল্টোদিকে অবস্থিত।
এর আগে এই এলাকা দখলের জন্য ছোট ছোট অনেক যুদ্ধ ও আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৮ম মাউন্টেইন ডিভিশনের উল্টোদিকে ছিল ৫৯ তম মাউন্টেইন ব্রিগেড। এই এলাকাটি সীমান্ত পর্যন্ত চা বাগান ঘেরা পাহাড় দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। আরও পশ্চিমে দৃষ্টিসীমার ভেতরে আরও কিছু ছোট ছোট পাহাড় চমৎকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলো।
সেই সাথে ভারতীয় সীমান্তে নজরদারীর জন্য জায়গাটি ছিল চমৎকার।
পাহাড়গুলো ছিল কুলাউড়ার ঠিক পূর্বে এবং সিলেটের সমতল অঞ্চল এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। কুলাউড়া ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র এবং রেলপথে ধর্মনগর – গাজীপুর – মৌলভীবাজার – সিলেটের সাথে সংযুক্ত ছিল।
৫৯তম মাউন্টেইন ব্রিগেডের সাহায্যে ধর্মনগর – গাজীপুর – কুলাউড়া, ধর্মনগর – জুরি সীমান্ত পোস্টগুলোর দখল নেওয়া।
৮১তম মাউন্টেইন ব্রিগেড শমশেরনগর – ফেঞ্চুগঞ্জ – মৌলভীবাজার অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবে।
লক্ষ্য ছিল সম্মিলিত সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।
পাকিস্তানের ১৪ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ৩১৩ তম ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড মৌলভীবাজারে অবস্থান করছিল। যখন এর ৩য় ব্রিগেড আরও দক্ষিণে ভৈরব বাজার এবং আশুগঞ্জ অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল, এর ২০২ তম ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড সিলেটে চলে গিয়েছিল।
২২ বেলুচ রেজিমেন্ট সাগরনাল, গাজীপুর, কুলাউড়া এবং জুরি এলাকা অতিরিক্ত মিলিটারি ইউনিট এবং EPCAF এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছিল।
এই ব্যাটালিয়ানের একটি ইউনিট ধর্মনগর – জুরি অঞ্চল এবং কয়েকটি সীমান্ত পোষ্টে নিযুক্ত ছিল।
প্রতি সীমান্ত পোষ্টে এক প্লাটুনের বেশি সৈন্য,
সাগরনালে EPCAF,
গাজীপুরে এক ইউনিট, কুলাউড়ায় ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার এবং অবশিষ্ট সৈন্য মৌলভীবাজারে অবস্থান করছিল।
কিন্তু ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের কাছে যে সেই সময় অতিরিক্ত পরিদর্শনমূলক ব্যবস্থা এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ ছিল সেটা কারো জানা ছিল না।
ভারতীয় ৫৯ মাউন্টেইন ব্রিগেড প্রাথমিক ভাবে ৪/৫ গোর্খা রাইফেলসের যা সীমান্ত বাহিনী নামে অভিহিত তাদের সাহায্যে সাগরনাল সীমান্তের আউটপোস্ট দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করে। ৯ম রক্ষীবাহিনী জুড়ি এবং
৬ষ্ঠ রাজপুত বাহিনী গাজীপুর দখল করে কুলাউড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।
যুদ্ধ চলার কারণে ৪/৫ গোর্খা রাইফেলস বা সীমান্ত বাহিনী
৬ষ্ঠ রাজপুত বাহিনীর প্রয়োজনে নিয়োজিত ছিল।
কুলাউড়া সুরক্ষিত হওয়ার পর এই দুই বাহিনীর একত্রে কাজ করার পরিকল্পনা করে ।
গাজীপুরের ধর্মতলা – কদমতল – সাগরনাল – গাজীপুর – কুলাউড়া রোডের অনেকটা অংশ গাজীপুর চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলো এবং দক্ষিণপূর্ব দিকের উঁচু এলাকা দিয়ে গিয়েছিল।
চা গাছের সারি এই এলাকায় গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছিলো এবং এর গলিগুলো স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বেষ্টিত ছিল।
এর উত্তরের উঁচু জমি ছিল নজরদারির জন্য চমৎকার স্থান। এখানকার ব্যাঙ্কারগুলো কলা গাছ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল যা
“কেলা-কা-বাগিচা “ নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর রাত ৯ টার দিকে ৬ষ্ঠ রাজপুত বাহিনী গাজীপুর আক্রমণ করে এবং শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।
ভোরের কিছুক্ষন আগে এটি স্পষ্ট হয় যে আক্রমণটি ব্যর্থ হয়েছে এবং সাহায্য চেয়ে পাঠানোর মত সময় নেই।
এই অবস্থায় ৪/৫ গোর্খা রাইফেলসকে বা সীমান্ত বাহিনী কে ১৯৭১ সালের ৪/৫ ডিসেম্বর পরবর্তী রাতে গাজীপুর দখল অভিযানের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।
তারা ৪ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আগের রাতের আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী যে কোন দিক থেকে যে কোন রকম আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
তাদের সাহায্যের জন্য কামান প্রস্তুত ছিল। পাকিস্তানের চমৎকার সংগঠিত ২২ বেলুচ কোম্পানি গাজীপুরের কেলা-কা-বাগিচায়, স্কাউটদের সাথে, ম্যানেজারের বাংলোতে, এমএমজির কারখানায় এবং কোম্পানির সদর দফতরে এক প্লাটুন করে নিয়োজিত ছিল এবং সাথে অন্যান্য পরিদর্শনমূলক এবং সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি ছিল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নির্মাণাধীন এলাকা কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল এবং তাদের সুসজ্জিত ব্যাঙ্কার প্রস্তুত ছিল।
গোর্খা রাইফেলস বা সীমান্ত বাহিনী পর্যায়ক্রমিক ভাবে ডেল্টা কোম্পানির সাহায্যে “কেলা-কা-বাগিচা,”
আলফা কোম্পানির সাহায্যে ম্যানেজারের বাংলো,
ব্রাভো এবং চার্লি কোম্পানির সাহায্যে কারখানা অঞ্চল দখলের পরিকল্পনা করে ।
সিও টু ,শ্যাম কেলকারকে
বি এবং সি কোম্পানি পরিচালিত কারখানা আক্রমণের প্রধান কমান্ডার করা হয়েছিল।
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিল ডেল্টা কোম্পানি। রাত ৮ টা ৩০ মিনিটের দিকে সামনের সৈন্যরা “কেলা-কা-বাগিচার” উত্তরের উঁচু জায়গায় পৌঁছায় এবং পাকিস্তানি বাহিনী কামান, এমএমজি এবং এলএমজি দিয়ে আক্রমণ করে। প্রায় ৮.৪৫ নাগাদ কোম্পানি আক্রমণ শুরু করে। একদম শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানিরা আক্রমণে সুবিধা করতে পারে এবং তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। সম্মুখ যুদ্ধে অনেকেই আহত হয়।
পরবর্তী লক্ষ্য ম্যানেজারের বাংলোর চারপাশে ব্যাঙ্কার থাকার কারণে এটি রীতিমত একটি দুর্গ হয়ে উঠে। চা গাছের সারির ফাঁক থেকে এবং কেলা-কা-বাগিচার সামনে থেকে আক্রমণ পরিচালিত হতে থাকে। রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আলফা কোম্পানির কোন খবর পাওয়া যাচ্ছিল না ফলে ব্রাভো কোম্পানির উপর ম্যানেজারের বাংলো দখলের দায়িত্ব পরে। আলফা কোম্পানি জানত না যে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ব্রাভো কম্পানিকে তাদের কাজটি দেওয়া হয়েছে।
ব্রাভো কোম্পানি যখন “কেলা-কা-বাগিচার” পাশ থেকে আক্রমণ করছিল তখন সৌভাগ্যবশত আলফা কোম্পানি একটি সঙ্কীর্ণ বাঁকের আড়ালে ছিল। ম্যানেজারের বাংলো দখলের সময় ব্রাভো কোম্পানির কমান্ডার সহ অনেকেই হতাহত হয়েছিল। অন্যদিকেও তখন সিও টু ,
মেজর শ্যাম কেলকার এর মৃত্যুতে নীরবতা বিরাজ করছিল। আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় সিও টু -মেজর শ্যাম কেলকার গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।
চা কারখানার শেষ এবং ফলাফল নির্ধারণকারী আক্রমণটি কমান্ডিং অফিসারের মৃত ব্রিগেডিয়ার এ বি হরলিকার, এমভিসি বক্তব্যে থেকে অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে ।
গাজিপুর বাগানে বেশ কয়েক বার গিয়েছি তাও স্বাধীনতার অনেক পরে হাবীব মামার বাংলোতে,তিনিও ৭১ এর অনেক পরে ঐ বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন ।তিনি হবিগঞ্জের সুরাবই সৈয়দ বাড়ির সন্তান ,হযরত সৈয়দ নাসিরুদ্দিন (রঃ)সিপাহসালার এর বংশধর এস এম হাবিব , কেউ কেউ তাকে হাসিব সাহেব বলে ডাকতো ,খুউব সুন্দর ব্যাডমিন্টন খেলতেন ৭০ এর দশকের শেষের দিকে কুলাউড়া থানার সামনে হাবিব মামার বেডমিন্টন খেলা দেখার জন্য থানার সামনে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করতাম , তার মেয়ে শাম্মী ও বেডমিন্টন খেলতো ,শাম্মী এবং ডাঃ আজহারুন্নেছা খালার মেয়ে ডলি দের একটি জুটি ছিল এরাও অত্যান্ত সাহসীকতার সাথে ডাকবাংলোর সামনে কোর্টেকাটা মাঠে বড়দের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখেছি ,
যাই হোক বলছিলাম হাবিব মামার কথা ,বড় মামা আমীর আলীর সাথে , কৌলার জুবেদ মামার সাথে সহ কুলাউড়ার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ও লোকদের সাথে ছিল তার যোগাযোগ ও উঠা বসা ,সেই সুবাদে যে কয়বার তার বাংলোতে বেড়াতে গিয়েছি তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতেন তার বাংলোর আশে পাশে কোথায় কিভাবে যুদ্ধ হয়েছে ,
এই গাজীপুরের যুদ্ধের সময়ের একজনের কথা না বললেই নয় , তিনি হচ্ছেন মুক্তি যোদ্ধা “ বীর প্রতিক আব্দুল জব্বার “
যার বাড়ি ময়মনসিংহের নান্দাইল থানায় ।
বীর প্রতিক আবদুল জব্বারের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার কপালহর গ্রামে। তার বাবার নাম ইসহাক আলী এবং মায়ের নাম সৈয়দজান বেওয়া। তার স্ত্রীর নাম আয়েশা বেগম। তাদের তিন মেয়ে, চার ছেলে।
বীর প্রতিক আবদুল জব্বার চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের অধীনে। তখন তার পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষে ভারতে যান। সেখানে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি বৃহত্তর সিলেট জেলায় যুদ্ধ করেন।
৭১ এর স্মৃতি ৩২ – (কাদিপুর ও রাউৎ গাঁও)
সৈয়দ শাকিল আহাদ ।।
আমরা বর্তমান সময়কে আধুনিক সময় বলছি , বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তির ছোয়াতে দেশ ও বিশ্ব অনেক উন্নতি সাধন করে চলেছে , এই চাকচিক্যময় স্বপ্নীল পরিস্থিতিতে ৫২ বছর আগের ঘটে যাওয়া কিছু লোমহর্ষক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ , স্মৃতিচারণ , যোগযোগের স্বল্পতার কথা স্বরণ,জ্ঞানী ও গুনী লোকদের অনুপস্থিতি ও স্থানের পরিবর্তন এদেশের আপামর জনগন এমনকি এই লেখা পাঠের দ্বারা এদেশের যেকোন স্থান থেকে বা বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে এই লেখাটি পড়ে যে কোন শ্রেণীপেশার পাঠক কিন্চিত পুলকিত হতে পারেন সেটা কোন বড় বিষয় নয় , বিষয় হচ্ছে লেখার বক্তব্য অনুধাবন করে ৭১ সালের ঘটে যাওয়া ঘটনা সমুহের অদেখা বর্ননা পড়ে মনের ভিতর মৃদু অনুভুতিতে আবেগ আপ্লুত হবেন যে কেউ এটাই স্বাভাবিক ।
বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত – বাড়িঘর , আবার দালানকোঠা তৈরি কিম্বা শিল্পায়ন ও ব্যবসার মত কেবল সম্পদ বৃদ্ধি করতে মত্ব আছেন কোন কোন বোদ্ধা তাদের সাথে টক্কর দেবার মানসিকতা নেই আমাদের কারোরই , আমরা শুধু আমাদের অহংকারের বিষয় ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছি , তাও আবার তৎকালিন সিলেট জেলার কুলাউড়া অন্চলের কথা বলে ।কুলাউড়া তখন সিলেট জেলার অন্তর্গত একটি পরিচিত থানা , রেলযোগাযোগের অন্যতম রেলওয়ে জংশন স্টেশনের একটি গুরুত্বপুর্ন স্টেশন ছিল এই কুলাউড়া থানা , পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে মৌলভীবাজার মহকুমা কে জেলায় উন্নীত করায় কুলাউড়াকে সিলেট জেলা থেকে আলাদা করে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্ভুক্ত করে থানাকে উপজেলায় রুপান্তরিত করা হয় এবং উন্নয়নের পথে পরিচালিত হয়ে কুলাউড়া এগিয়ে যেতে থাকে ।পরবর্তীতে সীমারেখা কমিয়ে জুড়িকে আলাদা উপজেলা করায় কুলাউড়ার পাঁচটি ইউনিয়ন জুড়িভুক্ত হয়ে যায় ।
এই কুলাউড়ার ইউনিয়ন সমুহ ছিল নিম্নরূপ ঃ ১) ভাটেরা
২) বরমচাল
৩) ভুকশিমইল
৪) জয়চন্ডি
৫) ব্রাম্মনবাজার
৬)কাদিপুর
৭) কুলাউড়া
৮) রাৎগাও
৯) পৃথিমপাশা
১০)টিলাগাঁও
১১) শরীফপুর
১২) কর্মধা
১৩) হাজীপুর
১৪) জায়ফরনগর
১৫) জুড়ী
১৬)গোয়ালবাড়ী
১৭) সাগরনাল
১৮) ফুলতলা
এই ইউনিয়ন সমুহের মধ্য উল্লেখযোগ্য একটি ইউনিয়ন হলো কাদিপুর , এই কাদিপুর ইউনিয়নের ডাঃ ফটিক সোমের কথা হয়তো অনেকেই ভুলতে বসেছেন ।তখন পাকিস্তানী আর্মিরা কুলাউড়া ও পৃথিমপাশাতে অবস্তান নেওয়ার পর কাদিপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ হিন্দুরা পরিবার পরিজন সহ ভারতে চলে যান কিন্তু এই কাদিপুর গ্রামের ডাঃ ফটিক সোম তিনি তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে দের ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে থেকে যান সবুজে ঘেরা নির্মল গ্রাম কাদিপুরের নিজ বাড়ীতেই ।বিপুল সহায় সম্পত্তি ও বিত্ব বৈভবের অধিকারী ডাঃ ফটিক সোম ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ মন্জুশ্রী চৌধুরীর চাচাতো ভাই । আশেপাশের গ্রামের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী রাজাকারর লোভ পরে তার সম্পত্তির উপর , রাজাকারেরা ডাঃ ফটিক সোম ও তার ভাই অযিত সোমকে ভারতীয় স্পাই আখ্যায়িত করে অভিযোগ দেয় পাক সেনা দের কাছে । তাদের ঐ অভিযোগের উপর ভিত্বি করে পাকিস্তানী আর্মিরা দুই ভাইকে ধরে নিয়ে এসে কুলাউড়া নবীনচন্দ্র হাই স্কুলের যমঘরে আটকে রাখে এবং চরম নির্যাতন করে । নির্যাতনের এক পর্যায়ে কয়েক দিন পর ভাই অযিত সোমকে ছেড়ে দেয় পাকিরা এবং ডাঃ ফটিক সোমকে নির্মম ভাবে হত্যা করে । যা স্বরন করে এখন ও অনেক বেশী ব্যাথিত করে তৎকালীন সময়ের অনেক ব্যাথাতুর কুলাউড়া বাসীর হ্রদয়কে । কাদিপুর এর অনেক মুক্তিযোদ্ধার কথা আলোচনা করার ভাবছি আগামীতে বড়পরিসরে আরো অনেকের কথা লেখার ইচ্ছা রয়েছে । চিকিৎসক হিসাবে আরো একজনের নাম এখনও অনেকের মনে আছে তিনি ছিলেন রাউৎগাও এর ডাঃ অক্ষয় কুমার চৌধুরী তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ।গ্রামের সহজ সরল লোকদের সাথে ছিল তার নিবির সখ্যতা , তার ছেলে অনুপম কান্তি চৌধুরী দেশকে শত্রুমুক্ত করার তাগিদে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে অন্যান্যদের সাথে চলে যায় ভারতে , পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পাকিদের ভয়ে নিরাপদ আস্রয় ভারতে চলে যায় । দেশের টানে এদেশের মানুষের মায়ায় থেকে যান ডাঃ অক্ষয় কুমার , ভেবেছিলেন তিনি জনগনের সেবা করেন , ডাক্তারী পেশায় আছেন বলে হয়তো তার কিছু হবে না কিন্ত তারপর ও নিস্তার মেলেনি , ২৭ শে মে ১৯৭১ সালে সকালে পাশের গ্রাম দেওগাঁও এর একজন চিন্হিত রাজাকারের নেত্বৃত্বে একদল রাজাকার তাকে পাক মেজরের তলব বলে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে । মুহুর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে ,খবর পেয়ে ছুটে আসে গ্রামবাসীরা ,তাকে ছাডিয়ে নেবার চেষ্টা করে এমন কি তখন গ্রামবাসীরা ঐ গ্রামের রাজাকারদের নেতা চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয় , তিনি সেদিন কর্নপাত করেন নি , তারা ডাঃ বাবুকে ধরে নিয়ে যায় সদপাশা স্কুলে , সারাদিন ইচ্ছামত শারীরিক নির্যাতন শেষে সন্ধার পর তাকে ব্রাস ফায়ার করে দেহ ঝাঝড়া করে ।তাকে হত্যার পর ঐ চেয়ারম্যান সাহেব তার সকল সম্পত্তি কুক্ষিগত করে ।
রাৎগাওয়ের আরো অনেক হ্রদয় বিদারক ঘটনা রয়েছে এই মুক্তিযুদধ কালিন সময়ে যা বলে শেষ করার মত সময় বে বলে মনে হয় না , তবে কিছু স্মৃতি , কিছু কথা , কিছু নাম বার বার স্বরনে আসে তেমনি ছিলেন প্রবির চন্দ্র ধর , রাধা বিনোদ প্রমুখ ,তিলাশিজুড়া গ্রামের অনেক হিন্দু পরিবার বাপদাদার ভিটাবাড়ী জমি জিরাত ছেড়ে ভিন্নদেশে আশ্রয় নিতে যান নি , বুকে সাহস নিয়ে থেকে গিয়েছিলেন , ৭১ এর কোন একদিন সকালে গ্রামের চৌকিদার একদল লোক নিয়ে এসে ঐ রাজাকার চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রবির চন্দ্র ধর, পুলিন বিহারী ধর প্রল্লাদ ধর ও তাদের এক তালতো ভাই পাশ্বের রাজনগর থানার গন্ডরী গ্রামের বিনোদ ধরকে এক সাথে ধরে নিয়ে যায় চেয়ারম্যানের অফিসে , সেখানে দীর্ঘক্ষন জেরার পর ছেড়ে দেওয়া হয় পুলিন বিহারী ও প্রহল্লাদ ধরকে ,এবং প্রবির চন্দ্র ধর ও রাধা বিনোদকে পাকিস্তানী হানাদার দের কুলাউড়ার নবীন চন্দ্র হাই স্কুল ক্যাম্প পাঠিয়ে দেওয়া হয় ।প্রবির ধরতে পাকিদের হাতে তুলে দিয়ে ঐ রাজাকার চেয়ারম্যান একদল রাজাকার বাহিনীকে সাথে নিয়ে প্রবির বাবুর বাড়ী লুট করে । উল্লেখ্য প্রবির বাবু ও বিনোদ বিহারীকে পাকিস্তানী হানাদারেরা নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে ।
ঐ সময় আরো একজনের নাম মনে হচ্ছে , তিনি হলেন মনরাজ গ্রামের ক্ষীরোদ মোহন দাসের ছেলে , হরেন্দ্র কুমার দাস । তার বাড়ীঘর এ পাকিরা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে এবং তাকে নির্মম ভাবে বেয়নেটের খোঁচায় জখম করে রবিরবাজারের কুমুদ রন্জন ডাঃ সহ আলী আমজদ স্কুলের উত্তর পশ্চিম কোনে গর্ত করে , গর্তে ফেলে চরম অত্যাচার করে হত্যা করে ।
অবর্ননীয় অত্যাচারে নিপীড়িত সাধারন দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৯৭১ সালে । গৌরবময় এই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমার তেমন উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহন বা ভুমিকা ছিল না , তা ছাড়া তখন এত ছোট বয়সে তেমন কোন অংশগ্রহন করার মত গ্রহনযোগ্য ও ছিলাম না তবে স্বাধীনতার স্বপক্ষে যারা ছিল তাদের অনেকের স্বান্নিধ্বে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল স্বাধীনতার পর আস্তে আস্তে যখন বড় হতে শুরু করি তখন অনেক কিছুই ভুলে যেতে থাকি ইদানিং সিলেট অন্চলের অনেক উল্লেখযোগ্য স্থানসমুহে বেড়ানোর সুবাদে এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সিলেট অন্চলে ভ্রমন করার বদৌলতে এবং অত্যান্ত সুন্দর এই “আমরার সিলটী আড্ডা”তে লিখতে লিখতে ৭১ এর অনেক সংগ্রামের স্মৃতি নিজের মনের মনিকোঠায় ভেসে উঠতে থাকে এবং বলা যায় তা একে একে অনেক শুভাকাংখী আত্বীয় ও বন্ধুদের অনুরোধে কিছুটা অগোছালো ভাবে লিখতে থাকি এবং ঘুরে ফিরে বার বার সেই কুলাউড়ার কথাই উঠে আসতে থাকে এবং তা ক্রমশ পাঠকদের কাছে গ্রহনযোগ্য হতে চলেছে বলে আমার বিশ্বাস ।
শত্রুমুক্ত করার জন্য জীবন ও রক্তের বিনিময়ে যারা দেশকে স্বাধীন করেছেন , মা , বাবা স্ত্রী, সন্তান এমন কি বাড়ীঘর জায়গাজমির মায়া ত্যাগকরেছিলেন সেই সকল হারিয়ে যাওয়া ত্যাগী প্রিয় মানুষদের কথা বর্তমানে কেউ আর তেমন একটা নেয় না তবে তাদের নাম এখন না নিলে পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো এই নাম গুলো শুনতে চমকে উঠতে পারে তাই তো একটু চেষ্টা করে চলেছি ।
পুরোনো স্মৃতিচারনে রং ছড়ানো ৭১ এর চর্চা সত্বিই অনেক দুরহ কাজ যা করার সাহস দেখিয়ে কতটুকু আমি সফল হবো জানিনা তবে আমার বিশ্বাস আগামী প্রজনম আমার এই লেখা পড়ে কিন্চিত পুলকিত হবে এবং তখনই হবে এই লেখার সার্থকতা।( চলবে )
“৭১ এর স্মৃতি – ১৯ ( মনসুর)
সৈয়দ শাকিল আহাদ ।
অনেক কথাই মনে হচ্ছে লিখি
কিন্তু কোনটা রেখে কোনটা লিখবো ভাবছি , তবে মুক্তিযুদধ চলাকালে উছলাপাড়াতে আমার নানা বাড়ির পশ্চিমের দেওয়াড়ে উঠলেই দেখা যেত যে গ্রাম তা হচ্ছে মনুর বা মনসুর , এই গ্রামের দক্ষিন পাশে ঈদগাহ ও গোরস্তান , উত্তর পাশে কাদিপুর যাবার রাস্তা মাঝে গাং বা খাল বা মরা গুগালী গাং , বর্ষার সময় পানি থাকতো ,শীতকালে বা শুকনা মওসুমে আইলের উপর দিয়ে হেঁটেই আসা যাওয়া করা যেতো ।এই খালটি বা গাংটি এখন মৃত এর কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই তবুও মরা গুগালী গাং এর কথা মনে আছে তাই লিখছি ।
খান সাহেব বাড়ীর পশ্চিমে বেশ কয়েকটি বাড়ি ছিল “রাইয়ত বাড়ী “, এই খান বাহাদুর আমজদ আলী সাহেব ছিলেন বৃটিশ আমলে আই জিপি ( ইন্সপেক্টর জেনারেল ওব পোস্টেজ ) বাড়ীর পশ্চিমে অনেকের বাড়ী ছিল যারা এই মুল বাড়ীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল , নানু সহ ঐ বাড়িতে তেমন একটা যাওয়া আসা হতো না বরং ওরা আসতো আমাদের বাড়িতে এবং তিনি আমাদেরকে তেমন একটা যোগাযোগ করতে ও দিতেন না তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মেরা বর্তমানে বিত্তশালী ,অসীম ক্ষমতাধর ও সমাজে প্রতাবশালী ।
ঐ বাড়ীগুলোর পরেই ছিল ধানী জমি , এবং তার পর ধানী জমি পেরুলেই গ্রাম ,
বাড়ির পশ্চিমের গ্রামগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে মনুর বা মনসুর ,
মনসুরের আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো মনুর অন্যটা বাদে মনুর , মনুর বা মনসুর এর পর যে গ্রাম গুলো আসে সেগুলো হচ্ছে ,আমতৈল , ভাগমতপুর , সাদেকপুর ,মৈন্তাম, গুপ্তগ্রাম ,তিলকপুর,কিয়াতলা,
হাসিমপুর , কাদিপুর , কৌলারশী,গোবিন্দপুর,ফরিদপুর,রফিনগর,গোপীনাথপুর ,ছকাপন,তিলকপুর,
হোসেনপুর ,,লক্ষীপুর ,উছাইল , নিংগিরাই,কাকিচার ,নয়াগাও,
অলিপুর , সুলতানপুর ,চুনঘর ,চাতলগাওয়ের একাংশ ইত্যাদি মিলে হয়তো আরও দুএকটি গ্রাম রয়েছে যা মিলে হলো কাদিপুর ইউনিয়ন।
এই কাদিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অনেক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন , যাদের বীরত্ব গাথা আমাদের ৭১ সালে ঘটে যাওয়া মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসকে সম্বৃদ্ধশালী করে রেখেছে , তেমনি একজনের কথা মনে পড়ছে ,
তিনি হলেন ,মনসুর গ্রামের ছমসুদ্দিনের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নং হচ্ছে ০৫৪০৪০২৮২ । পাকিস্তানী আর্মিরা কুলাউড়াতে এসে ক্যাম্প করার পর তিনি অন্যান্যদের সাথে গিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে এসে কর্মধা ,শিলুয়া , ফুলতলা প্রভৃতি স্থানে করেন সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহন নিয়েছিলেন ।
তা ছাড়া বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে ,আমতৈল গ্রামের মোঃ খালেদুর রব , তার পিতা ছিলেন মোঃ আব্দুর রব তিনি অত্যানত সাহসীকতার সাথে যুদ্ধের সময় তবিশেষ ভুমিকা পালন করেন । তাদের কুলাউড়ার বাসায় বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্তান করতো এবং তিনি তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন । যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীনের পর তাদের বাসা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত অস্র থানায় জমা দেওয়া হয় ।আমতৈল জন্ম নেওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদুর রবের ভাই এম এম শাহীন , সাংবাদিকতা ও পত্রিকা ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কুলাউড়ার রাজনীতির সাথে জড়িত হন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন ।প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা দের তালিকায় খালেদুর রবের নাম্বার হচ্ছে ০৫০৪০৪০৩১৬ ।
কাদিপুর ইউনিয়নের কৌলারশী বা মিনার মহল গ্রামে জন্ম নেওয়া আর এক বীর মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছেন আজির উদ্দিন । তার কথা কেউ মনে করবে কিনা জানিনা তবে , প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তার নং ঃ- ৫০৪০৪০৩৭১ বিভিন্ন কারনে এই আলোচনায় তার নাম এসে যায় , তার পিতার নাম আমির উদ্দিন ,তার ভাষ্যমতে ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর থেকেই তারা বুঝতে পারেন পাক শোষকদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সকলকে সংগ্রামে নামতে হবে এবং তখন থেকেই প্রস্তুতি নেন , মোজাহিদ সদস্য ছিলেন , শেরপুরের প্রতিরোধ ভাঙ্গার পর তার ভাই কবির উদ্দিন কে নিয়ে ভারতে চলে যান , ট্রেনিং নেন , ৪ নং সেক্টর এর অধীনে থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে যুক্ত থেকে সাহসীকতার সাথে সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন ।দুই ভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করার কারনে
কয়েক জন রাজাকারোর প্ররোচনায় তাদের বাবা আমির উদ্দিনকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানী মিলিটারীরা নির্মম ভাবে হত্যা করে ।
আমাদের উছলা পাড খান সাহেব বাড়ীর পশ্চিমের কাদিপুর ইউনিয়নের
মনুর বা মনসুর এবং বাদে মনুর বা বাদে মনসুর
গ্রামের ইতিহাস ঐতিয্য কুলাউড়ার ইতিহাসকে সম্বৃদ্ধশালী করে রেখেছে ।
যে ব্যক্তিটির নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম তিনি হচ্ছেন সিলেট অন্চলের কিংব্দন্তী “মামন্দ মনসুর” বা দেওয়ান মোহাম্মদ মনসুর , তিনি ছিলেন অত্যান্ত প্রতাপশালি জমিদার , তার পিতা দেওয়ান ইউসুফ ছিলেন ৮ নং তালুকের অধিকর্তা বা মালিক ।
তার নামঅনুসারে ইউসুফপুর বা ইছবপুর গ্রামের নামকরন করা হয়েছিল এই গ্রামটি বর্তমানে মনসুর গ্রামের সাথে একত্রিত হয়ে আছে ।
মামন্দ মনসুরের প্রপিতামহ মোহাম্মদ আনছফ বা মামন্দ আনছফ অত্যান্ত সাহসী, বলিষ্ঠ ও দুর্দান্ত দাপটি এক মহান পুরুষ ছিলেন । প্রবাদ ও জনশ্রুতি আছে তিনি সামান্য একটি ছুরি হাতে নিয়ে হিংস্র বাঘের উপর সরাসরি ঝাপিয়ে পড়তেন , লড়াই করতেন বাঘের সাথে , হার মানতো বনের হিংস্র বাঘ ,মামন্দ আনছফ নিজের জমিদারীর সীমানা নির্ধারণকল্পে উত্তর সীমানায় একটি খাল বা পরিখা খনন করান কুলাউড়া অন্চলে তখন এত জনবসতির নাম গন্ধ ছিল না , পাহাড় , জংগলে ঘেরা ছিল , বাঘ ভাল্লুক সহ বন্যপ্রাণীর আনাগোনা ছিল নিয়মিত ।তাদের পুর্বপুরুষ ছিলেন বাবা শাহজালাল (রঃ) এর অন্যতম সাথী হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী মামন্দ মনসুর হলেন তার চৌদ্দতম পুরুষ ।
ছোটবেলায় কুলাউড়ার প্রবাদ শুনেছি
লোকমুখে
বেটা কইলে মামন্দ মনসুর
আর যত পুয়া ,
হাওর কইলে হাকালুকি,
আর যত কুয়া ।
দেওয়ান মোহাম্মদ মনসুর বা মামন্দ মনসুর সম্পর্কে , তার জীবনীতে ঘটে যাওয়া কৃতকর্মের অনেক গল্প , অজানা কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে , ও বইয়ে প্রচলিত আছে ।
তার পিতা মামন্দ ইউসুফের অসুস্ততার জন্য অল্প বয়সেই তিনি জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান ।
তিনি পৃথ্বীমপাশার জমিদার গৌছ আলী খাঁর সমসাময়িক ছিলেন ।
ছোট বেলা থেকেই একটু রাগী ও জেদী স্বভাবের
ছিলেন কিন্তু জ্ঞানী এ পন্ডিত দের সম্মান করতেন । কাদিপুর ইউনিয়নের মনসুর গ্রামের বাড়ি ছাড়াও মামন্দ মনসুরের আর একটি বাড়ী ছিল কর্মধা ইউনিয়নের মনসুরপুর গ্রামে ।
উভয় গ্রামের উভয় বাড়ীই একই রকম ভাবে নয় খন্ডে বিভক্ত , কর্মধার মনসুরপুর গ্রামের বাড়ীটি “ন-খন্ডী” বাড়ী নামে পরিচিত আর কাদিপুরের বাড়িটি “মান-মনসুরের বাড়ী “ নামে পরিচিত ।
ঐ বাড়ীগুলো মাটির দেয়াল দিয়ে নয় ভাগে ভাগ করা ছিল ।মামন্দ মনসুরের কোন ছেলে সন্তান ছিল না ,
তার তিন মেয়ে ছিল যথাক্রমে নজিফা বানু , সিতারা বানু ও খতিজা বানু ।
বড় মেয়ে নজিফা বানুর বিয়ে হয়েছিল সিলেটের মজুমদারীর আহমেদ আলী মজমাদারের সাথে ।আহমেদ আলী মজমাদারের পুর্বপুরুষ ছিলেন ভারতের কৈলাশশহরের জমিদার ।
দ্বিতীয় মেয়ে সিতারা বানুর বিয়ে হয়েছিল কুলাউড়ার কৌলা গ্রামের জমিদার আব্দুল আলীর সাথে , তৃতীয় মেয়ে খতিজা বানু অবিবাহিত ছিলেন এবং বাবার বাড়ীতেই মারা যান ।
উল্লেখ্য মামন্দ মনসুরের বড় মেয়ে নফিজা বানুর দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে হয় সিলেটের মজুমদারীর মোহাম্মদ হাদী বখত মজমাদারের সাথে এবং দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয় সিলেট শহরের কুমারপারা ঝরনার পাড়ের আমার পুর্বপুরুষ সৈয়দ আব্দুল করিমের সাথে ।এই দ্বিতীয় মেয়ের অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন আশরাফ আলী মজুমদার , তার নাম অনুসারে
এই কাদিপুর ইউনিয়ন ভুক্ত মনসুর গ্রামের মুলবাড়ীর সামনে “ আশরাফিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা “ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ।
আমাদের বাড়ির পুর্বপাশ্বে ছিলেন এই মান মনসুরের অন্যতম বংশধর তপন ভাই , তপন ভাইয়ের ছোট বোন বীনার সাথে সম্প্রতি ফেসবুকের কল্যানে যোগাযোগ , তার দেয়া তথ্য মতে
৩৬০ আউলিয়া এর একজন হলেন সুদূর ইয়ামেন থেকে আসা শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী উনি প্রথম পূর্ব পুরুষ উনার ছেলে তাজউদ্দীন কুরেশি প্রথম মনসুর গ্রামে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বিয়ে করে বসবাস শুরু করেন উনার ছেলে মান মনসুর ۔۔ মান মনসুর এর ভাতিজি উনার চাচাতো বোনের বিশাল সম্পত্তি উনার সম্পত্তির সাথে সাথে পান উনার কোলে থাকা সন্তান আদিল চৌধুরী ( মান মনসুর এর যে মেয়ের বিয়ে হয়নি উনার ভাগ এর অংশ ) আদিল চৌধুরী এর মা ব্রিটিশ আমলে জমিদারি তালুক নিলাম হয় যথাক্রমে আট ও নয় তখন ওদের কাছে প্রজা হয়ে থাকতে হবে বিধায় রাতারাতি ছেলে আদিল চৌধুরী কে নিয়ে ঘাগটিয়া তে বাড়ি বানিয়ে পাড়ি জমান যার জন্য এই বাড়ি কে হাজমা বাড়ি ও বলতো লোকেরা এবং খাজনা দিতে হতো যারা তপন ভাইদের প্রজা বা রাইয়ত । এদেরকে সরকার বাড়ি ও বলতো আমরা ও ছোটবেলাতে শুনসি সরকার ও জাইরাম বলতে আদিল চৌধুরী এর দুই ছেলে সন্তান নাদির চৌধুরী ও হাশিম চৌধুরী হাশিম চৌধুরীর ছেলে সন্তান আমিনুজ্জামান চৌধুরী অর্থাৎ তপন ভাই ও বীনার আব্বার দাদা উনার তিন সন্তান দুই ছেলে মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী ও তপন ভাইয়ের দাদা কামরুজ্জামান চৌধুরী আর তাদের দাদি দাদাদের বোন ,উনার বিয়ে হয় পাথাড়ি বড়লেখা তপন ভাইয়ের আব্বা রা এক ভাই এক বোন , তার বড়ো দাদার চার ছেলে এক মেয়ে বড় জন মারা গেছেন পুলিশ হেডকোয়ার্টার এ জব করতেন ,তাদের মেজোচাচা রেলওয়ে তে জব করতেন সেজো চাচা স্কটল্যান্ড এ আছেন আর ছোট চাচা মিশিগান এ আছেন তপন ভাইরা সাত ভাই বোন
,সবার বড় ভাই শরিফুজ্জামান চৌধুরী তপন ,মেজভাই সেলিমুজ্জামান চৌধুরী ছোট ভাই অমরুজ্জামান চৌধুরী নবাব
আলী আমজাদ এর নানী আদিল চৌধুরীর মেয়ে নাম সৈয়দা অমরুন্নেসা আর এক মেয়ে কৌলা বড়ো বাড়িতে বিয়ে হইসে আতিয়া চৌধুরী দের পূর্ব জেনারেশন শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এর ফুপু আতিয়া চৌধুরী ও
নাদেল ভাইয়ের এর বাবা শামসুল আলম চৌধুরী এবং ওই বাড়ি আতিয়া বেগমের বাবা সৈয়দ বদরুল হোসাইন চৌধুরী উনার বাবা বশিরুল হোসেইন এর নামেই “বি এইচ প্রাইমারী স্কুল “নামে দক্ষিণ বাজারে একটি স্কুল আছে । আর উনার দেয়া স্কুল ঘাগটিয়ার সম্পত্তি মৌরসী সম্পত্তি
নাজিফা বানুর দেড়শো কিয়ার বা এক হাজার একর বিঘা টি গার্ডেনটি তপন ভাইদের সম্পত্তি যা ইস্পাহানি গাজীপুর এর সাথে এবং এই সম্পত্তি দখল করে ফল্স কেইস এ তপন ভায়েরা জিতেছিল কিন্তু লোকাল মাস্তান বাহিনী দিয়ে টাকা খাইয়ে তারা দখলে নিয়ে নিয়েছে ۔۔
তপন ভাইয়ের বড় চাচা মরহুম নাজিরুজ্জামান চৌধুরী
মেজো চাচা নাজিমুজ্জামান চৌধুরী
সেজো চাচা বদরুজামান চৌধুরী
ছোট চাচা ফখরুজ্জামান চৌধুরী ফকু ।
এবার কুলাউড়ার সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়ার
প্রয়োজন অনুভব করছি ,
বর্তমান কুলাউড়া উপজেলার উত্তরে ফেঞ্চুগঞ্জ ও জুড়ি উপজেলা, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে রাজনগর উপজেলা।
পাহাড়, টিলা সমতল ও জলাভূমির সমন্বয়ে কুলাউড়ার ভূমি গঠিত। এখানকার পাহাড়, টিলা গুলো বনজ সম্পদে ভরপুর। তার মধ্যে অন্যতম চা বাগান। বাংলাদেশের মোট ১৫৩টি চা বাগানের মধ্যে, কুলাউড়া উপজেলায় ১৯ টি চা বাগান রয়েছে। কুলাউড়া উপজেলায় মোট ১৭টি ইউনিয়ন ছিল। ২০০৪ সালের ২৬ আগষ্ট, ৪টি ইউনিয়ন জায়ফরনগর, গোয়ালবাড়ী, সাগরনাল ও ফুলতলাকে আলাদা করে জুড়ী উপজেলা গঠন করা হয়।বর্তমানে ১৩ টি ইউনিয়ন রয়েছে কুলাউড়াতে, সেগুলি হচ্ছে ঃ-
১)বরমচাল ইউনিয়ন
২)ভূকশিমইল ইউনিয়ন
৩)জয়চন্ডী ইউনিয়ন
৪)ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন
৫)কাদিপুর ইউনিয়ন
৬)কুলাউড়া ইউনিয়ন
৭)রাউৎগাঁও ইউনিয়ন
৮)টিলাগাঁও ইউনিয়ন
৯)শরীফপুর ইউনিয়ন
১০)পৃথিমপাশা ইউনিয়ন
১১)কর্মধা ইউনিয়ন
১২)ভাটেরা ইউনিয়ন
১৩)হাজীপুর ইউনিয়ন
কুলাউড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সর্ম্পকে প্রাচীনকালের তাম্রলিপিতে কিছু তথ্য পাওয়া যায় বলে জানা যায়।
কুশিয়ারা নদীর দক্ষিন তীরে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত,দ্বাদশ শতাব্দিতে “ইটা” নামে একটি সামন্ত রাজ্য ছিল।
“নিধিপতি শর্মা” নামে জনৈক ব্রাক্ষণ ইটা রাজ্যের রাজা ছিলেন। এক কালে এই রাজ্য
“ইটা মনুকুল” প্রদেশ নামেও অভহিত হতো।
প্রাচীন ইটারাজ্যের রাজধানী ছিল ‘ভূমিউড়া’ গ্রাম।
প্রাচীন নিদর্শন ভাটেরার তাম্র ফলকদ্বয়ের কুলাউড়া নামের কোন উল্লেখ নেই। তবে প্রাচীন একটি শ্লোকাংশে ‘‘লংলাইস্য কুলাউড়া, ইটাস্য নন্দিউড়া’’ কথাটির উল্লেখ রয়েছে।
এ থেকে বোঝা যায়, পরগণা ভিত্তিক শাসনামলে কুলাউড়া নামটি ছিল এবং ইটা পরগণা নন্দিউড়ার ন্যায়, লংলা পরগণার কুলাউড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান।
“হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী” নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মনসুর গ্রামের প্রখ্যাত দেওয়ান, মোহাম্মদ মুনসুর বা “মামন্দ মনসুরের” পিতামহ মামন্দ মনোহরের ভাই “মামন্দ কুলাঅর “ কুমার থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।
মামন্দ মনোহর ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে নিজ জমিদারির পূর্বাংশে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করে নাম রাখেন “কুলঅরার বাজার’’। কালক্রমে “কুলঅরার বাজার থেকে কুলাউড়া’’নামকরণ করা হয়েছে।কুলাউড়া নামকরনের আরো কিছু জনশ্রুতি রয়েছে তবে সঠিক তথ্যের অভাবে নামকরনের সুত্রের পক্ষে কোন গবেষকই অতীতে তোমন জোড়ালো দাবী রাখতে পারেন নাই ।
সিলেট বিভাগের অন্যান্য উপজেলোর চাইতে কুলাউড়া অনেক অগ্রসর ও উন্নত সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। অনেক কৃতি সন্তানের জন্ম এই কুলাউড়ায় যাদের দুই এক জনের কথা না বললেই নয় ,
সিলেট অঞ্চলের প্রথম দৈনিক পত্রিকা ‘বলাকা’র সম্পাদক শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি এই কুলাউড়ায় আরেক প্রখ্যাত সাংবাদিক- শ্রী গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি কুলাউড়া সদরে ।
প্রাচীনকালে কুলাউড়ার বিভিন্ন এলাকা জাহাজ ও যুদ্ধাস্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল।
সতের শতকে কুলাউড়ার
“জনার্দ্ধন কর্মকারের” খ্যাতি ও সুনাম ছিল সমগ্র উপমহাদেশব্যাপি।
জনার্দ্ধন কর্মকার ঢাকার
“কালে জমজ” (সদরঘাটের কামান বলে খ্যাত) ও “বিবি মরিয়ম “নামের লোহার দুটি কামান তৈরী করেন এবং এর ফলে কামান তৈরীর কারিগর হিসাবে ইতিহাসের খাতায় তার নাম অংকিত হয়ে আছে ,
যিনি কুলাউড়ার সন্তান । তার কোন বংশধরেরা এখন জীবিত আছেন কিনা বা থেকে থাকলে কোথায় আছেন , কেমন আছেন তা আমাদের অজানা , হয়তো এই লেখাটি পড়ে কেউ “জনার্দ্ধন কর্মকার” এর বংশধর দের তথ্য দিয়ে আমাদের কে সহায়তা করবেন । (চলবে)
৭১ এর স্মৃতি -১২
সৈয়দ শাকিল আহাদ
সংগ্রামের সময় কেমন ছিল কুলাউড়া?
দোকান পাঠ ও রাস্তা ঘাট কেমন ছিল ?
যতদুর মনে পড়ে ,এক রাস্তার শহর কুলাউড়ার উছলাপারায় আমাদের নানা ছিলেন অবসর প্রাপ্ত জেলা রেজিষ্টার জনাব এ এম আশরাফ আলী , আমি সেখানেই ছিলাম , সেই খান সাহেবের বাড়ি থেকে বের হয়ে বটগাছের নিচে এসে বড় রাস্তায় অর্থাৎ কুলাউড়া মৌলভীবাজার রোডে উঠে উত্তর দিকে এগুলেই একটু সামনে আসলে প্রথমেই ছিল আমাদের বাড়ির আর একটি রাস্তা যা ছিল মুলত চটই মামু ও সত্তার মামুর ‘ বাড়িতে যাওয়ার জন্য বড় রাস্তা থেকে আইল মার্কা রাস্তা , বৃষ্টির সময় ঐ রাস্তা কর্দমাক্ত থাকতো যা দিয়ে চলাচল অত্যান্ত দুর্বিসহ ছিল ।তার পরে খাই , ঐ খাই এর পাশে রশি টাংগানো থাকতো ,যেখানে রশি গুলো কাপর ধুয়ে শুকানোর জন্য ব্যবহৃত হতো , আরএকটু এগুলেই পশ্চিমদিকে ছিল কনা নানার বাড়ী , তিনি কাদিপুর ইউনিয়নের করণিক ছিলেন , সেটাকে কেরানী সাহেবের বাড়ি বললেই সবাই চিনতো ,কনা নানার একটি সাইকেল ছিল , মুলত সেই সাইকেলে চড়ে তিনি কাদিপুর যাওয়া আসা করতেন ,নানী ছিলেন ভীষন সুন্দরী , নাম জানতাম না বলে তাকে “সুন্দরী নানী” বলেই ডাকতাম ,কনা নানার এক ভাই ছিল নাম ‘গেদন’, গেদনের একটি ‘তরজার বেড়ার ‘ মুদির দোকান ও ছিল , গেদনকে নানা রকম অপকর্মের জন্য অনেকেই এক নামে চিনতো , মতি মিয়া নামের তাদের এক ভাগিনা গেদনের অনুপস্থিতিতে ঐ দোকানটি চালাতো ,পাশেই ছিল ছানা নামের কুলাউড়ার একমাত্র ধোপার দোকান , ছানাকে সবাই চিনতো কারন তার দায়িত্বে থাকতো ময়লা কাপর পরিষ্কার করার বিষয়টি ,তাকে সারা কুলাউড়ার অধিকাংশ লোকের কাপর ধোয়া ও ইস্ত্রির কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা যেতো, ছানা নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপর সংগ্রহ করে ধোলাই করে দুই দিন পরে সুন্দর করে ইস্ত্রি করার পর ফেরত দিয়ে আসতো , তার ইস্ত্রিটিও ছিল লোহার একটু বড়সর , কয়লা গরম করে সেটাকে উত্তপ্ত করে কাপর ইস্ত্রি করতে দেখা যেত।
কনা নানার বাসার পরেই ছিল পশু ডাক্তারখানা , এখানে একটি সুপেয় পানির চাপ কল ছিল । বিপরীতেই ছিল একমাত্র সিনেমা হল , যার নাম পুবালী সিনেমা হল , এর পাশেই স্বাধীনতার পর পরই আর একটি সিনেমা হল হয়েছিল যেটি ছিলো লিলি সিনেমা হল , পরবর্তীতে লিলি সিনেমা হলটি স্টেশন রোডে স্নানান্তরিত হয় ।একটু এগুলেই পশ্চিমে ছিল তারিণী বাবুর বাড়ী ও বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি পুকুর , রাস্তার সামনেই ছিল একটি কামারের দোকান ,ঐ খানে দাড়িয়ে লোহা গরম করা দেখতাম , ভাল লাগতো দেখতে দুই তিনজন মিলে কয়লা পুড়িয় লোহা গরম করে পিটিয়ে দা কুড়াল , খন্তি বানানো দেখতে , কামারের দোকানের পরেই ছিল বিমলদের ঝুপরি মার্কা একটি চায়ের দোকান দোকানটি খোলার ব্যবস্তা ছিল অনেক মজার, এক পাশ্বে তরজার দুই পার্ট ওয়ালা ডালা , ডালাটি একটি বাঁশ দিয়ে ঠেক দিয়ে রাখা হতো আর ফ্লোরটি ছিল মাটির , ঐ দোকানটিতে তিনটি টুল ও দুইটি উঁচু বেন্চ ছিল ,
ঐ চায়ের দোকানে চা য়ের সাথে লুচী এবং সুজীর হালুয়া ও বিক্রি হতো ,
এর পরেই ছিল মটর স্ট্যান্ড,হাতে গোনা কয়েকটি মোটর গাড়ি কুলাউড়া হতে মৌলভীবাজার রোডে চলাচল করতো, বিপরিতে অর্থাৎ পূর্বদিকে ছিলো জব্বার মিয়া নামক এক লোকের খালুয়ার ঘর বা চামরার গুদাম , ভীতরে একটি ডোবা আকৃতির পুকুর ও ছিল, যা কচুরী পানায় আবৃত থাকতো । যে পুকুরে গরুর চামরা ও মটর গাড়ির চাকা ইত্যাদি ধোওয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো , ঐ পুকুরের ভিতরে পূর্বদিকে ঘাটলা ছিল , ঘাটলাটি কালো সুন্দর ঝাঝের মত চার কোনা পাথরের দ্বারা বাধাই করা ছিল ।মটর স্ট্যান্ডের কথাটি বেশ মনে হতো ।
সম্ভবত সংগ্রামের পর পরই বা আগেও হতে পারে সেই মটর য্ট্যান্ডে আলালপুরের হাফিজ সাহেবের ছেলে ‘লেদু মিয়া’ মামার একটি চায়ের দোকান ছিল । সেখানেও ভাল চা নাস্তা পাওয়া যেতো , বিপরীতেই ছিল হাজি ইয়াকুব আলীর দালান । মোটর স্ট্যান্ডের পরই ছিল কুলাউড়া পোস্ট অফিস , পোস্ট অফিসটি ছিল অত্যান্ত্য সুন্দর , বৃটিশদের ডিজাইনে তৈরী করা সুন্দর একটি অফিস হাফ বিল্ডিং , এর পরই ছিল একটি খাই বা ডোবা , এই ডোবার পাশ দিয়ে সফাত মাস্টরের বাসা র পাশ দিয়ে দক্ষিন বাজার পেরিয়ে বি এইচ স্কুলে যাওয়া আশা করতাম ।তার পরেই ছিল কুলাউড়া জামে মসজিদ , ঐ মসজিদের ই মক্তবে ফজরের নামাজের পর ইমাম সাহেব , হুজুর সৈয়দ রাশিদ আলীর কাছে আমি ও এলাকার আশেপাশের অনেক কোমলমতি শিশু কিশোরেরা নিয়মিত আরবি পড়তাম , তিনি অনেক লম্বা ছিলেন ও পাগড়ী পড়তেন ও কাঠের খড়ম পড়তেন বলে আমরা সবাই তাকে পাগড়ী ওয়ালা হুজুর এবং কেউ কেউ খড়মঅয়ালা হুজুর ও বলতাম , উনার ছেলের নাম ছিল জুবায়েদ আলি ,মসজিদের পিছনে ছিল অজু করার জন্য ছোট্ট একটি পুকুর ,পুকুরের পশ্চিমে ছিল লাবু পালের বাসা ,তিনি পরবর্তীতে ঐ বাসা মসজিদের নিকট বিক্রয় করে অন্যত্র চলে যান ।
এই মসজিদের উন্নয়নের জন্য পথচারীদের কাছ থেকে পালা করে টাকা , মুঠির চাল ঊঠাতেন যে দুই তিন জনের কথা এত বেশি মনে পড়ছে যাদের কথা না বললেই নয় , উনারা হচ্ছেন একজন আমাদের পিছনের বাড়ির মনাউল্লাহর ছেলে ‘চটই মিয়া’ও অন্য জন ‘আতই মিয়া’,সাথে নাজমা হোটেলের মালিক ছিলেন মনসুর গ্রামের ‘কনা মিয়া ‘তাকেও মসজিদের উন্নয়ন কাজে বলিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা গেছে ,মসজিদের সামনে কয়েকটি দোকানের মধ্যে ছিল,
কারি সাহেবের ভুষিমালের দোকান,আবুল মামার লেপ এর দোকান,আতই মিয়ার হোমিও হল।
মসজিদের একটু আগে বিপরিতে একটি আমগাছের অস্তিত্বের কথা স্পষ্ট মনে আছে , ঐ আমগাছের নিচেই ছিল লষ্কর পুরের লুলু মিয়া মহরীর ভাগিনা মতিন ভাইয়ের সাইকেলের দোকান । পাশেই ছিল জহির আলী হাজি মামার ছেলে মুহিব ভাইয়ের মাইকের দোকান ( সম্ভবত স্বাধীনতার পরে হয়েছে ) আরও ছিল “ আহমেদ ক্লথ ষ্টোর” নামে একটি কাপরের দোকান।
ঐ আমগাছের নিচেই একটি মুচী বসতো , তার একটু পিছনেই একটি লেম্প ও হারিক্যান এর চিমনী ও নানা রকম লোহার সামগ্রী
ও তারকাটা ও পিতল ,লোহার দ্রবাদি বিক্রির একটি দোকান এবং একটি নিমকি ও মিষ্টির দোকান ও ছিল ।
মসজিদ সংলগ্ন বিল্ডিং এ তিনটি দোকান খুউব বিখ্যাত ছিল ,লষ্করপুরের আবুল চৌধুরীর ‘রিয়াজ শার্ট ‘ , আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেবের ভাই ,বাচ্চু মামার “ বিলাস বিপনি ও “ রামগোপাল ফার্মেসী ,
ঐ বিল্ডিং এর উপরে জুবেদ মামার অফিস এবং নীচে সিড়ির কোনায় একটি ঘড়ি মেকানিকস এর দোকানের কথা এ মনে পড়ছে , উনার বাড়ী সম্ভবত মনসুর এলাকায় ছিল এবং এই ঘড়ির দোকানটি পরবর্তীতে কাদিপুর রোডে ইরফান আলী মামার বাড়ীর বিপরীতে চলে যায় ।
মাগুরা হয়ে এই রাস্তাটিকে মনসুর রোড বা কাদিপুর রোড ও বলা হতো, মুখেই ছিল মোমিন মিয়ার বড় মুদি দোকান ও তার পর একটি চাউলের দোকান , এই পাড়ে ছিল একটি পানের আড়ৎ ও একটি চুল কাটার সেলুন , চুল দাড়ী সাধারণত বাজারের ভিতরেই দক্ষিন পুর্বকোনে কাটতে দেখতাম , ছোট বড় সবাইকেই ।এই রাস্তায় ছিল কালীবাড়ি ও বশিরুল হুসেন বা বি. এইচ প্রাইমারী স্কুল , এই এলাকা আগে কৌলার জমিদার বশিরুল হুসেন জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল ।তার নাম অনুসারেই এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ।
দক্ষিন বাজার থেকে থানায় যাবার পথে ছিল মক্তোদির নানার রেশনের দোকান তার পাশ দিয়ে একটি টিপা রাস্তা রেল কোলনি ভেদ করে স্টেশনে পৌছেছে ,
একটু পাশেই ছিল ঢাকাইয়া তারা মিয়ার “রেইনবো বেকারী “, তাদের এক ছেলের নাম ছিল কাদির ,,একটু সামনে এগুলেই বাম দিকে ছিল কুলাউড়া থানা , রাস্তায় দাড়িয়ে থানার কার্যক্রম দেখা যেত , থানার এক পাশে ওসি সাহেবের রুম ,অন্য পাশ্বের রুমে অন্যান্য দারোগার বসার জায়গা ও তিন চারটি টেবিল ছিল , টেবিলের উপর থাকতো মোটা মোটা চারকোনা বড় বড় খাতা , মাঝখানের রুমটি ছিল হাজত খানা , কেউ আটকা পড়লে তাকে দেখার জন্য রাসতায় কৌতুহলী লোকের লাইন পরতো, থানার বিপরিত দিকে ডাকবাংলো , ডাক বাংলোর কোনায় ছিল ফুটবলার লিটন দের বাসা , লিটন বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী , ইন্টারনেট এর কল্যানে কথা বলার সময় কুলাউড়ার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে লিটনের কাছে থেকে অনেক অতীত তথ্য ও ইতিহাস পাওয়া যায় ।
ডাক বাংলা পেরুলেই ছিল ইউনিয়ন অফিস , আওয়ামীলীগ অফিস , এখানে একটি খাবার পানির কল ছিল , সারাক্ষন পানি পরতো এবং আমরা অবাক হতাম এত পানি কোথা থেকে আসে ?
স্টেশন রোডে ছিল পুরোনো হাসপাতাল , জয়পাশার কাদির মিয়া ও সিকান্দর ভাইয়ের পরিচালনায় “ সিকান্দর ক্লথ ষ্টোর “ দক্ষিন ভাগ চা ষ্টল “ জেলা পরিষদের ডাকবাংলো,লাবু কাকার মিষ্টির দোকান,
ময়না হাজির চাউলের দোকান , মোস্তাক মিয়ার “রহমানিয়া ষ্টোর ,”শফিক হাজীর রড সিমেন্টের দোকান ,জয়পাশার একটি লাইব্রেরী ও সাহেব বাড়ীর সৈয়দ হাবিবুল্লাহের আরোগ্য নিকেতন নামের ফার্মেসী , কয়েকটি কাপরের দোকান ও সত্তার মিয়ার অফিস ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য,
চৌমুহনী মোড়ে আলাউদ্দিন হাজী সাহেবের “ কুলাউড়া রেষ্ট হাউজ “
মোবারক মিয়ার “ আজম বোডিং এবং উত্তর বাজারের দিকে যাবার পথে “জয়নাল আবেদিন সাহেবের স্টার এজেন্সী, কালামিয়ার লেপের দোকান , বিপরীতে ডা: রিয়াজ উদ্দিনের চেম্বার ,তিনি হাজি ফরমুজ আলীর বাসায় ভাড়া থাকতেন ।
সনু মেম্বারের ফ্যাশান কর্নার , মজিদ মিয়ার বিওসি তেলের পাম্প ,সাধনা ঔষধালয় , শক্তি ঔষধালয়,রায় কুঠি বিল্ডিং , “ মর্ডার্ন ফার্মেসি , প্রবন বাবুর হোমিও হল , রোডস এর অফিস ,ডাঃশিশির বাবুর ‘ শিশির হোমিও হল , পপুলার লাইব্রেরি ,উত্তর বাজার জামে মসজিদ ,সাব রেজিষট্রী অফিস ( মজার ব্যপার হলো এই অফিসের সাব রেজিষ্টার সাহেবের মাথার উপরে হাতে টানা পাখার ব্যবস্তা দেখতে ভীর করতাম আমরা অনেকেই )উত্তর বাজার ,সি ও অফিস রোড , আলাউদ্দিন হাজী সাহেবের বাড়ি , তাজু হাজীর রাইস মিল ,রাবেয়া স্কুল ,দুএকটি টং দোকান,কয়েকটি মূহরীর গদি , এনাম ভাইদের ঔষধের দোকান , কুলাউড়া হাসপাতাল সহ আরো কত কিছু ?
সারা কুলাউড়ায়ে সম্ভবত দুইটি স্টুডিও ছিল
ষ্টুডিও নটরাজ ও অজন্তা ।(চলবে)
৭১ এর স্মৃতি -পর্ব ২৩ ( আমানীপুর )
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কুলাউড়ার কৌলা,পৃথিমপাশা , ঘরগাও , পাল্লাকান্দি,কানিহাটি ছাড়া ও তার আশপাশের আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য আত্বীয় বাড়ির সাথে সংগ্রামের সময় যোগাযোগের কথা মনে আছে ।
বিশেষ করে আমানীপুরের কথা ।
আমানীপুর সাহেব বাড়ি কুলাউড়ার দক্ষিন পু্র্বে টিলাগাঁও রেল য্টেশনের কাছে পাল্লাকান্দি থেকে মাইল খানেক দুরে , সবুজে ছড়ানো পাহাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত ।
কুলাউড়া থানার টিলা গাঁও ইউনিয়নের অনেক গুলো গ্রাম , যেমন , লাল বাঘ , আস্রয় গ্রাম ,নয়াপতন, যাদবপুর,বালিয়া,তাজপুর,গন্ডারগড়,
পুরিগ্রাম,দুন্দালপুর,খন্দকারের গ্রাম,শাহাজাদপুর,জালালপুর,সন্দারাজ,ডরিতাজপুর,
ইফসুবপুর,বাদেস্যালন,বালিয়া,বিজলী, শাহাপুর,চানপুর,সুজাপুর,লালপুর,মীরপুর,ছালামতপুর,কালামপুর,বালিসিন্দি,মোবারকপুর ,নৈমপুর,কাজিরগাঁও ,লহরাজপুর,বৈদ্যশাসন,পাল্লাকান্দি,পূর্বহাজিপুর,মুহিবনগর,
আমানীপুর ইত্যাদি গ্রামগুলো সবুজে ঘেরা ,এরই মধ্যে ছবির মত সাজানো একটি গ্রামের নাম আমানীপুর ঐ গ্রামেই একটি সুবিশাল সাহেব বাড়ী রয়েছে , যে বাড়িতেই একবার যাবার সুযোগ হয়েছিল , বাড়ির সামনে শাহ মতিউল্লাহ (রঃ) এর মাজার একটি দিঘী, মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন একটি পুকুর ছিল যার স্বচ্ছ টলটলে পানি পান করতো সমগ্র গ্রামবাসী ঐ পুকুরে শুধু অযু করতে পারতো সবাই , অন্য পুকুরটিতে গোসল করতে হতো এবংঅতি প্রাচিন কালে প্রতিষ্ঠিত একটি টি টাইপের বাংলো , যা কালের স্বাক্ষী বহন করে আজও অনেক স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে ।
বাবা হযরত শাহজালাল ( রঃ) এর সাথে আগত ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম হবিগঞ্জের হযরত সৈয়দ নাসিরুদ্দিন সিপাহসালাহ এর পরবর্তী ১২ তম পুরুষ শাহ সৈয়দ ইকরামুল্লাহ অবস্তান করেন পাল্লাকান্দিতে আর তার অপর ভাই শাহ সৈয়দ ইনামুল্লাহর ও তার পরবর্তী বংশধরগন এই আমানীপুর সাহেব বাড়িতে অবস্তান করেন ।
সৈয়দ ইনামউল্লাহর প্রৌপুত্র সৈয়দ বুরহানউদ্দিন ,তার তিন ছেলের মধ্যে সৈয়দ রেহানউদ্দিন ও সৈয়দ জাফরউদ্দিন বিয়ে করেন কুলাউড়ার কৌলার সৈয়দ বশিরুল হোসেন এর চাচা সৈয়দ সমদুল হোসেনের দুইকন্যা যথাক্রমে নজিবুন্নেছা ও তালেবুন্নেছা কে ,সৈয়দ রেহানুদ্দিনের মেয়ে মজিবুন্নেছার বিয়ে হয় কানিহাটির আব্দুল মান্নান চৌধুরী সাহেবের সাথে , আব্দুল মান্নান চৌধুরী ছিলেন ১৯৩০-১৯৪০ সালে অবিভক্ত ভারতের সাউথ সুরমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বৃটিশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান , তিনি তৎকালিন সময়ে আই এল ও কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং অসুস্তবোধ করলে চিকিৎসার জন্য ল্ন্ডনে অবস্তানকালে ইহলোক ত্যাগ করেন । তাকে লন্ডনেই সমাহিত করা হয় ।
সৈয়দ বুরহানুদ্দিনের আর এক ছেলে সৈয়দ আফতাব উদ্দিন । তার তিন ছেলের মধ্যে একছেলে সৈয়দ মিসবাহউদ্দিন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিযুক্ত হন , তিনিই এই কুলাউড়া অন্চলের প্রথম বিচারপতি , তিনি একজন পরহেজগার , অমায়িক ও অত্যান্ত বিনয়ী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন , তার ছেলে সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন একজন প্রতিষ্ঠিত বড় কোম্পানীর উচ্চপদে ছিলেন এবং বর্তমানে ঢাকায় অবস্তান করছেন । তার চার মেয়ে যথাক্রমে সৈয়দা দীনা আহম্মেদ , সৈয়দা লিপু চৌধুরী, সৈয়দা তারানা ফারুক , সৈয়দা তামান্না কোরেশী ।
সৈয়দ মিসবাহউদ্দিনেরাও তিন ভাই , সৈয়দ মিতফাউদদিন ও সৈয়দ আহবাব উদ্দিন , সৈয়দ মিতফা উদ্দিনের ছেলে সৈয়দ মহিউদ্দিন হোসেন দীর্ঘদিন টিলাগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে ছিলেন এবং প্রচুর জনহিতকর কাজ করেছেন । এই বংশের অন্যান্য নারী সদস্যদেরও অনেক ভাল ভাল সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয়েছে এবং তারা স্ব স্ব স্হানে প্রচুর সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছেন ।
টিলা গাঁও ইউনিয়নের বাঘের টেকী নামক স্হানে , যা ব্রাহ্মন বাজার শমশের রোড়ের পাশ্বে অবস্থিত গাছ গাছালীতে ঢাকা একটি মাজার রয়েছে যাকে ‘বাঘের টেকীর মাজার’ বলা হয়ে থাকে ,ঐ মাজারটি কোন দরবেশের তা কেউ বলতে পারেন নাই তবে তিনি বাবা শাহজালাল (রঃ) এর সাথী বলে স্থানীয় ভাবে পরিচিতি রয়েছে ।
এই মাজারে এখনও অনেক লোক মাঝে মাঝে বাঘ দেখতে পান বলে জনশ্রুতি রয়েছে ।
১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কুলাউড়ার সাথে টিলাগাও ,শরীফপুর , হাজিপুর ইউনিয়নের দুরত্ব বেশি থাকায় এই ইউনিয়ন তিনটির সব প্রকার কাজ কর্মই চলতো শমশেরনগরকে কেন্দ্র করেই । তাছাড়া তখন সড়ক পথের চেয়ে রেল পথই যোগাযোগের অন্যতম নির্ভরযোগ্য পথ ছিল বলে সকলেই রেলপথকে সবার আগে বেছে নিতো।
এই অন্চলের ভানুগাছ , শমশেরনগর , মনু ,টিলাগাঁও , লংলা , কুলাউড়া, বরমচাল প্রভৃতি রেলস্টেশনে উল্লেখযোগ্য স্বরনীয় ঘটনা সমুহ ইতিহাসের স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে ।কিছু উল্লেখ যোগ্য ঘটনা রয়েছে শমশেরনগর , টিলাগাঁও রেল স্টেশন সমুহে ..
সংগ্রামের শুরুতেই পাকিস্তানী সৈন্যদের পৈশাচিকতার খবর শুনে জেনারেল আব্দুর রবের পরামর্শে তৎকালিন শমশেরনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোজাহিদ ,ক্যাপটেন মোজাফ্ফর আহমেদ , আব্দুল গফুর ,সাজ্জাদুর রহমান ও আমজদ আলী প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের উপস্হিতিতে শমশেরনগরে ছাত্রলীগ , আওয়ামী লীগ ও মুক্তি কামী জনগনকে নিয়ে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে সীমান্ত ফাঁড়ী গুলোর বাঙ্গালী ই.পি.আরদের প্রতিরোধ সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য আহব্বান জানানো হবে , সেই লক্ষ্যে নেতৃবৃনদ আলীনগর চা বাগানের ম্যানেজারের গাড়ীতে করে বিক্ষুব্ধ জনতার সমন্নয়ে ২৮ শে মার্চ প্রথমেই চাতলাপুর বাগানের ফাঁড়ীতে যান ।সেখানে ছিল দুইজন অবাঙ্গালী সৈন্য । বিক্ষুব্ধ জনতা সেই অবাঙ্গালী সৈন্যদের জবাই করে হত্যা করলে , সেখানকার ফাঁড়ীর সুবেদার শামসুল হক সহ সকল বাঙ্গালী সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্তান নেন এবং সবাই মিলে মোজাফফর আহম্মেদ এর নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজ নামে একটি বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেন ।(চলবে)
৭১ এর স্মৃতি —(১৩)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
একাত্তরে কুলাউড়ার কত স্মৃতি ,কত কথা ,কত গান মনে পড়ছে , কোনটা রেখে কোনটা লিখবো , কাকে বাদ দিয়ে কার কথা লিখবো ? ভেবে পাচ্ছি না , যেহেতু লিখতে বসেছি তাই কিছু তো লিখতেই হবে , যা পাঠ করে বর্তমান প্রজন্ম সহ সেই সময়ের অনেকেই ক্ষনিকের তরে হলেও সম্মিত ফিরে পাবে , আবার ভাল না লাগলে কেউ কেউ কটুক্তিও করতে পারেন যা বোধগম্য।
যাই হোক , সংগ্রামের সময় কোনএকদিন কুলাউড়া রেল ষ্টেশনে গিয়েছিলাম সম্ববত , আমাদের ছোট নানু , মানে নানার ছোট বোন তাহেরা বানু ,যার বিয়ে হয়েছিল কিয়াতলার নবাব আলী নানার সাথে , ঢাকায় যার বাড়ি ছিল নাখালপাড়া এলাকায় তাদেরই কেউ কেউ এসেছিলেন সেদিন কুলাউড়াতে , তাদেরকে ষ্টেশন থেকে বাড়িতে আনার উদ্দেশ্য ছিল , সাথে ছিলেন বড় মামা আমির আলী , ছোট মামা মনির আলম ও আমাদের বাড়ির কৃষি কাজের সহযোগী দুইজন লোক যথাক্রমে চাতলগাও য়ের ‘কটা মিয়া’ ও মনুরের ‘বশিরউদ্দিন ‘ এরা দুইজনই ছিল বাগিদার , আমাদের বাড়ীর ধান ক্ষেত ও ফসলাদি ওরা শর্তসাপেক্ষে প্রতি মৌসুমে চাষ করে দিত , এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে বিশেষ করে নানীর অনুরোধে নানা প্রকার বিপদে আপদে ,কাজে কর্মে নিঃস্বার্থ ভাবে সহযোগীতা করতো , আগেকার লোকেরা এমনি দরদী ছিল , এখনকার মত এত হিসাবী ছিল না ।তেমনি দরদী এই দুইজনের কাছে শ্রদ্ধাসহ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওদের মংগল কামনা করছি , জানি না সেই ‘ কটা’ ভাই এখনও জীবিত আছে কিনা , মরে গিয়ে থাকলে , তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি , পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি ,’কটা ভাই ‘ ছিল দেখতে কালো কিন্তু অত্যান্ত সহজ সরল ও হাসিমাখা মুখে সবসময় সে সকল প্রকার গ্লানি সহ্য করতো ।
ঐ দিন ষ্টেশনে ঢাকা থেকে আগত মেইল ট্রেনটি সকাল সাতটায় আসার কথা ছিল কিন্তু কি কারনে জানি আসি আসি করে অনেক লেট করেছিল প্রায় দশটার দিকে এসে পৌঁছেছিল ।
ইতি মধ্যে ষ্টেশনে বসা ছিলাম ফাস্টক্লাস অয়েটিং রুমে , খুউবসুন্দর ছিল সেই রুমটি ,এক পাশে ইজি চেয়ারে বসা ছিলেন এক জন যাত্রী , যিনি খুউব সম্ভ্রান্ত কেউ ছিলেন হয়তো , বনেদী পান্জাবী ও কোটি পড়া ছিলেন , চোখে চশমা ও হাতে হাত ঘড়ি ,বড় মামা ছোট মামা শুধু ‘ ভাইসাব’ ‘ভাইসাব’ করছিলেন উনি ঐ ট্রেনে করেই সিলেট যাবেন পরে জেনেছিলাম উনি জয়পাশার বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী যার নাম সৈয়দ জামাল উদ্দিন পিতার নাম হাজি সৈয়দ মাহমুদ আলী , বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষনের পর ৮ ই মার্চ ঢাকা থেকে কাগজের তৈরী স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে আসেন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা গিয়াসউদ্দিন আহমেদ আর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে কুলাউড়ার অধিকাংশ ঘরে তোলা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা এই সৈয়দ জামাল ই কুলাউড়াতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন ,
তিনি সেদিন সিলেট যাচ্ছিলেন , কিছুক্ষনের মধ্যেই তাকে ঘিরে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে ।তার সহযোগীতার জন্য সেদিন ‘টেকওই’এবং ‘বকওই’ নামে জয়পাশা এলাকার সহযোগী দুই ভাইয়ের আগমন ঘটেছিল ষ্টেশনে । ।
যতদুর মনে পড়ে তখন সিলেট যাওয়ার জন্য সকাল বেলা এই মেইল ট্রেনটিই ছিল অন্যতম ভরসা , সকাল বেলা এই ট্রেনটি চলে যাবার একটু পরে ১০ টার দিকে আরো একটি ট্রেন যা লাতু’র ট্রেন নামে পরিচিত ছিল তা লাতু থেকে কুলাউড়া আসতো সেই ট্রেনটি , ষ্টেশনে ঢুকে , বগি থেকে ইন্জিন আলাদা হয়ে , দক্ষিন দিকে গিয়ে অন্য একটি লাইন দিয়ে পিছনে ফেরত এসে উত্তর দিকে আবার ঐ ট্রেনের পিছনের বগির সাথে যুক্ত হয়ে ইন্জিনটি ট্রেনটিকে নিয়ে সিলেটের উদ্দেশ্য রওয়ানা হতো ।এই ট্রেনটি ছিলো লোকাল ট্রেন , সব য্টেশনে থেমে থেমে যেত ।কুলাউড়া রেল ষ্টেশনের উত্তর দিকে ইন্জিন ঘুড়ানোর আরো একটা সুন্দর ব্যবস্তা ছিল , গোলাকার একটি চাকতি্র মত জায়গায় ইন্জিনটি দাঁড়াতো ঐ অবস্তায় লাইন সহ চাক্তীটি ইন্জিন সমেত ঘুড়ে যেতো ।
আমরা দুর থেকে দেখতাম , কাছে যেতে পারতাম না ,কাঠের দুটি পাল্লা মার্কা গেইট ছিল , ইন্জিন টি ঐখানে ঢোকার সাথে সাথেই গেটকিপার নিরাপত্তা জনিত কারনে ঐ কাঠের জালি মার্কা গেইটটি লাগিয়ে দিতো , ইন্জিনটি সহ চাক্তিটি ঘুরে গেলে আবার গেইটটি খুলে দিত ।
কুলাউড়া জংশন নামের ষ্টেশনটি এই বাংলায় নানা কারনে বিখ্যাত ছিল এখনও আছে তবে আগের সেই জৌলুশ বদলেছে , ষ্টেশনের উত্তর দিকে দুইটি হোটেল ছিল একটি হিন্দু হোটেল বা নিরামিষ হোটেল অন্যটি মুসলিম হোটেল বা আমিষ হোটেল ।নিরামিষ হোটেলটি চালাতো দিলীপ কাকা যার বাসা ছিল দক্ষিন বাজারের মাগুরা এলাকায় আর আমিষ হোটেলটির পরিচালনায় ছিল রেইনবো বেকারির তারা মিয়া ।
, ঠিক মাঝখানেই ছিল টিকিট কাউন্টার ,
টিকিট কাউন্টারের দুইপাশে দুইদিকে দুইটি লোহার বেন্চ ছিল সাধারন যাত্রীদের বসার জন্য পশ্চিমদিকে একটি বুক ষ্টল ও ছিল যেখানে প্রতিদিনের পত্রিকা পাওয়া যেতো , সিলেট থেকে যুগভেরী নামক একটি পত্রিকা রের হতো তা ই আগে পাওয়া যেতো আর ঢাকার পত্রিকা পড়তে হলে একদিন অপেক্ষা করতে হতো ।
দুইটি পান বিরির বাক্স মার্কা দোকান ও ছিল , বুক ষ্টলের দক্ষিন দিকেই ষ্টেশন মাস্টারের রুমটি ছিল , প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের গা ঘেঁষেই ছিল একটি করিডোর , পূর্বদিকের প্লাটফরমটি একটু উচুতে ছিল , তার দক্ষিন দিকেই একটি ক্যান্টিন ছিল ,ক্যান্টিনে খাবারের পরিবেশনা অনেক সুন্দর ও মান এবং দাম অনেক গ্রহনযোগ্য ছিল ।ক্যান্টিনের উপরে ছিল একটি কেবিন , রোজার মাসে ঐ কেবিন থেকে কুলাউড়া বাসীদের সেহরী খাবার জন্য সাইরেন বাজানো হতো । ষ্টেশনের পশ্চিমেই ছিল রেলওয়ের প্রাইমারী স্কুল , ভাল পড়াশুনা হতো এই স্কুলে ,অনেক নামী দামী ব্যক্তিদের হাতে খড়ি হয়েছে এই পুরোনো স্কুলটিতে,আরো অনেক কিছুই ছিল কুলাউড়া রেল ষ্টেশনে । আগামীতে আরো ব্যাপক ভাবে লেখার ইচ্ছা রাখি । ( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি পর্ব-১৬-( জয়পাশা-১)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
৭১ এ কেমন ছিল কুলাউড়ার জয়পাশা সাহেব বাড়ী ?
অনেক বার মনে হয়েছে এই ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি সম্পর্কে কিছু লিখি , কিন্তু লিখতে গিয়ে বার বার পিছিয়ে যাচ্ছি , কিছু তথ্যের প্রয়োজন ছিল যা এই বংশের অন্যতম সদস্য সৈয়দ ইশতিয়াক লন্ডন থেকে ও সৈয়দ হাদী সুদুর আমেরিকা থেকে আমাকে ইমেইলে আমার বাবার লেখা ১৯৬০ সালের একটি বই সহ কিছু ছবি পাঠিয়ে সহযোগীতা করায় তা সম্ভব হতে চলেছে ।
জয়পাশা জমিদার বাড়িটি মুলত আমার আব্বার নানার ভায়রা খন্দেগার সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর বাড়ি ।আমার আব্বা মরহুম সৈয়দ আব্দুল আহাদ মশকুরের এবং আমার জন্ম হয়েছে তার নানা, বাংলার বার ভুইয়া খ্যাত মসনদে আলা ঈশাখার বংশধর কিশোরগন্জর কিংবদন্তী ,হয়বতনগর দেওয়ানবাড়ির দেওয়ান মান্নান দাদ খানের বাড়িতে তবে আমাদের পুর্বপূরুষের আদি অবস্তান সিলেটে ,শহরের কুমারপাড়া ঝরনার পাড়ে হযরত শাহাজালালের (রঃ) সহযাত্রী হযরত সৈয়দ হামজা ( রঃ) শেরসোয়ারী আমাদের পুর্বপুরুষ , সিলেট থেকে আমার আব্বার পিতামহ সৈয়দ আব্দুল হাফিজ বা টিলা সাহেব কিশোরগন্জের সেকান্দর নগরে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হন এবং তারপর আমার পিতামহ সৈয়দ আব্দুল হাকাম ওরফে বুলবুল মিয়া হয়বতনগরে দেওয়ান বাড়িতে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হন এবং বাড়ী সংলগ্ন পশ্চিমে নিজ বাড়ী তৈরী করে অবস্থান করেন , এই বাড়ির সর্বশেষ জমিদার দেওয়ান মান্নান দাদ খানই আব্বার নানা , তিনি একে একে পাঁচটি বিয়ে করেন , ১) দেওয়ান মান্নান দাদ খান প্রথম বিয়ে করেন নওয়াব ফয়জুননেছার ভাই ইয়াকুব আলী চৌধুরীর ছেলে সেকান্দর আলী চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে নান্নী বিবিকে , সেই পক্ষের দুই মেয়ে ছিল
ক)দেওয়ান মাকসুদা বিবি যিনি আমার দাদী আর আমার দাদা ছিলেন সেকান্দর নগরের সৈয়দ আব্দুল হাকাম বুলবুল মিয়া সাহেব ,আমাদের পুর্বপুরুষ সিলেট শহরের কুমারপারা ঝরনার পারের ,আমার আব্বা সৈয়দ আব্দুল আহাদ ও আমার চাচা সৈয়দ আব্দুল হাদী রা দুই ভাই এই পক্ষে আমার বাবা চাচার কোন বোন ছিল না
অন্য মেয়ে
খ) দেওয়ান হালিমা আক্তারের বিয়ে হয় ইটনায় দেওয়ান আব্দুল আলীম সাহেবের সাথে ।এই পক্ষে কোন সন্তানাদি ছিল না
দেওয়ান মান্নান দাদ খানের এই পক্ষের একমাত্র ছেলে দেওয়ান মাহতাব দাদ খান নিঃসন্তান থেকে ২২ বছর বয়সে মারা যান ।
দেওয়ান মান্নান দাদ খানের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন বৌলাই জমিদার বাড়ীর সৈয়দ আজিজুল হকের কন্যা ,সৈয়দ হাবিবুল হকের একমাত্র বোন সৈয়দা খুজেস্তা বেগমের সাথে , এই পক্ষের দুইটি ছেলে হয়েছিল তারা অল্প বয়সে মারা যানএবং তার এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার মাতা হয়বতনগর স্টেইট এর অধিকারী জমিদার, কর্তিৃ সাহেবা হিসাবে সবাই যাকে চিনতো সেই আয়শা আক্তার খাতুন তাকে তৃতীয় বিয়ে করান , হবিগঞ্জের দাউদ নগর সাহেব বাড়ীর সৈয়দ আবদুর রহমান সাহেবের কন্যাকে ।ঐ পক্ষের ছেলে দেওয়ান সাত্তার দাদ খান বা সাইয়ারা মিয়া কেই দেওয়ান মান্নান দাদ খানের বড় ছেলে হিসাবে সবাই জানতো , তার একমাত্র বোন হলো দেওয়ান বারিরা আক্তার বা আনজুমান বিবি আন্জুমান বিবির বিয়ে হয় সুলতানশী সাহেববাড়ির ফিরুজ মিয়া সাহেবের ছেলে সৈয়দ আব্দুল কাদির ওরফে সুরুজ মিয়ার সাথে। উনাদের আম্মা মারা যাবার পর দেওয়ান মান্নান দাদ খান চতুর্থ বিয়ে করেন , সিলেটের মজুমদারীতে সায়রা খাতুন মজমাদারকে এই পক্ষের জুনায়েদ মিয়া ও জানে জানান মিয়ার ( এরা আমার দাদীর ভাই ) এক বোনের নাম দেওয়ান সাওদা আক্তার , যার বিয়ে হয় বানিয়াচং জমিদার বাড়িতে স্যার ফজলে হাসান আবেদের চাচার সাথে আর এক বোন হচ্ছে মরিয়ম বিবি উনার বিয়ে হয়েছিল বৌলাই সাহেব বাড়ীর সৈয়দ মাজহারুল হক নুর মিয়ার সাথে , আমার এই নুর দাদা শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের ঈমামতি করেছিলেন কোন এক ঈদের জামাতে , উনার মেয়ে আক্তারী ফুপু ঢাকাতেই থাকেন ।
আর দেওয়ান মান্নান দাদ খান সর্বশেষ বিয়ে করেন হযরত সৈয়দ নাসিরউদদিন সিপাহসালারের উত্তরসুরী সুলতানশী সাহেব বাড়ীর ফিরুজ মিয়া সাহেবের কন্যা সৈয়দা মনিরুন্নেছা খাতুনকে , এই পক্ষের ছয় সন্তানের মধ্য পাঁচ সন্তান যেমন দেওয়ান সবুর দাদ খান বিশরাফী দাদা , দেওয়ান খালেক দাদ খান আবু আইয়য়ুব দাদা ,দেওয়ান হাফসা আক্তার ,হাফসা দাদী ,দেওয়ান হোসনা আক্তার ,হোসনা দাদী ও দেওয়ান হাসনা আক্তার ,হাসনা দাদী এখনও জীবিত আছেন ওদের সবার ছোট ভাই আমাদের প্রানপ্রিয় দেওয়ান ওয়াদুদ দাদ খান সোয়েব দাদা ও তার স্ত্রী বেবী আপা আমাদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন
।দেওয়ান মান্নান দাদ খান যে তৃতীয় বিয়ে করেন হযরত সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহসালার (রঃ) এর বংশধর হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগন্জের দাউদনগর সাহেব বাড়ীর সৈয়দ আব্দুর রহমানের মেয়ে এবং গাজি মিয়া সাহেবের বোনকে ,সৈয়দ আবদুর রহমানের পাঁচ মেয়ের এক মেয়েকে , অন্য আর এক মেয়েকে বিয়ে করেন জয়পাশা জমিদার বাড়ির জমিদার সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহ , মান্নান দাদ খানের ভায়রা ভাই ছিলেন খন্দেগার সৈয়দ হেদায়েতউল্লাহ , আবার
এই খন্দেগার সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর বড় বোনকে বিয়ে করেন দেওয়ান মান্নান দাদ খানের প্রথম পক্ষ লাকসাম নওয়াব বাড়ীর সেকান্দর আলী চৌধুরীর ছেলে আইয়ুব আলী চৌধুরী অর্থাৎ নান্নী বিবির ভাইয়ের কাছে ,
ছোটবেলা থেকেই আমার আব্বা তার নানীর বোনের বাড়ীতে, অর্থাৎএই জয়পাশা জমিদার বাড়ীতে নানীর মতই আদর স্নেহ পেতেন, পুরো পরিবারের সকলেই ছিল তার কাছে অত্যান্ত মর্যদাসম্পন্ন এবং তিনিও ছিলেন এই জয়পাশা জমিদারবাড়ির সকলের কাছে প্রিয়পাত্র ও সর্বক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিত্ব ।সেই সুবাদেই এই বাড়িতে অবস্তান কারী যারা যারা থাকতেন সবাইকে অত্যান্ত আপনজন এবং ঐতিয্যবাহী এই বাড়িটিকে আমার আব্বার মামার বাড়ী বা আমি আমার দাদা বাড়ি হিসাবে জানি ও জেনে এসেছি।
যতদুর মনে পরে , যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই আম্মার সাথে প্রায়ই যেতাম কুলাউড় জয়পাশার সেই বিখ্যাত খন্দেগার বাড়িতে ,আমাদের নানাবাড়ি উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে পুর্বদিকে রেল লাইনে উঠতাম , রেল লাইন ধরে উত্তর দিকে এগুলেই একটু সামনে গেলে পুর্বদিকে ছিল রেলওয়ে থানা , তার পাশদিয়ে গিয়ে বেশকিছু ঘনবসতিপূর্ণ বাড়িঘর পেরিয়ে সাহেববাড়ির দক্ষিনদিকের মাটির দেওয়ার বা বাউন্ডারী ওয়াল পেরিয়েই পড়তো ছোট দাদা অর্থাৎ সৈয়দ হবিবউল্লাহ দাদার অংশ সেই অংশের আতিথেয়তা ছিল মনোমুগ্ধকর দাদি ছিলেন অনেক সুন্দরী এবং বিরামচরের জমিদার কন্যা ,বিরামচরের সেই দাদী ছিলেন অনেক বিনয়ী ও সদালাপী , তারপর সৈয়দ অলীউল্লাহ দাদার অংশ যেখানে ভাটিপারার আরএক জমিদার কন্যা আমার ঐ দাদী খুউব পান খেতেন এবং গান শুনতে পছন্দ করতেন , আমরা গেলে পরে চাচা ফুপুরা ঘিরে থাকতো , তারপর যেতাম অত্যান্ত পরহেজগার সবসময় বসে থাকতেন বিশাল বারান্দার ইজি চেয়ারে , সেই প্রিয় মাখন দাদার অংশে , যিনি স্বাধীনতার আগে কুলাউড়া ইউনিয়ন পরিষদে দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধিত্ব করেছেন এই দাদার অংশে আসলে অনেক সময় পেরিয়ে যেত , দাদী ছিলেন সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জের কানিশাইল (উত্তর বাড়ীর )নামকরবাড়ির জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের মেয়ে ,তিনি ছিলেন বৃটিশ আমলের তৎকালীন সিলেট জেলার তিনজন শিক্ষিত ব্যক্তির একজন , সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পাকিস্তানের শুরুতে বগুড়ার ডি.সি. ছিলেন , এই দাদীর নাম ছিল হোসনা আরা চৌধুরী,কোনদিন তাকে ঘোমটা ছাড়া দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার এই দাদীর ও পানের বাটা সাথে থাকতো তিনিও পাকিস্তান আমলের মেট্রিক পরীক্ষাতে জিওগ্রাফীতে লেটার পেয়ে পাশ করা একজন শিক্ষিত মেয়ে এবং উত্তরদিকে সবার বড় ভাই মাহবুবউল্লাহ দাদা বা মবুব মিয়ার অংশ এই বড় দাদী ছিলেন অত্যানত্য সুন্দরী এবং চাঁদপুরের রুপসা জমিদার বাড়ীর একজমিদার কন্যা, সবকটি ঘর ঘুরা শেষে সামনে পুর্বদিকে বাংলোঘরে আর যাওয়ার সময় পেতাম না ।তবে দু এক বারগিয়েছি ,সুন্দর সুন্দর অনেক গুলো রুম ছিলো ঐ বাংলাঘরটিতে , শতবর্ষী এই বাংলাতে অনেক নামী দামী নেতা নেত্রীর আগমন হয়েছে , আত্বীয় স্বজনের পদচারনায় সর্বদা মুখরিত থাকতো, এলাকাবাসীর অনেক বিচার সালিশ ও আন্ন্দধন পরিবেশ ও পরিস্তিতির অগ্নিস্বাক্ষী স্মৃতি বিজরীত এই বাংলোঘর ।
জয়পাশা সাহেববাড়ীর ইতিহাস ঐতিয্য অনেক বিশাল ও সম্বৃদ্ধ, সারাদেশের সকল সম্ভ্রন্ত পরিবারের সাথে ছিল এই পরিবারের পারিবারিক যোগাযোগ ও কমবেশি আত্বীয়তা ।কিছু কথা প্রসংগক্রমেই এসে যায় । ৬০ এর দশকের শুরুতে আমার আব্বা সৈয়দ আব্দুল আহাদ মশকুর রচিত গ্রন্থ “জয়পাশার খন্দেগার পরিবার “থেকে জানা যায় হযরত সৈয়দ নসরুল্লাহ “ যিনি হযরত সৈয়দ শাহজালাল ( রঃ) এর সাথে ইয়েমেন থেকে সাথী হয়ে সিলেটে আসেন ,হযরত শাহজালালের মৃত্যুর পর তিনি একবার এই অন্চলে অন্যান্য সাথীদের সাথে দেখা করতে আসেন ।ফেরার পথে জয়পাশার পাহাড়ী ভুমিতে অবস্তান করে কিছুদিন ইসলাম প্রচার করেন ।সৈয়দ নসরুল্লাহ তৎকালীন সিলেটের শাসনকর্তার মেয়েকে বিয়ে করেন , তাদের পুত্র সৈয়দ মামুদ হাফেজ একজন বিখ্যাত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন ।
সৈয়দ মাহমুদ হাফেজের অধঃস্তন পুরুষ স্বীয় প্রতিভাবলে ১৫৯৯ খৃষ্ঠাব্দে দিল্লির সম্রাট আকবরের অমাত্য মজঃফর খাঁর স্বান্নিধ্য লাভ করেন ।মজঃফর খা সৈয়দ মুসার শিক্ষা রাজনীতি জ্ঞান এবং কার্যকুশলতা দেখে স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দানের দ্বারা সম্পর্ক মজবুত করেন ।
সৈয়দ মুসার অধঃস্তন পুরুষ
সৈয়দ শাহ মোমরেজ দিল্লিশ্বর আওরঙ্গজেবের দরবারে কার্যদক্ষতা দেখিয়ে “ শেখ উল উলামা “উপাধি প্রাপ্ত হন ।পরবর্তীতে তিনি সিলেটে এলে সিলেটের শাসনকর্তা তাকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন । সৈয়দ শাহ মোমরেজ দেওয়ানের পদ থেকে অবসর নেবার সময় নবাব কর্তৃক লংলা পরগনার কিছু জমির স্বত্ত লাভ করেন ।এই জমিই বর্তমানে মোমরেজপুর গ্রাম ,তৎপুত্র সৈয়দ আজিজ উল্লাহ ও সৈয়দ মুতি উল্লাহ বহু শ্বাস্রে সুপন্ডিত ছিলেন ।তারা তৎকালীন দিল্লী সম্রাটের দরবারে পান্ডিত্য দেখিয়ে “খোদা ওন্দেগার “উপাধী এ মদদ মাস স্বরুপ বিস্তর ভুস্বম্পত্বি প্রাপ্ত হন । এর পর থেকে ঐ বংশের একাংশ খোন্দ গাঁর বা খন্দকার শব্দটি নামের সাথে ব্যবহার করে আসছেন ।সৈয়দ মুতি উল্লাহ “তুফেজে আজিজি “ নামের একটি গ্রন্থের লেখক ছিলেন ।সৈয়দ আজিজুল্লাহর পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ ও বিশিষ্ট লেখক ছিলেন , তার লেখা “ইস্রাফুল আরেফিনি এ বুরহানুল আসকিনি “নামক গ্রন্থ দুইটি উর্দু ভাষায় লেখা ।তিনিও নবাবের কাছ থেকে কিছু জমি পেয়েছিলেন ।সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ হেলিম উদ্দিন কুরেশীর বংশীয় দেওয়ান মান আনসারের কন্যাকে বিয়ে করেন , সৈয়দ আতাউল্লাহর অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ কেফায়েতউল্লাহ একজন ব্যক্তিত্ববান পুরুষ ছিলেন ,তার পুত্র হেদায়েত উল্লাহ ও একজন সুপুরুষ ছিলেন ।এই সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর পাঁচছেলের মধ্যে বড়ছেলেই হচ্ছেন সৈয়দ মাহবুবউল্লাহ বা মবুব মিয়া ।
সৈয়দ মাহবুব উল্লাহ ওরফে মবুব মিয়া ছিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতি বিদ , আওয়ামী লীগের সভাপতি , তার সাথে সাধারন সম্পাদক ছিলেন স্টার এজেন্সির জয়নাল সাহেব , পরবর্তীতে তিনি এ কুলাউড়া আওয়ামী লীগের সভাপতি হন ।
সদাহাস্সোজ্জল অত্যন্ত বিনয়ী , ফর্সা ধবধবে সাদা মবুব সাহেবকে দেখা মাত্র যে কেউ তার প্রতি আসক্ত ও শ্রদ্ধাশীল হতো ।
কখনও তিনি কারো সাথে কটুকথা বা দুর্ব্যবহার করেছেন কিনা সন্দেহ আছে ।এই মবুব দাদা আব্বাকে ভীষন আদর করতেন ,উনার বড় ছেলে মাসুম চাচা ও আর এক ভাগিনা লাকসামের লনী দাদীর ছেলে বেলায়েত চাচার মধ্যে ছিল ভীষন মিল ও দারুন সখ্যতা , এরা তিনজন সব সময় মবুব দাদার কাছাকাছি থাকতেন , বর্তমানে সবাই প্রয়াত ।
পাকিস্তানিরা তাদের বাড়ীতে মর্টারের আঘাত হানে ফলে উনাদের তৃতীয় ভাই জনাব অলিউল্লাহ সাহেবের ঘরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় ।
সৈয়দ অলিউল্লাহ সাহেব ও সাদাসিধে ভাবে চলাফেরা করেছেন , বড় তিন ভাইই পরলোক গত হয়েছেন তবে সবার ছোটভাই সৈয়দ হাবিবউল্লাহ সাহেব যিনি ৭১ সালে কুলাউড়া স্টেশন রোডে আরোগ্য নিকেতন নামে একটি ফার্মেসী খুলেছিলেন ,বর্তমানে ভাই বোনদের মাঝে একমাত্র তিনিই পরিবার পরিজন নিয়ে আমেরিকাতে অবস্তান করছেন এবং অপর একবোন মাধবপুরে জীবিত আছেন।
সৈয়দ হেদায়েতউললাহ সাহেবের পাচ মেয়ে ছিল তাদের কথা না লিখলে অর্থাৎ আমার সেই দাদীদের কথা না উল্লেখ করলে আমার এই স্মৃতি কথা লেখা অপূ্র্ণ থেকে যাবে , পাঁচ মেয়ের মধ্যে বড়মেয়ে
১) সৈয়দা নাজমুন্নেছা (লনী) বিবির কে বিয়ে দেন লাকসামের নওয়াব ফয়জুননেছার ভাই ইয়াকুব আলী চৌধুরীর নাতি আইয়ুব আলি চৌধুরীর ছেলে “বু আলী চৌধুরীর সাথে , অপর এক মেয়ে
২) সৈয়দা হোসনা আফরোজকে বিয়ে দেন লাকসামের বু আলী চৌধুরীর ভাই মসি আলী চৌধুরীর সাথে ।একই বাড়িতে দুইবোনের বিয়ে হয় দুই ভাইয়ের সাথে ।
আর এক মেয়ে ,
৩) সৈয়দা দিল আফরোজকে বিয়ে দেন বগুড়া নবাববাড়ির সাতানী অংশের খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌধুরীর ছেলে আবিদুর রহমান চৌধুরী টুকু মিয়ার সাথে ।
আর এক মেয়ে,
৪) সৈয়দা রুহ আফরোজকে বিয়ে দেন সিলেট দরগামহল্লার মুফতি বাড়ীর মুফতি রোকনউদ্দিন সাহেবের সাথে ।
এবং এক মেয়ে ,
৫) সৈয়দা ছালেহা বেগমকে বিয়ে দেন , হবিগঞ্জের মাধবপুর বহরা সাহেববাড়ির জনাব মনিরুল বারী চৌধুরীর সাথে আমার এই দাদীর এখন ও জীবিত এবং মাধবপুরেই আছেন। ( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি – পর্ব- ২৬ ( ঘরগাঁও)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত ‘সংকল্প’ কবিতায় বলেছেন
“ থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,-
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণারে।। “ এই জগত দেখার মানসেই একবার কুলাউড়া থেকে সংগ্রামের সময় আখাউড়া গামী মিস্ ট্রেন এ করে লংলা গিয়ে নেমেছিলাম বড় মামা আমির আলীর সাথে উদ্দেশ্য ছিল পৃথিমপাশা নবাব বাড়ীর রাজা সাহেবের কাছে যাবো , বড় মামা আমাকে সাথে রাখতেন সম্ভাব্য বিপদ আপদে তার নিজের একটু সাহস বাড়ানোর লক্ষে ।
কিন্তু লংলা স্টেশনে নেমে বড় মামা সিদ্ধান্ত পাল্টে আমাকে নিয়ে হাটতে হাটতে পুর্বদিকে প্রথমে মনরাজ ,তারপর সুলতানপুর
এবং তারপরে দৌলতপুর ,আসামপুর ,
রবিরবাজারের পর পৃথিমপাশা নওয়াব বাড়ীর একটু উত্তরপুর্বে ঘরগাও সৈয়দ বাড়িতে সৈয়দ আনোয়ার সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলেন ,তিনি বর্তমানে ইহলোক ত্যাগ করেছেন , তার দুই ছেলে সৈয়দ রিপন ও সৈয়দ লিটন এবং দুই মেয়ে লিনা এ সাবিনা বিভিন্ন জায়গায় অবস্তান করছেন ।তিনি বিয়ে করেছিলেন ব্রাম্বনবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর ঊপজেলার নাসিরপুর সৈয়দ বাড়ীর সৈয়দ আবদুল নকীব এর কন্যা সৈয়দা ফরকুন্দা বিবিকে , এই আনোয়ার সাহেব একটু নীচুস্বরে কিন্তু অত্যানত্য দ্রুত কথা বলতেন , বড় মামা ও এখন বেচে নেই তবে সেদিন তার সাথে ছিলাম আমি সেই কথা স্পষ্ট মনে আছে । এই ঘরগাও এর সাথে সম্পর্ক হয় আরো অনেক পরিবারের বিশেষ করে আমানীপুরের শাহ সৈয়দ ইনামুল্লাহ এর নাতি সৈয়দ
আফতাব উদ্দিনের ভাগ্নী সৈয়দা আসিয়া খাতুন ( ডালই বিবিকে) বিয়ে করেন সৈয়দ মহিবুর নুর সাহেব , ডালই বিবি ছিলেন কুলাউড়া উপজেলার কৌলা (বড় বাড়ি) নিবাসী সৈয়দ সদরুল হোসেন ও হামিদুন নেছা চৌধুরীর কন্যা তাঁদের সন্তানগণঃ- ১) সৈয়দ মজিবুর নুর (কয়ছর),
২) সৈয়দ মাহবুবুন নুর (আফছর), ৩) সৈয়দা সামসুন নাহার (মমতা), ৪) সৈয়দা নাজমুন নাহার (মায়া) ও ৫) সৈয়দা জেবুন নাহার (শেফা) ।এছাড়াও সারাদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে আত্বিয়তা রয়েছে এই বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যা অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য ।
পৃথিম পাশা ইউনিয়নের ছোট্ট একটি গ্রাম ঘরগাও , পৃথিমপাশা নওয়াব বাড়ির সামনে দিয়ে একটু সামনে উত্তর পশ্চিমে এগুলোলেই সেই ঐতিহ্যবাহী গ্রাম , এই গ্রামে একটি সাহেব বাড়ী রয়েছে যার গোড়া পত্তন হয়েছিল সৈয়দ শামসুল হাসানের মাধ্যমে , ইতিহাস ঘেটে জানা যায় বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই এস এম ইলিয়াসকে তিনি তার লেখা “সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরুদ্দিন (রঃ) সিলেট ও তরফ বিজয়ী “নামক গ্রন্থে অনেক পরিশ্রম করে অনেক অজানা তথ্য উপস্থাপন করেছেন ।
সৈয়দ শামসুল হাসানের পুর্বপুরুষ ছিলেন সিরাহসালার হযরত সৈয়দ নাসিরুদ্দিন (রঃ) , তিনি হবিগঞ্জের মুরারবন্দের নরপতি উত্তর হাবেলীর বংশধর সেখানকার ঘরগাও থেকে এসে পৃথিমপাশার প্রসিদ্ধ জমিদার নবাব আলী আমজদের পরিবারে বিয়ে করেন এবং জমিদারীর একাংশ পেয়ে এই খানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ।তার পূর্বপুরুষদের স্থায়ী বাসস্থান ঘরগাও য়ের নাম অনুসারে এই এলাকার নাম রাখেন ঘরগাও ।
এখনও নরপতি মুড়ারবন্দের পাস্বে অবস্থিত ঘরগাঁও এর সেই পুরোনো বাড়িটির নাম পীরের বাড়ী ।বর্তমানে সেই বাড়ীতে তাদের কোন বংশধর নেই , অন্য লোকেরা সেখানে বসবাস করছেন ।কিন্তু পীরের বাড়ী নামটি আজও মুছেনি । এই বাড়ীর সামনেই যুগের শ্রেষ্ট তাপস হযরত সৈয়দ ইলিয়াস কুতুবুল আওলিয়া (রঃ) বসে অজু করতেন সেই পাথর আজও বিদ্যমান ।পৃথিমপাশার পাশ্বে অবস্থিত ঘরগাও সাহেববাড়িও অনেক সুন্দর ।বাড়ির সামনে বিরাট দিঘী , প্রসস্থ মাঠ , মসজিদ বাংলো , ফুলবাগান সবকিছু মিলিয়ে অতি চমৎকার পরিবেশ ইত্যাদি ওয়াকফ স্টেটের অধিনে রয়েছে ।( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি -পর্ব – ২১ –( নর্তন সৈয়দ বাড়ি এবং সৈয়দ আকমল হোসেন)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কুলাউড়ার পুর্বদিকে ,দানাপুর দতরমুরি ,লষ্করপুর কামারকান্দি , ঘাগটিয়া ,রঙ্গীরকুল বিজয়া , দিলদারপুর, ক্লিবডন,গাজিপুর এবং এর আশে পাশের গ্রাম গুলোর ও চা বাগান গুলোর অনেক তথ্যই বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা ।যুদ্ধকালিন সময়ে যখন প্রথম গাজিপুর যাই সেই স্মৃতিও বেশ মধুর , রাস্তার দুইধারে ফসলের মাঠ , বড় বড় গাছ গাছালী পরিবেষ্টিত সড়ক , সেই সড়কটি ও ছিল পাথরের নুড়ি বিছানো , উচুনীচু রাস্তায় রিকশাই ছিল অন্যতম বাহন , বাগানের কিছু জীপ ও ট্রাক্টর ও মাঝে মাঝে চলতে দেখা যেতো , তবে সচরাচর সাইকেলে চড়ে ও পায়ে হেটে চলাচল করতে দেখা যেত বেশী ।, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদের লেখা “ইতিহাসের দর্পনে কুলাউড়া “নামক বইয়ে উল্লেখ রয়েছে “হযরত শাহ হেলীম উদ্ভিদ কুরেশী ও তোয়ারিখে সাহাবউদ্দিন পাশা নামক দুইটি বই থেকে জানা যায় , হযরত শাহাজালাল ( রঃ) এর নির্দেশে শাহ হেলীম উদ্দীন কুরেশী ( রঃ) নামে একজন দরবেশ লংলা পরগনায় এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন ।তিনি ছিলেন চৌকি পরগনার শাহ তাজ উদ্দিন কুরেশীর ভাই ।সেই সময়ে লংলা অন্চলে পাহাড়ীয়াদের প্রাধান্য ছিল ।লংলা অন্চলটি তখন নামে মাত্র সিলেটের অধীন ছিল , সিলেট তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল যা ত্রিপুরার রাজার কর্তৃত্বে ছিল ।
তখন শাহ হেলিম উদ্দিন কুরেশী লংলার একটি পাহাড়ীয়া এলাকায় ভয়ংকর স্থানে বসবাস শুরু করেন ও আরাধনায় নিমগ্ন হন ।জনশ্রুতি আছে একদিন সকালে বনের মধ্যে শাহ হেলিমউদ্দিন রোদ পোহাচ্ছিলেন তাকে ঘিরে ছিল বেশ কয়েকটি বাঘ ।এই দৃশ্য দেখামাত্রই আশেপাশের লোকজন সকলে ভয়ে এই এলাকা ছেড়ে লুসাই পাহাড়ের দিকে চলে যায় ।একদিন এক অসুস্ত রোগাকান্ত হিন্দু মহিলা এই দরবেশের কাছে এসে তার কাছে রোগথেকে মুক্তি কামনা করেন । তিনি তখন আল্লাহ পাকের নামে নিজের হাতের একটি ফল খেতে দেন । ফলটি খেয়ে কিছুক্ষনের মধ্যেই মেয়েটি সুস্ত হয়ে উঠে । পরবর্তীতে ঐ মহিলাটি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করলে হযরত শাহ হেলীমউদ্দিন কুরেশী তাকে বিয়ে করেন । ওয়েজউদ্দিন এবং তয়েজউদ্দিন নামে তাদের দুইটি ছেলে সন্তান ছিল ।
দরবেশ হযরত শাহ হেলীম উদ্দিন কুরেশীর মৃত্যুর পুর্বেই তার অধিকারভুক্ত জমির মধ্যাংশে একটি বিশাল দীঘি খনন করে ঐ দীঘির উত্তর অংশ ওয়েজউদ্দিন এ
দক্ষিন অংশে তয়েজউদ্দিন কে ভাগ করে দেন , এই দীঘিটি হদের দীঘি নামে আজও পরিচিত ।ঐ দীঘির পাশ্বে শাহ হেলীম উদ্দিন কুরেশীর মাজার রয়েছে ।বর্তমান কুলাউড়া রবিরবাজার রাস্তার পশ্চিম পাশ্বে ও ফানাই নদীর দক্ষিনে এই মাজার ও দীঘির অবস্তান । শাহ হেলীম উদ্দিন কুরেশীর অধঃস্তন বংশধরদের মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন এই বংশের অনেকেই কিয়াতলা,কাদিপুর,জয়পাশা,
নজাতপুর , রাউৎগাও , কর্মধা, পৃথিমপাশা, ঘাগটিয়া প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন ।জনশ্রুতি আছে ওয়েজউদ্দিন ও তয়েজউদ্দিনের মধ্যে জমি ভাগ হবার পর এর উত্তরাংশ উত্তরভাগ পরবর্তীতে উত্তর লংলা এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণভাগ পরবর্তীতে দক্ষিন লংলা নামে পরিচিত হয় ।
ওয়েজউদ্দিনের পুত্র বুরহান উদ্দিন তার একমাত্র চাচাতো বোনকে বিয়ে করেন ।বুরহান উদ্দিন ও নুরউদ্দিন সময় সিলেটের শাসনকর্তার সাথে ত্রিপুরার রাজার বিরোধ বাধে ।সিলেটের শাসনকর্তার পক্ষে বুরহান উদ্দিন ও নুরউদ্দিন বীরত্ব দেখান ।এই কারনে দিল্লীশ্বর তাদেরকে “খান ই খানান “ উপাধী দান করেন ।নুরউদ্দিনের পুত্র জালালউদ্দিন , দরিয়া উদ্দিন ও বরকতউদ্দিনের মধ্যে জালাল উদ্দিন একজন বিখ্যাত ব্যাক্তি ছিলেন ।
দিল্লির রাজ দরবার থেকে তিনি “মজলিশ জালাল খান “ হিসাবে ভুষিত হন ।তার পুত্র গওহর খাঁ , গহর খাঁর পুত্র গাজি খান সৌখিন বাঘ শিকারী ছিলেন । দিল্লীর জনৈক শাহজাদা একবার শ্রীহট্ট বেড়াতে এলে গাজি খান তার শিকারের সঙ্গী হন ।তারা গভীর জংগলে শিকারের অপেক্ষা কালে হটাৎ একটি বাঘ এসে তাদেরকে নিয়ে আসা হাতিকে আক্রমন করে বসে ,তখন গাজি খান অসীম সাহসের সাথে বাঘটিকে উপর্যপুরি গুলি করে হত্যা করেন।শাহজাদা দিল্লী ফিরে গিয়ে উক্ত ঘটনা সম্রাটকে জানালে , সম্রাট গাজি খানকে ‘গাজি শের খান ‘ উপাধী দিয়ে একটি সনদ পাঠান । এই গাজি খানের নাম অনুসারেই গাজিপুর নামটি হয়েছে ।সেখানে তার মাজার রয়েছে ।
উল্লেখ্য হযরত শাহ হেলীম উদ্দিন নারলুলী নামে আরও একজন দরবেশ কুলাউড়ার পাহাড়ীয়া অন্চলে মনু নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করে ধর্ম প্রচার করেন ।তিনি তার অলৌকিক ক্ষমতা বলে তৎকালে হিন্দু রাজা কর্তৃক তার রানী কনকরানী ও রাজকন্যা কমলা কে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত করে রাজ্যের অংশ বিশেষ প্রাপ্ত হন ।যা কনকহাটি বা কানিহাটী নামে পরিচিত ।ঐ বংশের অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের নিয়ে পর্যায় ক্রমে আগামীতে বিষদ আলোচনা করার আশা রয়েছে ।
কুলাউড়া রবির বাজার রোডে শাহ হেলিম উদ্দিন (রঃ) এর মাজারের একটু দক্ষিনে নর্তন গ্রামের আমঝুপ এলাকায় রেল লাইনের পশ্চিমে রয়েছে সৈয়দ বাড়ী যা নর্তন সৈয়দ বাড়ী নামে পরিচিত নয়নাভিরাম এই বাড়িটি মুলত একজন পীর সাহেবের বাড়ী উনার নাম ছিল সৈয়দ আবুল বাশার মোহাম্মদ রেজওয়ান যিনি অত্র এলাকায় ‘রেজান পীর’ নামে সুপরিচিত । তিনি অত্যান্ত ধার্মিক ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন , তিনি আধুনিকতার ছোয়ায় পুর্ন একজন সাধক ছিলেন ।গতানুগতিক দাড়ি টুপি আলখেল্লা না পড়ে প্যান্ট শার্ট ,স্যুট পড়তেন ,তার পিতা সৈয়দ রমুজ আলীও অত্যানত ধার্মিক ও মজ্জুব ব্যক্তি ছিলেন । রেজান পীর সাহেব বিয়ে করেছিলেন আমার আব্বার এক মামাতো বোনকে ,মামা হবিগঞ্জের সুলতানশী হাবেলীর সৈয়দ আব্দুস সালাম সাহেবের ছোট মেয়ে সৈয়দা তহুরা আক্তার খাতুন কে ।সৈয়দ এ বি এম রেজওয়ান সাহেব সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে তিনি বাঘের সাথে কথা বলতেন , তাকে রাতের বেলা যখন খাবার খেতে দেওয়া হতো তিনি সেই খাবারটি কিছুটা দুরত্বে গিয়ে সাথে কাউকে নিয়ে বসে খেতেন এবং খাবার শেষে আর ঐ আগন্তুককে আর দেখা যেতো না গায়েব হয়ে যেতো , ভক্তরা দাওয়াত দিলে তিনি তা কবুল করতেন ।অনেকেরই দাবীতে তিনি এক সাথে কয়েক টি ভক্তের বাড়ীতে দাওয়াত খেয়েছেন , যা ছিল একরকম অবিশ্বাস্য । রেজান পীর সাহেবের মাজার ও মসজিদও ও সৈয়দ বাড়ি নামে একটি ডাকঘরও রয়েছে ।
পীর আওলীয়া পরিবেষ্টিত এই কুলাউড়ার এই নর্তন সৈয়দ বাড়ীর প্রধান ব্যক্তি সৈয়দ রেজওয়ান আলী ওফাত হন ১৯৭০ সালের ৬ ই ডিসেম্বর , ফলে ৭১ এর যুদ্ধচলাকালে এ বাড়ীর সকল সদস্য ঢাকাতে থাকায় আমি আর ছোট মামা মনির আলমকে নিয়ে একবার সেই বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে আসি । পরবর্তীতে তার কনিষ্ঠ ছেলে সৈয়দ এ বি এম মান্নান ও অত্যান্ত আমলদার ও ধার্মিক ছিল । বর্তমানে তার বড় ছেলে সৈয়দ এবিএম হান্নান এই বিশাল অবিভক্ত সৈয়দ বাড়ীর গদ্দীনশীন।
অত্যান্ত সুন্দর ছিমছাম ঐ সৈয়দ বাড়ীর সামনে দিয়ে সংগ্রামের সময় ট্রেনে করে যাবার কালে অনেক বার চেষ্টা করেছি লংলা ষ্টেশনে নেমে ,ঐ বাড়ীতে যাবার কিন্তু যাওয়া হয়নি ।পরবর্তীতে বহুবার গিয়েছি এবং নর্তন সৈয়দ বাড়ীর প্রচুর স্মৃতি বয়ে চলেছি যা বলে শেষ করতে পারবো না হয়তো ।
বড় কাপন নামের একটি গ্রাম এই কুলাউড়ার ইতিহাসের অগ্নীস্বাক্ষী হয়ে আছে কারন এই বড়কাপনেরই ছেলে হচ্ছেন “ সৈয়দ আকমল হোসেন ।”
সৈয়দ আকমল হোসেন নাম মনে হতেই একজন জন্মবিদ্রোহী মানুষের কথা মনে পড়ে। মনে হয় জন্মেই এ মানুষ যেন, কমরেড লেনিনের ভাষায় সমাজটাকে পা উপর দিকে এবং মাথা নিচু দিকে দিয়ে উল্টোভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। মনে হয় সমস্ত উলট-পালট করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েই তাঁর জন্ম। প্রয়াত কমরেড তারা মিয়া এবং কমরেড আসাদদর আলী ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের কাজে বেরিয়েছিলেন । কমরেড আসদ্দর আলীর ভাষ্যে যা বিভিন্ন যায়গায় প্রকাশিত হয়েছে , তিনি বলছেন “কুলাউড়ামুখী হওয়ার সাথে সাথে তারা মিয়া বললেন, আকমল হোসেনকে নিশ্চয়ই কুলাউড়ায় পাব। আরও বললেন, সে মুসলিম লীগের দুর্দান্ত কর্মী ছিল। আমি মুসলিম লীগে ছিলাম না। মুসলিম লীগের যে কয়েকজন নেতা এবং কর্মীর সাথে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক তারাও কমিউনিস্ট মার্কা। খাঁটি মুসলিম লীগের দুর্দান্ত কর্মী সম্বন্ধে আমার খুব আগ্রহ থাকার কথা না। তারা মিয়ার কথায় বেশী উৎসাহ বোধ করলাম না।
কুলাউড়া পৌঁছে সৈয়দ আকমল হোসেনের সাথে দেখা হল। তাঁর সঙ্গে পাকিস্তান ডান পত্রিকার বর্তমান নির্বাহী সম্পাদক মজিদ সাহেবও ছিলেন। এক যুবককে দেখিয়ে তারা মিয়া বললেন এই হচ্ছেন সৈয়দ সাহেব। তরুণ বয়সে মুখভরা চাপ দাঁড়ি, সরস সোজা দেহ যষ্টি। অশান্ত উদ্যত বাচন ভঙ্গী। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সহসা মনটাই যেন উদ্দাম আবেগে বেরিয় আসছে। চলার ভঙ্গীতে কোন বাধা মানবো না ধরনের নাজরুলিক এক বিমুক্ত ছন্দ। দেখেই মনে হল একজন নতুন মানুষ দেখা হল। কমরেড আসাদ্দর আলী বলছেন “আমার মারাত্মক ত্রুটি ,প্রথম সাক্ষাতেই পরিচয় দূরে থাক্, হৃদ্যতা করা আরও দূরে থাক, সাধারণ কথাবার্তা বলতেও আড়ষ্টতা বোধ করি। কিন্তু সৈয়দ আকমল আমার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর হাতে পড়ে আমার আড়ষ্টতা বিপন্ন হয়ে পড়ল। প্রশ্নের পর প্রশ্নের বান ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাকে ঘর্মাক্ত, রক্তাক্ত করে তিনি যখন আবিষ্কার করলেন যে, আমি পাকিস্তান আন্দোলনের মত পূতঃ পবিত্র মহান কর্মে শরীক ছিলাম না, তিনি স্বস্তিই বোধ করলেন। বললেন, এই জন্যই এতদিন আপনার সাথে সাক্ষাত হয়নি। অর্থাৎ আমি সিলেট জেলার একজন জলজ্যান্ত মানুষ হয়েও সৈয়দ আকমলের সঙ্গে পরিচিত নই। এমন বিষ্ময়কর অবস্থাটা এতক্ষন তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। পরবর্তী সময়ে দেখেছি সৈয়দের অপরিচিত মানুষ এই জেলাতে সত্যিই বিরল ছিল।
আমরা অনেক সময় সভা সমিতিতে নীরবে নিভৃতে থেকে প্রায় অদেখা অজানা অবস্থায় যাওয়া আসা করতে পারতাম। কিন্তু সৈয়দ আকমলের উপস্থিতি যে কোন আসরে তাঁকে মনে রাখার মত করে সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন না করে পারতো না।
ছাত্র আন্দোলন, রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন, যুবলীগ সংগঠন, কৃষক শ্রমিকের সংগ্রাম, যুক্তফ্রন্টের কাজকর্ম সহ বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগঠনে সৈয়দ আকমল হোসেনের সঙ্গে আমরা যারা কাজ করেছি সকলেই তাঁকে একটু সমীহ করে চলতো । কাজ কর্মের ফাঁকে ত্র“টি বিচ্যুতি চোখে পড়লে ক্ষমাহীন আক্রমণ। প্রগতিশীল আন্দোলনে বৃহত্তর সিলেট জেলায় কুলাউড়া ও শমসেরনগরকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট কর্মী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। রাজা সাহেব, সালাম সাহেব, সৈয়দ আকমল, সৈয়দ ছয়ফুল হোসেন এবং মফিজ আলীই এই বাহিনীর সেনাপতি মন্ডলীর ভূমিকা পালন করতেন। মফিজ আলী বয়সে সকলের ছোট হলেও সাংগঠনিক কাজে বিশেষতঃ শ্রমিক কৃষক সংগঠনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রাজা সাহেব এবং সালাম সাহেবও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। সৈয়দ সাহেবের কাজ ছিল সর্বব্যাপী। তাঁকে ছেড়ে কোন কাজই যেন পূর্ণ হতনা। ডাঃ পবন, সৈয়দ বশির আলী, মোঃ আজম, তাহির মাষ্টার, শরীফ উল্লাহ ভাই, আবু কায়সার খান, সীতারাম বর্মন, রাধাকিষণ কৈরী, বেচু হরিমন, আজির উদ্দিন খান, আব্দুল মালিক, তাহির আলম, পংকুমিয়া, সুনীল লৌহ, আফজন, শিশির দে, ফৌরদৌস, স্বপন, ছাত্রনেতা শফকাতুল ওয়াহেদ, গজনফর আলী প্রমুখ কর্মীর বয়সের ব্যবধান যতই থাকুক, সৈয়দ আকমল যখন একসঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করতেন মনে হতো একটি বিরাট পরিবারের কয়েকজন ভাই যেন একত্রে বসেছেন। সৈয়দ সাহেব যেন সকলের বড় ভাই। ভাষা আন্দোলনের পর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কমিউনিস্টরা যুক্তফ্রন্ট গঠন করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তখন কমিউনিস্টরা পার্টির নামে প্রকাশ্যে একটি ছোট টিম রেখে আওয়ামীলীগ ও গণতন্ত্রী দলের ভিতরে থেকে কাজ করার কৌশল গ্রহণ করেন। আসদ্দর আলীরা আওয়ামীলীগে এবং অন্য কয়েকজন গণতন্ত্রী দলে কাজ করতেন। সৈয়দ আকমল গণতন্ত্রী দলে। কিন্তু পার্টি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সকলেই সুশৃংখলভাবেই পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেন ।যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পরে ৯২(ক) ধারা জারী করে প্রায় আড়াই হাজার রাজনৈতিককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দু’ভাগ হয়। কমিউনিস্ট পার্টিরকে বেআইনী ঘোষনা করা হয়। কিছুদিন আত্মগোপনে থাকার পর মনিরউদ্দিন সাহেব এবং কমরেড আসদ্দর আলী এক সঙ্গে ধরা পড়ন।মনির উদ্দিন সাহেব গণতন্ত্রী দলের জেলা কমিটির সম্পাদক। মাহমুদ আলী সাহেব তখন লোকদের ডেকে নিয়ে পৃথকভাবে আলাপ আলোচনা করতেন। আকমল হোসেন তাঁর খুবই ঘনিষ্ট লোক ছিলেন। পার্টির পক্ষ থেকে আসদ্দর আলীকে সৈয়দ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়।
সৈয়দ সাহেব প্রথমে পার্টির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে পার্টির লেজুর বৃত্তি ছাড়াই কাজ করা উচিত ছিল। পার্টির কৌশল সম্পর্কে তাঁকে ব্যাখ্যা করা হলে তিনি অবশেষে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হন। অনেকের ধারণা ছিল সৈয়দ সাহেব কোন নিয়ম মানেন না। কিন্তু জনশ্রুতি আছে , অনেকের মতে সৈয়দ সাহেব বিদ্রোহী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বিশৃঙ্খল ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সৎ, নিয়মনিষ্ঠ, রুচিবান ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনতার প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামের পুরোভাগে সৈয়দ আকমল হোসেন ছিলেন। রাজাসাহেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। রাজা সাহেব তাঁর নিজের সঙ্গে সৈয়দ সাহেবের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রায়ই সরস ভাষায় বলতেন, একদিন তাঁর সম্মুখ দিয়ে কট কট আওয়জ তুলে দ্রুতগতিতে একজন লোক বেপরোয়াভাবে ‘হায়দার মঞ্জিলে’ প্রবেশ করেন। তাঁর ব্যতিক্রমর্ধী গতিবিধিতে রাজাসাহেবের মনে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। ফেরার পথে তিনি আগন্তুককে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কোথায় কার কাছে গিয়েছিলেন? উত্তরে আগন্তুক তার নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বলেন, “আমি হায়দার খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এলাম।” রাজা সাহেব অবাক বিষ্ময়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন, আমি এই সর্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে আব্বা হুজুরের নাম উচ্চারণ করতে শুনলাম। এই বাড়িতে রেওয়াজই ছিল বড় হুজুর-ছোট হুজুর, বলে তছলিম করে এই বাড়ির পুরুষদের উল্লেখ করা।
পরবর্ত্তী সময়ে যতটি আন্দোলন হয় তার সঙ্গে সৈয়দ সাহেব কোন না কোন ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে ফুলবাড়ী নামক স্থানে পৃথ্বিমপাশা কৃষি খামার সম্প্রসারনের জন্য কৃষকদের উচ্ছেদ শুরু হয়। হাতি দিয়ে কৃষকদের ঘরবাড়ি ভাংগার জন্য জমিদারের বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। রাজা সাহেব, সৈয়দ আকমল, তারা মিয়া, সৈয়দ সাইফুল হোসেন প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে কৃষক সমিতি প্রতিরোধ গড়ে তুলে। আন্দোলনের চাপে তৎকালীন সরকার জমিদারদের মাহফিজখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং সেই স্থানে পুলিশ ক্যাম্প বসায় জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে।
১৯৫৬ সালে রেলওয়ে ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে সৈয়দ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৭ সালে বড়লেখার ধামাই চা বাগানের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। সিলেটের ৮৭টি চা বাগানের শ্রমিক এই ধর্মঘটে প্রতি সমর্থন জানায়। ধর্মঘট ১৪দিন চলে। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটের শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে। বাহির থেকে ধামাই এর শ্রমিকদের জন্য খাদ্য সাহায্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ এবং ই, পি, আর সকল সড়ক পথ অবরোধ করে রাখে। তখন মফিজ আলী, আবু কায়সার খান, সুনীল লোহ, পংকু মিয়া প্রমুখ সহযোগে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির টিমই চা শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বে ছিলেন। জেলা কেন্দ্র থেকেও পার্টি নেতারা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। রেলযোগে খাদ্য সরবরাহ করে ধামাই অবরোধের প্রতিবিধান চিন্তা করা হয়। ধামাইয়ে রেল ষ্টেশন ছিল না। রেল কর্মীদের উপর সৈয়দ সাহেবের বিরাট প্রভাব ছিল। তাঁর সাহায্যে ধামাইয়ের নিকট রেল থামানোর ব্যবস্থা করে খাদ্য দ্রব্য ফেলে দেয়া হত। সেখান থেকে মহিলা শ্রমিকগণ কাপড়ের আঁচলে করে চাল ডাল গোপন পথে বাগানে নিয়ে যেতেন।
১৯৭০ সালে নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রের (?) অপরাধে অন্যান্যদের সঙ্গে সৈয়দ সাহেব এবংকমরেড আসদ্দর আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে সেই সময়ে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন নেতা আসদ্দর আলীর উপর খুব বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাদের অভিযোগ ছিল (১) সোভিয়েত রাশিয়া সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলে আসদ্দর আলী বিশ্বাস করতেন না না। (২) তিনি নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন । (৩) কমরেড চারু মজুমদারের লাইন সঠিক মনে করতেন না। (৪) তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্খাই প্রধান জাতীয় প্রবণতা ছিল বলে কমরেড আসদ্দরের ধারণা ছিল সৈয়দ আকমলও কমরেড আসদ্দরের প্রতি এই অভিযোগ বিরুপ ছিলেন। জেলে প্রথম আলাপেই তিনি অকপটে এ কথা স্বীকার করেন। তিনি মুখ কাটা বলেই সবাই জানতেন। আসদ্দরকে কিছু কাটা কাটা কথাও তিনি শুনান। তাঁর অভিযোগের উত্তরে কমরেড আসদ্দর বলেছিলেন “আমার বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগগুলো সত্য। কিন্তু এতে আমার দোষ কোথায়? আমার বিশ্বাস বা ধারণার কথাতো আমি নির্দিষ্ট ফোরামের কাউকে বলিনি। দ্বীতিয়তঃ আমি পার্টির নিয়ম শৃংখলার বিরোধী কোন কাজ করেছি বলে পার্টি থেকে আমার বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ তো আনা হয় নাই। আমার কথায় বিশ্বাসগুলোর পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি না দেখিয়ে ১৯৬৯ সালের বাস্তব অবস্থা এখানেও বর্ণনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি।
ষাট দশক থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা ‘মস্কো লাইন’ ও ‘চীনা লাইন’ এর পথ ধরে বিভক্ত হয়ে দুই বিপরীত ধারায় কাজ করেছেন। এই দশকের শেষ দিকে দুই ধারার অনুসারীদের বিশেষ করে কৃষক শ্রমিক ছাত্র বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের মন মানসিকতা বিরাজ করছিল।
১৯৬৯ সালে সমশেরনগর চা বাগানের শ্রমিক কর্মী নীরাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। খবর পেয়ে গভীর উৎকন্ঠা নিয়ে সবাইসসিলেট থেকে রওয়ানা হয় কিন্তু সমশেরনগর পোঁছেই দেখে এলাহী কান্ড। হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক পাহাড় কামলা ও ছাত্র কর্মীদের সমাগমে শোভাযাত্রার শ্লোগনে সমশেরনগরে সেদিন সংগ্রামের জোয়ার ডেকেছিল। সৈয়দ আকমল তখন জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক। শ্রমিক নেতা সৈয়দ আকমল হোসেনের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে দূর্বার দুর্ণিবার জনসংগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সেদিন সমশের নগরে তৈরী হয়েছিল। তার সঙ্গে জেলার আন্দোলন সংগ্রামের যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন ছিল। চীন সোভিয়েত বিরোধের দিকে না তাকিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সকল কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি সকল শ্রেণী সংগ্রামের স্রোতধারার গতিমুখ সার্বিক মুক্তির দিকে প্রবাহিত করতে পারতেন তখন সকল গণতন্ত্রকামী ও স্বাধীনতাকামী শক্তিকে সংগঠিত করা সম্ভ হতো। মাওলানা ভাসানী সহ জাতীয় নেতারা তখন কমিউনিস্টদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপনকে পূন্যের কাজ মনে করতেন। সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন জানাত।কমরেড আসদ্দরের আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই সৈয়দ সাহেব বললেন, “আপনি আপনার কথা পার্টির কাছে লিখিত ভাবে জানান।” এই বলে নিজস্ব ভঙ্গিতে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গিয়ে তিনি অন্যান্য কাজে লেগে গেলেন।॥জেলেও তাঁর এক মুহুর্ত অবসর থাকার জো ছিল না। জেলে ফল ফুলের বাগান ও সব্জী বাগানের কাজ কর্ম ছাড়াও কয়েদীদের বিভিন্ন কাজ করতেন তিনি ১৯৭১ সালে সংবাদের আহমেদুল কবির সহ আবার গ্রেফতার হন এবং ছাড়া পান । সংগ্রামের সময় চাপের মুখে বিতর্কিত ভুমিকার জন্য ৭২ সালে আত্মগোপন করেন ।১৯৮৫ সালে ৩০ শে জানুয়ারী সদাহাস্য উজ্জল এই সংগ্রামী নেতা ইহলোক ত্যাগ করেন । ( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি ,পর্ব-২৯ (রাউৎগাও )
সৈয়দ শাকিল আহাদ
অনেক দিন পর আবারও আজ
কি মনে করে জানি লিখতে বসলাম , কত কথাই না মনে পরছে , লিখতে ইচ্ছা করছে কিন্তু ঐ একটাই সমস্যা কোনটা রেখে কোনটা লিখি ? আল্লাহ পাক রাব্বুল আলাআমিন এর কাছে লক্ষ কোটি শুকরিয়া তিনি আমাকে এই সময়েও লেখার ধৈর্য ও স্মৃতি শক্তি প্রখর করে দিয়েছেন যার আলোকে সংগ্রামের ৫২ বছর পরও কিছুটা স্বরন করে ,আবার কিছুটা নানা জনের কাছ থেকে জেনে ,নিজের জানা অংশটুকু সাথে পরখ করে এবং বিভিন্ন সুত্র ও গবেষকদের তথ্য স্মবলিত প্রকাশিত বই থেকে জেনে এর সত্যতা যথার্থভাবে যাচাই করে
আবার আমার মত করে লিখছি ,
“একাত্তরের স্মৃতি “
অনেকটা নেশার মত ।
এ নেশায় মত্ত হওয়া মানেই হচ্ছে নিজেকে ঐ একাত্তর সালে নিয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধ কালীন সময়ের ঘটে যাওয়া ঘটনাসমুহ যা এখন ‘গল্প’ তাই চোখের সামনে স্পস্টাকারে ভাসিয়ে তোলা ।
বার বার ঘুরে ফিরে কুলাউড়ার কথাই মনে পড়ে , স্মৃতির পটে চলে আসে ‘কুলাউড়া ‘ ।
কুলাউড়া থেকে দক্ষিন দিকে পৃথ্থিমপাশা কর্মধা হাজিপুর শরীফপুর ইত্যাদি হয়ে ভারতের কৈলাশটিলা যাবার পথটির কথা এই মুহুর্তে একটু বেশীই মনে পড়ছে ,ঐ পথটাই চোখের সামনে চলে আসছে ।
কুলাউড়ার স্কুল চৌমুহনী পেরিয়ে রেল ক্রসিংয়ের পর একটু এগুলেই পড়ে চৌধুরী বাজার ।এই বাজারের দোকান পাঠ বা জনগন এখন আর আগের মত নেই , আধুনিকতার ছোয়ায় আমুল পরিবর্তন এসেছে এই বাজারে ও আশে পাশের এলাকা সমুহে , অতি সম্প্রতি চোখে পড়লো একটি মসজিদ ,যা এই বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদুর আমেরিকাতে অবস্তান কারী কৌলার জুবেদ চৌধুরীর ছেলে বড় ছেলে রাসেদুল চৌধুরী হেশাম , কুলাউড়ার লিটন আহমেদ ওরফে ডাকবাংলোর লিটন এবং লন্ডন প্রবাসী তাহরাম চৌধুরী সহ আরো বেশ কয়েক জন কুলাউড়ার প্রবাসী কৃতিসনতানের এবং বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কৌলার মরহুম জুবেদ চৌধুরীর ছোট ছেলে যিনি দেশে অবস্তান করছেন ,সেই মেজর নুরুল মান্নান চৌধুরী ( অবঃ) সহ স্থানীয় অনেকের সমন্বিত প্রচেষটায় ও তাদের সাথে দেশে বিদেশের আরো অনেক স্বজনের অর্থনৈতিক ও সার্বিক সহযোগীতার ফলে এই মসজিদটি নান্দনিক হয়ে উঠছে । অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাই এই প্রচেষটাকে ।
তাদের এই জাতীয় সমন্বিত উদ্দোগ এর ফলে এবং আরো অনেক উদার মনের মানুষের নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন এর পরিকল্পনার ফলে সমগ্র কুলাউড়ার পূরোনো মসজিদ সমুহের সংষ্কার ও উন্নয়ন এবং ঐতিয্য সংরক্ষনের চিত্র পরিবর্তন হওয়ার ব্যপারে আমি ভীষন ভাবে আশাবাদী ।
উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশ ও এখন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৈদেশিক বানিজ্য ,যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিস্তর এবং অকল্পনীয় উন্নতি লাভ করছে যার সুফল গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে ।
এই যেমন একাত্তরে এই রাউৎগাও এর উপরদিয়ে বয়ে যাওয়া রাস্তা অর্থাৎ কুলাউড়া রবির বাজার রোড পাকা ছিল না , পাথরের নুড়ী বিছানো ছিল , এলাকাতে বিদ্যুৎ ছিল না আর এখন গ্রাম পর্যায়ের অধিকাংশ ঘরেই , টিভি , ফ্রিজ. ও এসির ব্যবহার হচ্ছে আগে এসি কি জিনিষ তা কেউ চিনতো না তবে স্বাধীনতার পর দেখেছি কুলাউড়া রেল ষ্টেশনে মেইল ট্রেনের মাঝে একটা বগী থাকতো যার গায়ে বাইরে লেখা থাকতো “ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত” এবং প্লাটফর্মে ঐ বগী টিতে যখন কেউ উঠতো বা নামতো তখন তার চারপাশে ভীড় লেগে যেতো কারন ঐ বগীর যাত্রীরা থাকতেন কোন বিশেষ শ্রেনীর মর্যাদাসম্পন্ন ।
তাকে নিয়ে সবাই কৌতুহলী থাকতেন ।
এই চৌধুরী বাজারেই রয়েছে একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা যেখান থেকে নিয়মিত ছাত্ররা কোরআন শরীফ মুখস্ত করে হাফিজে পরিনত হচ্ছে ।
চৌধুরী বাজার মুলত রাউৎগাও ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত , আমার ফুপুর বিয়ে হয়েছিল রাউৎগাও এর নর্তন সৈয়দ বাড়ীতে , ফুপুর দুই ছেলের মধ্যে অত্যান্ত পরহেজগার ছিল ছোটভাই সৈয়দ এ বি এম মান্নান ,অনেক আদরের সেই প্রয়াত ফুপাতো ভাই মান্নান এর বাড়ীতে যাওয়া আসার সময় রাস্তায় পরতো এই রাস্তাটি ,চৌধুরী বাজারটি । তাছাড়া এই রাস্তা ধরেই যাওয়া আশা করেছি আমাদের সম্ভ্রান্তআত্বীয় স্বজনদের বাড়িতে, বিশেষ করে পৃথ্থিমপাশা, ঘরগাও,পাল্লাকান্দি,আমানীপুর ,কানিহাটি,কৌলা ইত্যাদিতে । এই রাউৎগাও ইউনিয়নের আশে পাশের অনেক গ্রামেরই বাজার সদায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল এই ছোটখাটো বাজার , চৌধুরী বাজার তথা রাউৎ গাঁও ইউনিয়ন , এই ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ,
কৌলা,নর্তন , মুকুন্দপুর মৈশাজুড়ি,মনরাজ, হাসামপুর,মিনারমহল , আব্দুলপুর ,একিদত্তপুর, লালপুর,কালিজুড়ি ,বনগাও, আবদা, সজরকান্দি ,নজাতপুর,কৃষ্নপুর , পাল গ্রাম ,বাগাজুড়া,রুস্তমপুর, কবিরাজি, বড়বাড়ী,ভবানীপুর, বনগাও,ভাটুগ্রাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।
শিক্ষাক্ষেত্রে কুলাউড়ার অন্যান্য ইউনিয়নের তুলনায় এই রাউৎগাও ইউনিয়ন অনেকটা এগিয়ে এখানকার “ রাউৎগাও হাই স্কুল “ নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মিত হয় ১৯২৮ সালে এই অন্চলের অনন্য দানবীর জনাব আব্দুর রহিম চৌধুরী এই স্কুলের জন্য ২৮ বিঘা জমি ওয়াকফ করে দেন তখন এই শিক্ষা প্রতিষঠানটির নাম ছিল “ রাউৎগাও এম ই মাদ্রাসা , ১৯৫৩ সালে তা জুনিয়র স্কুলে রুপান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে যখন আব্দুর রহিম চৌধুরী সাহেবের ছেলে জনাব আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী কুমিল্লার জেলা প্রশাসক ছিলেন তখন তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্কুলটি হাই স্কুলে রুপান্তরিত হয় এবং বর্তমানে কলেজ শাখা ও চালু আছে ।জনাব ইয়াহিয়া চৌধুরী প্রশাসনিক দক্ষতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক হিসাবে অত্যন্ত্য সুদক্ষতার সাথে কর্তব্য পালন করে সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচীব হিসাবে অবসর গ্রহন করেন এবং পরবর্তীতে বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর একান্তসচীব হিসাবে ছিলেন ১৯৯৬-২০০১ সেশনের পুরোটা সময় ধরে । বর্তমানে তিনি অবসরে আছেন ,তিনি একজন সংগঠক, কবি , লেখক ও অত্যানত উঁচু মানের সাহিত্যিক ।
লংলা আধুনিক মহাবিদ্যালয় নামে একটি কলেজ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ইউনিয়নে , তা ছাড়া শাহাজালাল উচ্চ বিদ্যালয় নামে আরেকটি উচ্চ বিদ্যালয় ও স্থাপিত হয়েছে ১৯৯০ সালে ।চৌধুরীবাজার হাফিজিয়া মাদ্রাসা , রাউৎগাও গৌছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা , ভবানীপুর এবতেদায়ী মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য ।
৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে এই রাউৎগাও ইউনিয়নের অনেক দামাল ছেলেদের অনবদ্য সাহসীকতার কথা শোনা যায় , যারা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে জীবন বাজি রেখে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধে , এদের অন্যতম একজন হলেন রাউৎগাও গ্রামের শহীদ ডাঃ অক্ষয় কুমার চৌধুরীর ছেলে “ অনুপম কান্তি চৌধুরী , মুক্তিযাদ্ধা তালিকা নং ০৫০৪০৪০০০৫ ।তিনি ১৯৭০ সালে কুলাউড়া কলেজে ছাত্রাবস্তায় থাকাকালীন সময়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদিয়ে ট্রেনিং নেন ।তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়েছেন পরবর্তীতে নবাব আলী সারোয়ার খান চুন্নু ,আলাউদ্দিন চৌধুরী ও আব্দুল জব্বার মিয়ার উৎসাহে এবং অনুরোধে উন্নত ট্রনিংয়ের জন্য ভারতের পানিভরা ইয়থ ক্যাম্পে ২১ দিন ও লোহারবনে দীর্ঘ একমাস অস্রচালনা ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে , গাজিপুর, আলীনগর , কর্মধা,মুরইছড়া,পাইকপাড়া , শিলুয়া , চাতলাপুর সহ মৌলভীবাজারের বিভিন্ন স্থানে সম্মুখ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহন করেন ।শিলুয়ার সমিমুখ যুদ্ধে পাক বাহিনীর নিক্ষিপ্ত শেলের আঘাতে পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে ধর্মনগরে এবং পরবর্তীতে ভারতের কৈলাশহরে হাসপাতালে একমাস চিকিত্সাধীন ছিলেন ।
ক্রমেই সুস্ত হয়ে দেশে ফেরার পর জানতে পারেন অনুপম কান্তি যুদ্ধে যাবার দরূন তার বাবা ডাঃ অক্ষয় কুমার চৌধুরীকে তৎকালীন চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে একদল লোক এসে তাকে তুলে নিয়ে হত্যা করে ।
কিন্তু শহীদ দের নামের তালিকায় তার বাবার নাম নেই ।
উল্লেখ্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনের পর ,অনুপম কান্তি চৌধুরীর মাতা সুরুচী রানী চৌধুরীকে শহীদ পরিবার হিসাবে তখন দুই হাজার টাকার চেক আর্থিক সাহায্য হিসাবে প্রদান করেন ।
অপর আর এক মুক্তিযাদ্ধা এই রাউৎগাও ইউনিয়নের তিলাশিজুরা গ্রামের মোঃ ফজলের পুত্র আব্দুল মতিনের জন্ম ১৯৫২ সালে ,তিনি ১৯৭১ সালে মৌলভীবাজার কলেজে দ্বাদশ শ্রেনীতে পড়তেন । দেশকে শত্রূমুক্ত করতে তিনিও যুদ্ধে সক্রীয় ভাবে অংশগ্রহন করেন । তার মুক্তিযোদ্ধা ক্রমিক নং -০৫০৪০৪০১১৬ ।
১৯৭১ সালের মার্চমাসে প্রতিরোধ সংগ্রামীদের দ্বারা শেরপুরে ডিফেন্স গঠন করা হলে তিনি তখন সেখানে খাদ্য সরবরাহের মত গুরুত্বপুর্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হন ।এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে এসে তখন যখন ঐ প্রতিরোধ বাহিনী বিভিন্ন ভাবে জেলার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পরে এক কথায় ভেংগে যায় ।আব্দুল মতিন তখন কুলাউড়ায় চলে আসেন এবং এই অন্চলের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শীর্ষসংগঠক আলী সফদর খান রাজা সাহেব , এবং আলাউদ্দিন চৌধুরী , জুবেদ চৌধুরী সহ আরো বেশ কয়েক জনের সাথে যোগাযোগ করেন এবং পাকিস্তানীরা কুলাউড়া আসার ঠিক তিন দিন পর তাদের নির্দেশে মুরইছড়া সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের টিলাবাজার হয়ে কৈলাশহরে চলে যান ।ভারতের কৈলাশহরের টাউন হলে তখন মুক্তিসেনাদের ট্রেনিং ক্যাম্প , সেই ক্যাম্পে আব্দুল মতিন নিজের নাম লেখান , সেখানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জনাব ফারুক আহমদ চৌধুরী , ঐ ক্যাম্পে ১৮ দিন ট্রেনিং নেবার পর আসামের লোহারবনে আরো দেড়মাস উন্নত প্রশিক্ষন শেষে
৮ নং সেক্টরাধীন টিলাবাজার ক্যাম্পে ফিরে আসেন ।
সেখানে এসে সময়ে সময়ে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন ।
অল্প কিছুদিন পর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কৈলাশহর ক্যাম্পে ।মুক্তিযুদধের কথা বলতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়েছেন তার স্বরনীয় ঘটনার মধ্যে একটি হলো সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কর্মধা ইউনিয়নে পান্জাবীদের ক্যাম্প আক্রমন ।কোন এক শুক্রবারে এই অন্চলের আর এক সাহসী বীর আব্দুল গফুরের নেতৃত্বে ২৫ জন যোদ্ধা নিয়ে , যাদের মধ্যে সেই দলে ছিলেন মুকিত আহমেদ চৌধুরী , বাদশা , হারুন , মখলিছ সহ আরে অনেকেই ।
সেদিন আকছরাবাদ চা বাগান হয়ে কর্মধা ইউ পি অফিসে স্থাপিত পান্জাবীদের ক্যাম্পে হামলা চালানো হলে , পান্জাবীরা অতর্কিত আক্রমনে বিপর্যস্ত হয়ে গুলি করতে করতে পৃথিম পাশার দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রান বাঁচায় ।
আব্দুল মতিন আরো জানান সেদিন পাক সেনাদের ফেলে যাওয়া ৯টি রাইফেল ও কিছু বহনযোগ্য জিনিষ ছাড়া বাকি সবই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং সবাই আবার কৈলাশহরে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন ।
আব্দুল মতিন মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক গুলো আক্রমনের মধ্যে বিশেষ করে মনু ব্রীজ আক্রমন সহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন সুত্রের কাছে ।
মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিনের দেওয়া তথ্যমতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই রাউৎগাও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুক্তিকামী মানুষের ও তাদের পরিবারের উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন তৎকালীন দূর্যোগময় সময়ে ।
উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে সর্বত্র স্বরনীয় যে ,ঐ বাউৎগাও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ভাটগাওয়ের নিরঅপরাধ আব্দুল গফুরের ছেলে মোঃ ছগির আলীকে নিজ হাতে খুন করেন , ছগির আলীর অপরাধ ছিল তিনি মুক্তিবাহিনীকে সহযোগীতা করেছিলেন ।আরো একটি ঘটনা ও মুক্তিযুদধের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম , ঐ চেয়ারম্যান কোন একদিন মনরাজ গ্রামের বশির মিয়াকে নিজ হাতে হত্যা করে ,হত্যার পর ফতোয়া জারি করেন যে , এই লাশ ছোবল না ,
এই কবরস্থানে দাফন করলে কবর অপবিত্র হয়ে যাবে ।
অনেক অনেক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন এই রাউৎগাও এ যাদের কথা লিখে শেষ করা যাবেনা , তবে দুই একজনের কথা না লিখলেই নয় তাই একটু চেষ্টা করলাম কিছুটা জানাতে । এই ইউনিয়নের অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের নাম এ তাদের অবদানের কথা বিভিন্নভাবে , বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে উঠেছে , যেমন এই মুহুর্তে রাউৎগাওয়ের অনেকের কথাই মনে পড়ছে , তেমনিএকজন হচ্ছেন আলাউদ্দিন চৌধুরী ,তার পিতার নাম আব্দুল বারী চৌধুরী , মুক্তিযোদ্ধা ক্রমিক নং ০৫০৪০৪০১৩৫ অন্যজন হলেন সৈয়দ আমজদ আলী , পিতা সৈয়দ রমুজ আলী , যতদুর জেনেছি তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার । এরা দুজনেই রাউ্ৎগাওয়ের এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন এবং অনবদ্য ভুমিকা রাখেন ।
রাউৎ গাঁও এর আলাউদ্দিন চৌধুরীর অবদান ও ত্যাগ অনস্বীকার্য , পাক বাহিনী এদেশে আসার পর আলাউদ্দিন চৌধুরী ভারতে গিয়ে অস্রচালনা ট্রেনিং নেন ও ফিরে এসে সরাসরী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন । এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সফল সংগঠক ও স্বেচছাসেবক ছিলেন তিনি , তার স্ত্রী জোহুরা আলাউদ্দিন বর্তমান জাতীয় সংসদের এই জেলার মহিলা সংসদ সদস্য।
আরও একজনের কথা বিভিন্ন জনের কাছে বহু শুনেছি , তিনি ও একজন সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা , তার নাম মোঃ আজহার আলী পিতা মৃত আমজদ আলী , তিনি ১৯৭০ এর নির্বাচনে আএয়ামীলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন ।তার বাড়ী কৌলা , তিনিও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্নস্থানে সরাসরি যুদ্ধ করেন , তার মুক্তিসেনা নং ০৫০৪০৪০১৩৭।
অনেক অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মনে পড়ছে , যাদের কথা আগামীতে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে ।
কিছু ঘটনার সত্যতা মিলিয়ে দেখেছি এই কুলাউড়ার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদের লেখা মুক্তি যুদ্ধ ভিত্তিক বই “ মুক্তিযুদ্ধে কুলাউড়া” বই এর সাথে । কৃতজ্ঞতা জানাই মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদকে , তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন সুন্দর একটি গবেষনার মাধ্যমে , তা না হলে হয়তো আমরা বা আমাদের আগামী প্রজন্ম কুলাউড়া অন্চলের মুক্তিযুদধের অনেক তথ্য পাওয়া থেকে বন্চিত হতো ।
তথ্য ও ছবি সংগ্রহে কৃতজ্ঞতায় ,
১) আ. ফ.ম. ইয়াহিয়া চৌধুরী
২)মেজর (অবঃ ) নুরুল মান্নান চৌধুরী
৩) ফাতেউল আলম সোহেল
৪) মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ
( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি — (৮) সৈয়দ শাকিল আহাদ
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ের দুর্দান্ত ঘটনাবহুল স্মৃতি ,বিশেষ করে সিলেট অন্চলের সীমান্ত ঘেষা চাবাগান পরিবেষ্টিত থানা শহর কুলাউড়ার উল্লেখ যোগ্য কিছু ঘটনার সাথে কিছু লোকের নাম ও চেহারা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই চোখের সামনে ভাসতে থাকে । তেমনি এক জন হলেন রাজা সাহেব ,যেহেতু তখন আমার বয়স কম , বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন হয়নি তবে ‘রাজা’বলতে , সেই এলাকার প্রধান ব্যাক্তি কেই বুঝতাম । মজার ব্যপার হলো রাজা সাহেব যেদিন কুলাউড়া আসতেন , সেদিন আমি আমাদের উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ি থেকে দৌড়ে ফিল্ডের পশ্চিমে বটগাছের নিচে গিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম কখন তিনি এই বড় রাস্তা দিয়ে ফিরবেন , তাকে একনজর দেখবো তার বহর সহ , অপেক্ষা করতে করতে কখন বেলা গড়িয়ে যেত তা টের পেতাম না আর রাজা সাহেবকেও দেখা হতো না ।তিনি কুলাউড়া আসলে মসজিদ সংলগ্ন রামগোপাল ফার্মেসির দোতালায় আড্ডা মারতেন , সকল রথী মহারথীর মিলন ঘটতো তখন সেখানে , মাঝে মাঝে থানার বিপরিতে ডাকবাংলায়ই বসতেন , তা ছাড়া মোবারক মিয়ার আজম বোডিংয়ে বসতো তাদের আড্ডা ।কুলাউড়াতে সেদিন পাকিস্তানী মিলিটারীদের আগমনের খবর পেয়ে পৃ্থিমপাশা ইউনিয়নের নবাব পরিবারের একাংশের অবাধ্য সদস্য রাজা সাহেবের চাচাতো ভাই মুসলীম লীগ নেতা নবাব আলী ইয়াওর খান দ্রুত দুইজন দূত মারফতে মিলিটারীদেরকে তার নিজ এলাকা পৃথিমপাশায় যাবার জন্য ,দূতদের নাম নাম সোনা মিয়া এবং আব্দুল খালেক বলে জানা যায় ,তাদের মারফতে দাওয়াত পাঠান ।
দাওয়াত পেয়ে ঐ মোতাবেক ক্যাপ্টেন দাউদের নেতৃত্বে চারটি জীপে করে ৭ ই মে বিকালে পাকবাহিনীর সদস্যরা রবির বাজার আলিনগর সীমান্ত ফাঁড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় ।
পাক সেনাদেরকে আলী নগর সীমান্ত ফাঁড়ীর দিকে রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে নবাব ইয়াওর আলী খান রবির বাজারে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন । মিলিটারীদের সাথে দেখা হওয়ার পর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে কিছু দিতে হয় মনে করে তাৎক্ষনিকভাবো রিক্সাচালক কুনুরকে তার জয়বাংলার খবর কি জানতে চাইলেই সে সালাম না দিয়ে গান শুরু করাতে তাকে ‘মুক্তিকামী ‘ উল্লেখ করে তাদের হাতে সোপর্দ করেন এবং নিজেও তাদের সাথে কুলাউড়ায় চলে আসেন । তিনি ছিলেন ঐ পরিবারের বেপরোয়া সদস্য ও পাকিস্তান পন্থী , অথচ ঐ নবাব বাড়ীরই প্রধান অংশের অন্যতম জনপ্রিয় সদস্য ছিলেন ,নবাব আলী সফদর খান ‘রাজা সাহেব ‘ অত্র অন্চলের যে সকল মানুষ , ও পরিবার পরিবার পরিজনদের নিয়ে সীমানা পেরিয়ে ভারতের কৈলাশহর , আগরতলা , কুকিশহর প্রভৃতি স্হানে ছিলেন , তিনি পরিবার সহ কৈলাস শহরে একমাস থাকার পর গৌড় নগরে , বর্তমানে জেলা শহর ছিলেন । তিনি পরিবারদের রেখে এসে কালাইজুড়ির নিজস্ব মুক্তি যোদ্ধার ক্যাম্পে থেকে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সেখান থেকে ভারত গামী শরনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও তাদের গমনপথে সর্বাত্তক সাহায্য সহযোগীতা করেন ।
লোকমুখে প্রচলিত আছে ওপারে যাবার পথে লুটেরারা অসহায় শরনার্থীদের কাছ থেকে মুল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে যেত এবং অনেক ক্ষেত্রেই রাজা সাহেব তাদেরকে লোক মারফত ধরে এনে শাস্তি দিয়েছেন ।আসাম প্রাদেশিক পরিষদের মন্ত্রী পৃথিমপাশার নবাব আলী হায়দার খানের বড় ছেলে নবাব আলী সফদর খান রাজা সাহেব জন্মেছিলেন ১৯১৯ সালে ,তিনি ছিলেন অত্যানত্য অমায়িক , গরীব দু:খী ও মেহনতী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথী, জমিদার পরিবারে জন্মালেও তার চাল চলন স্বভাবে জমিদারী দাপট ছিল না ,১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে অত্যানত্য গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করেন ।পাকিস্তানী মিলিটারীরা কুলাউড়া আসলে পরে বহুবার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ।কিন্ত তিনি বেঁচে যান , এবং বাড়ি ঘর ফেলে ভারতের আগর তলায় স্ত্রী পুত্রদের অন্যত্র রেখে নিজে থেকেছেন শরনার্থী ক্যাম্পে ।তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন জমিদার পিতার বিরুদ্ধে , অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে , ১৯৭৪ সালে তিনি মারা যান ।আমরা তার বিদেহী আত্বার শান্তি কামনা করি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাত নসীব করুন । আমিন ।( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি —(৫)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
স্মৃতি বড়ই মধুর আবার এই স্মৃতিই অত্যন্ত্য জ্বালাময় , ৭১ এর স্মৃতি কোন ভাবেই মধুর নয় অবশ্যই বেদনাদায়ক , যাদের আপনজন হারিয়েছে তাঁরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারে সেই ব্যাথা কতটা ভয়াবহ ?
আজ এতদিন পরে সেই একাত্তরের কথা লিখতে বসে মনটাকেও বানিয়ে নিতে হচ্ছে ঐ সময়ের শিশুসুলভ ।
অনেক অনেক জলজ্যান্ত ঘটনার মত দুই একটি ঘটনা না বলে আর পারছি না ।
ছোট্ট থানা শহর কুলাউড়াতে পাকিস্তানী মিলিটারীরা প্রবেশ করে মে মাসের ৬ তারিখ রাতে , শহরে ঢুকেই তারা কুলাউড়া হাসপাতালে ,গার্লস স্কুলে , পৃথ্বীমপাশা নওয়াববাড়ি ও নবীনচন্দ্র স্কুলে ক্যাম্প তৈরি করে । আর তাদের প্রধানেরা , ক্যাপ্টেন দাউদ এবং মেজর আব্দুল ওয়াহিদ মোঘল অবস্তান নেন কুলাউড়া থানার বিপরিতে ডাক বাংলোতে ।
ক্যাপ্টেন দাউদের অতি মাত্রায় নির্যাতন ও পাশবিকতার দরুন তাকে সারা কুলাউড়ার সবাই যমের মত ভয় পেত ।
নবীনচন্দ্র স্কুলের একপাশে ক্যাম্প
স্থাপন করে , স্কুলের শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিল ছাত্রদের এনে নিয়মিত ক্লাস চালিয়ে যেতে যাতে স্কুল কলেজ খোলা আছে এবং ছাত্ররা নিয়মিত স্কুলে আসছে তা বিশ্ববাসি বুঝতে পারে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ,ঐ সময়ে ছাত্ররা ভয়ে স্কুলে আসা বন্ধ করেছিল । তারপরও শিক্ষকগন ও আলবদর , রাজাকারেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুরোধ করতো স্কুলে আসার জন্য , ইতিমধ্যে অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছিল ওপারে , কেউ কেউ আবার দেশকে শত্রুমুক্ত করার তাগিদে ভারতে গিয়ে যোগদিয়ে ছিল ট্রেনিং ক্যাম্পে , যারা দেশ ছেড়েছিল ওরা তো বেচে গিয়েছিল অনেক সাহসী ছাত্ররা শিক্ষকদের মান সম্মান রক্ষার্থে ভয়ে ভয়ে অনিচছা সত্বেও স্কুলে আসতো , ছোট বড় বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেদের একসাথে করে নামেমাত্র রোল কল করে ২/৩টি ক্লাস নেওয়া হতো ,আর বারান্দায় হাটতো পাকিস্তানী সৈন্যরা। সেই দূ:সময়ের এক সাহসী নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল রাৎগাওয়ে জমিউর রহমান , তার মুখেই শোনা ,মিলিটারীরা কুলাউড়া আসার পরে প্রাণভয়ে কেউ স্কুলে আসতো না , রাজাকারেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতো , স্কুলে না গেলে পাকিস্তানি মিলিটারীরা এসে ধরে নিয়ে যাবে , হত্যা করবে ,আর স্কুলে গেলে ছাত্রদের এবং তাদের পরিবারের কোন অসুবিধা হবে না ,
জামিউর আরো বলেছিল , আমরা অনিচছা সত্বেও স্কুলে যেতাম ক্লাস যখন চলতো তখন দরজার কাছে বসে থাকতো পাকিস্তানি সেপাহী ।
অক্টোবরের শেষের দিকে কোন একদিন আমাদের ক্লাসের সম্মুখে এসে বসেছিল এক মোছওয়ালা সৈন্য,ক্লাস নিচ্ছিলেন আহসান স্যার ঐ সৈন্যের কোকরানো মোছ দেখে আমাদের হাসি পাচ্ছিল ,সৈন্যটি ক্লাসে উকি দিতেই হোসেনপুর গ্রামের নুর মিয়া উচ্চস্বরে হেসে উঠে ,হাসির শব্দ শুনে সৈন্যটি অগ্নিমুর্তি ধারন করে ক্লাসের ভিতর ঢুকেই স্যারকে জিজ্ঞেস করে ‘কোনসে ছোকড়া হাসা ?
দেখেননি বলতেই ,সে স্যারের গালে দুটি চড় বসিয়ে দিয়ে দ্রুত ক্যাপ্টেন দাউদের কামরায় চলে যায় ।১৫ মি পরে একটি গাড়ি নিয়ে এসে স্যারসহ আমাদেরকে গাড়িতে উঠতে বলে ,আমাদেরকে কুলাউড়া হাসপাতালের বর্তমান ইমার্জেন্সী রুমে নিয়ে ঢুকিয়ে বাহির থেকে তালা মেরে দেয় ।সেখানে আমরা ২৬ জন ভয়ে পাথর হয়ে ছিলাম ,আহসান স্যারও এক কোনে নিরবে বসেছিলেন ।আমরা কয়েকজন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি রামপাশার বাতির মেম্বার , মাহতাব চৌধুরী ও তার সাথে এক কাবুলীওয়ালার এবং একজন পাক সেনা উর্দুতে কি যেন বলাবলি করছে ,বেশ কিছুক্ষন পর দুইজন সিপাহী এসে রুমের তালা খুলে আমাদের কে বেরুতে বলে ,ভয়ে সেদিন ঐ রুমে আল্লাহকে কত যে ডেকেছি তার ইয়ত্তা নেই ,আমরা এক এক জন রুম থেকে বের হই আর সৈন্যরা আমাদের গালে দুইটা করে চড় মারে ,ওদের হাত বেশ শক্ত ছিল , আমার গালে এমন চড় মেরেছিল যার দরুন গাল বেশ কয়েক দিন ফোলা ছিল ।তার পর আমাদেরকে বেলা ৪টার দিকে গাড়িতে করে নিয়ে যায় স্কুলে , সেখান থেকে বই খাতা নিয়ে বাড়িতে চলে যেতে বলে ।বাঘের খাঁচা থেকে মুক্তি পাবার পর বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছি , কাফুয়ার পুলের কাছে যাবার পর পুল পাহারারত মুকুন্দপুরের রাজাকার ইব্রাহিম আলি পুলের উপর দিয়ে যেতে মানা করে , কি আর করবো তখন বই খাতা জামা কাপর ভিজিয়ে সাতরে ফানাই গাং পাড়ি দিয়ে বাড়ি যাই ।যতদিন পাকিস্তানী আর্মিরা ছিল ততদিন আর স্কুলে ক্লাসে যাইনি ।
জমিউর আরো বলেছিলেন ,
আমরা স্কুলে গিয়ে বাইরে থেকে দেখতাম , স্কুলের ফিল্ডে বহুদিন বহুলোক জড়ো হয়ে আছে ।স্কুলের দক্ষিন পশ্চিম পাশ্বের খালি জায়গায় প্রতিদিন বন্দিদের দিয়ে গর্ত খনন করানো হতো , পরের দিন দেখতাম সেই গর্তগুলো মাটি চাপা দেওয়া আর আগের দিনের ঐ মানুষ গুলো নেই ।তাগড়া জোয়ান ,শরীরের নানা জায়গায় আঘাতের চিন্হ, হাত পা বাঁধা , সুর্যের দিকে তাকিয়ে আছে , পাশ্বে সেন্ট্রি দাঁড়ানো সেই লোক গুলোর অমানবিক নির্যাতনের কষ্টের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, তাদেরকে তিলে তিলে হত্যা করা হতো , জমিউরের সচক্ষে দেখা পাকিস্তানী আর্মিদের সেই অমানবিক অত্যাচারের বর্ননা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও বইয়েও
উঠেছে । আমরা রাউৎগাওয়ের সেই স্কুল ছাত্র জমিউর রহমানকে স্যালুট জানাই তাকে তো আর মুক্তিযোদধা বলতে পারবো না ,তবে তিনি সহযোদ্ধা ৭১ । (চলবে)
৭১ এর স্মৃতি -পর্ব ২৫ ( পাল্লাকান্দি)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
লংলার আশপাশের আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য ইতিহাস ও ঐতিয্যে সম্বৃদ্ধ আত্বীয় বাড়িতে গিয়েছিলাম মনে আছে ।
বিশেষ করে পাল্লাকান্দির কথা । পাল্লাকান্দি সাহেব বাড়ি কুলাউড়ার পরেই লংলা স্টেশন থেকে দক্ষিন পশ্চিম দিকে অবস্থিত, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত সবুজের পাহাড়ে ঘেরা টিলাগাঁও ইউনিয়নের অনেক গুলো গ্রামের একটি গ্রামই হ্চছে এই পাল্লাকান্দি ।ঐ গ্রামেই রয়েছে একটি ইমাম বাড়ী , একট্ মসজিদ , পুকুর সহ বিরাট সাহেব বাড়ী,
যে বাড়িতেই সংগ্রামের সময় একবার যাবার সুযোগ হয়েছিল যা অত্যান্ত সুন্দর ফুলবাগান , ফলের গাছে সাজানো ছবির মত ছিল সেই সুবিশাল বাগান সম্বৃদ্ধ সাহেব বাড়ীটি , ঐ
“পাল্লাকান্দি “
বাড়ীর কেউ হয়তো সেই ছোট্ট শিশুটিকে মনে রাখেনি কিন্ত আমার স্মৃতিতে যতটুকু দেখেছি তাতেই ঐ বাড়ি আজও উজ্জল হয়ে আছে বলেই ঐ বাড়ির , ঐ বংশের কিছু কথা লিখতে পারলে নিজেকে গৌরবাননিত মনে করবো , তাই লিখছি ,কোন সম্পর্কে কিভাবে গিয়েছিলাম তা এতটা মনে করতে পারছি না তবে কানিহাটি , আমানীপুর এর পরই , পাল্লাকান্দি তে যাই ,তা ছাড়া একটা বিশেষ কথা মনে আছে উনাদের চা বাগান ছিল এবং কেউ গেলে অতিথীকে ফেরার সময় সম্মান সুচক উপহার হিসাবে সুন্দর করে গোলআকারে পত্রিকায় মোড়ানো প্যাকেটে চা পাতা দিতেন উপহার দিতেন ঐ চায়ের গন্ধ ও স্বাদ ছিল ভিন্নতর যা বাজারের চা য়ের সাথে কখনই মিলতো না ।পরবর্তীতে আমার বংশের অনেক মুরব্বীদের সাথে আলোচনা কালে জেনেছি তাদের ঐতিয্যের বর্ননা ।
১৯৭১ সালের শেষের দিকে পাল্লাকান্দি বাড়ীতে বইছিল থমথমে নিরবতা এই বাড়ীর জমিদার সৈয়দ আলী আকতার এর দ্বিতীয় কন্যা সৈয়দা সাকিনা আক্তারের স্বামী হবিগঞ্জের আউশপাড়ার পুরুষ সৈয়দ সিরাজুল আব্দালকে পাকিস্তানী রা বাড়ী ঘেরাও করে অন্দরমহলের সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে বলে সৈয়দ সিরাজুল আব্দাল কে দিতে , অন্যথায় সবাইকে গুলি করে মারবে , সকলের কথা চিন্তা করে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং পাকিস্তানীরা তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করে ,তার লাশ পাওয়া যায়নি ।তিনি এর আগেও একবার সিলেটে পাকিস্তানীদের হাতে গ্রেফতার হন এবং সৌভাগ্যক্রমে বেচে যান ।তিনি ছিলেন প্রথমে লাক্কাতুরা চা বাগানের সহকারী ব্যাবস্থাপক পরে কেয়াছড়া বাগানের দায়িত্বে এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোক । শহীদ সৈয়দ সিরাজুল আবদাল মামুন (বীর মুক্তিযাদ্ধা) ১৯৩১ সালের ১৮মে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী আউশপাড়া (সাহেব বাড়ি) নিবাসী জনাব সৈয়দ সাজিদ আলী সাহেবের ঔরসে ও সৈয়দা জামিলা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত খাজা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহিদ বোগদাদী (রাহ:)। সৈয়দ সিরাজুল আবদালের পিতামহ ছিলেন সৈয়দ রেহমান আলী সাহেব এবং মাতামহ ছিলেন হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী চন্দ্রচুরি (সাহেব বাড়ি) নিবাসী সৈয়দ ইজহার আলী পীর সাহেব। তিনি ছিলেন ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন (রাহ:)’র পরবর্তী বংশধর।
উল্লেখ্য সৈয়দ সিরাজুল আব্দালের মা-খালারা ছিলেন চারজন। তন্মধ্য তাঁর বড়খালা:- সৈয়দা কামরুন্নেছা খাতুনের বিবাহ হয় মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কনকপুর (খান বাড়ি) নিবাসী জমিদার নজাবত আলী খান সাহেবের পুত্র গোলাম ইয়াজদানী খান সাহেবের নিকট। মেঝখালা:- সৈয়দা সামসুন্নেছা খাতুনের বিবাহ হয় হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী স্নানঘাট (দেওয়ান বাড়ি) নিবাসী দেওয়ান তমিজ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেবের পুত্র দেওয়ান আব্দুল গণী চৌধুরী সাহেবের নিকট।
উনার ছেলে মেজর ( অবঃ) ডাঃসৈয়দ জামিল আব্দাল ও দুই মেয়ে সৈয়দা তাহমিনা আব্দাল কানাডা প্রবাসী ও সৈয়দা সায়মা আব্দাল ঢাকাতেই রয়েছেন তারা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন সেই দিনের সেই পিতৃহারানোর ব্যাথা – উনারা হয়তো আরো বিশদভাবে বিস্তারিত বলতে পারবেন ।
সম্প্রতি আমানীপুরের উপর লেখাটি প্রকাশিত হবার পর আমার সাথে যোগাযোগ হয় আমানীপুরের সৈয়দ আহবাব উদ্দিনের কন্যা সৈয়দা হাসিনার সাথে , উনার আর এক বোন সৈয়দা জান্নাতুল কুবরা ও ভাই সৈয়দ হোসেন শহীদ দেশেই আছেন ।কথা প্রসংগে উনার সাথে আলোচনা করে এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হই । কৃতজ্ঞতা জানাই উনাকে আত্বীয়তার শিকড় খুঁজতে গিয়ে জানলাম কানিহাটির আব্দুল মান্নান সাহেবের মেয়ে দিলারা রশিদ যার বিয়ে হয়েছে বেগম সিরাজুন্নেছার ছেলে জাহান জেব রশিদ চৌধুরীর সাথে তিনি সম্পর্কে সৈয়দা হাসিনার বোন হন , আর দিলারা খালাকে যেহেতু আমি খালা ডাকি এবং তিনি আমার খালা সুতরাং উনাকও খালা ডাকবো তিনি আপত্তি করেন নাই। তিনিও আমেরিকা এবং বাংলাদেশ মিলিয়েই থাকেন , উনার আপন খালুই হচ্ছেন সৈয়দ সিরাজুল আব্দাল । সৈয়দা হাসিনা খালার স্বরণ শক্তি অত্যান্ত প্রখর , তিনি অনেক তথ্য দিয়েছেন , অনেক গুলো নাম ও সম্পর্ক নিশ্চিত করেছেন অন্যথায় লেখাটিতে হয়তো কিছু ত্রুটি থাকতো ।
পাল্লাকান্দির জমিদার সৈয়দ আলী আখতার বাবা হয়রত শাহজালাল (রঃ) এর অন্যতম সাথী সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাসিরুদ্দিনের ১৪ তম পুরুষ , তার পিতার নাম সৈয়দ আলী আকবর ,পিতামহ শাহ সৈয়দ ইকরামুল্লাহ , সৈয়দ ইকরামুল্লাহ এর এক ভাই ছিলেন আমানীপুরের সৈয়দ ইনামুল্লাহ , আর এক ভাই সৈয়দ রহমতুল্লাহ , উনার পুত্র সৈয়দ মাহতাব উদ্দিন চলে যান নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার হারুলিয়া সাহেব বাড়ি। উনার নাতি ছিলেন বৌলাইয়ের বিখ্যাত জমিদার জালাল উদ্দিন আহমদ খুরশিদ মিয়া সাহেব ।
পাল্লাকান্দির সৈয়দ আলী আকতার সর্ব প্রথম বিয়ে করেন আওরঙ্গপুরের সৈয়দ আনহার বক্তের (ইয়াওর বক্তের ভাতিজা) বড় বোন কে। কিন্তু অল্প দিন পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান।
দ্বিতীয় বিয়ে করেন ইয়াওর বক্তের মেয়ে সৈয়দা সালেহা খাতুনকে – তাঁর ঘরে
১. সৈয়দা ফাতেমা আহবাব
২. সৈয়দা সাকিনা আবদাল
২. সৈয়দা কুলসুম এজাজ
৩. সৈয়দা যয়নব আলীম
৪. সৈয়দ জয়নাল আক্তার
৫. সৈয়দা সালমা ইসলাম
কিন্তু আওরঙ্গপুরের ইয়াওর বক্তের সাথে কোন কারনে মতবিরোধ হলে ইয়াওর বক্ত তাঁর মেয়েকে পাল্লাকান্দি যেতে দীর্ঘদিন বাধা দেন। যার কারনে সৈয়দ আলী আক্তার সেখান থেকে ফিরে এসে মন্ডাজে অপর বিয়ে করেন। উনারা কেউই জিবিত নেই আল্লাহ উনাদের সকলকে জান্নাত বাসি করুন।
তিনি ও তার দুই ছেলে সৈয়দ আলী আফজাল এবং সৈয়দ আলী আহসান “ পাল্লাকান্দি টি ষ্টেট এর অনেক উন্নয়ন করেন,
এই পাঁচ মেয়ের মধ্যে
১ম মেয়ে সৈয়দা ফাতেমা আক্তার স্বামী সৈয়দ আহবাব উদ্দিন যিনি আমানীপুরের সৈয়দ বুরহান উদ্দিনের নাতি ।
২য় মেয়ে সৈয়দা সাখিনা আক্তার , স্বামী সৈয়দ সিরাজুল আব্দাল মামুন
৩য় মেয়ে সৈয়দা জয়নব আক্তার , স্বামী এ.কে়.এম.এ. আলীম কোরেশী , বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী
৪র্থ মেয়ে সৈয়দা কুলসুম আক্তার , স্বামী মেজর জেনারেল এজাজ আহমেদ চৌধুরী (অঃ) ,সিলেট ফুলবাড়ী।
৫ম মেয়ে সৈয়দা সালমা ইসলাম স্বামী নজরুল ইসলাম , একজন ব্যবসায়ী ছিলেন
সৈয়দ আলী আকতারের পিতা ছিলেন সৈয়দ আলী আকবর প্রথম বিবাহ করেন নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার হারুলিয়া সাহেব বাড়ি নিবাসী সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া সাহেবের কন্যাকে। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন কিশোরগন্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার বিখ্যাত জংগলবাড়ী দেওয়ান হাবেলী নিবাসী জমিদার সৈয়দ এমদাদ উদ্দিন হোসেন সাহেবের কন্যাকে। উল্লেখ্য তিনি ছিলেন ভাটি বাংলার বারো ভুইয়াদের প্রধান মসনদ-ই-আলা দেওয়ান ঈশা খাঁ’র পরবর্তী বংশধর দেওয়ান আজিম দাঁদ খান সাহেবের দৌহিত্র বংশীয়।
এই জংগলবাড়ীতে অবস্তানরত অন্যতম জমিদার সৈয়দ এমদাদউদ্দিন হোসেন যিনি তরপের নরপতির জমিদার , জংগলবাড়িতে আসেন হবিগঞ্জের নরপতি হতে তিনি ঐ জংগলবাড়ির খানেদামান্দ ছিলেন তার এক মেয়েকে বিয়ে দেন পাল্লাকান্দি সৈয়দ আলী আকবরের সাথে সৈয়দ এমদাদ উদ্দিন এর অপর মেয়েকে বিয়ে দেন বৌলাই সাহেব বাড়ীতে এবং তার একমাত্র ছেলের নাম ছিল দেওয়ান আজিম দাদ খান ওরফে মেনু মিয়া ।
সৈয়দ আলী আকতার পাক পান্জাতন ও আহলে
বায়েত এর অনুসারী ছিলেন । তাদের এখানে প্রতিবছর মহররম মাসে মহা শোক দিবস পালন করা হয় তিনি কারবালার শহীদানদের স্বরনে শোকাবিভুত থাকতেন ১০ ই মহররম আশুরার দিনে শোক মিছিলে অংশ নিতেন । তিনি অত্যানত দানশীল ছিলেন ও মানুষের সেবা করতেন ।আমাদের এই সকল হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন বাড়ীর কৃর্তিমান পর্বপুরুষদের ,কাছে দুরের নারী পুরুষ আত্বীয় স্বজনদের বিদ্বেহী আত্বার শান্তি কামনা করি ।আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাদের জান্নাত নসীব করুন । আমিন । ( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি – ( ১৫ )
সৈয়দ শাকিল আহাদ
স্মৃতি কখনও মুছে ফেলা যায় না , তবে ভুলে থাকা যায় ,
৫১ বছর আগের কথা , মুক্তিযোদ্ধাদের কথা , যুদ্ধ চলাকালিন সহযোদ্ধাদের কথা , বীরাঙ্গনাদের কথা , শহীদদের কথা ও হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বরন করার মাঝে হয়তো কারো কারো মনে হবে , হতেই পারে যে আমি অযথাই সময় নষ্ট করছি
আসলে কি লাভ ৭১ সালের দোকান পাঠ বা রাস্তাঘাট কিম্বা বাড়ীঘরের কথা মনে করে ? তাৎক্ষনিক ভাবে লাভ ক্ষতির হিসাব না মিললেও আমার বিশ্বাস এক সময় এই লেখা পড়ার জন্য মানুষ হন্য হয়ে ঘুরবে , যার গন্ধ আমি এখনই পাচ্ছি , এমন কি অনেকেই পুরোনো আপনজনের কথা এখানে জানতে পেরে আবেগে আপ্লুত হচ্ছেন ।
বলছিলাম কুলাউড়ার কথা , সংযুক্ত ছবিটির কথা , ছবিটি আমার বন্ধু লিটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত , প্রচন্ড মেধা সমপন্ন ও তুখোর স্মৃতিতে ভরপুর আমেরিকা প্রবাসী লিটনের কাছে আমি ঋণী , লিটনকে সবাই ডাকবাংলোর লিটন বলেই চিনে , ডাকবাংলোর পাশেই তার বাসা ছিল , সে একজন ফুটবল খেলোয়ার ও সংগঠক , কুলাউড়ার প্রাচীনতম সংগঠন “ জাতীয় তরুন সংঘ” এর সে সাধারন সম্পাদক ছিল বহুদিন ,ইন্টারনেটের কল্যানে বিশেষ করে এই কোভিড দুর্যোগ কালিন সময়ে প্রায়ই ভোরবেলায় ফজরের নামাজের পর যখন মেসেন্জারে দেখতাম ওর নামের পাশে সবুজ বাতিটি জ্বলছে , সাথে সাথেই কল দিয়ে বসতাম এবং কুলাউড়ার নানা বিষয়ে কথা বলতাম ,এই লিটনের উৎসাহে ই আমি আরও একটি তথ্যবহুল ও পর্যটন সহায়ক গ্রন্থ
“ হাওরে পাহাড়ে কুলাউড়া” সম্পাদন করে ফেলেছি ।
যা এখন প্রকাশের অপেক্ষায় আছে ,এবং এই গ্রুপে যে লেখাটি ক্রমাগত যাচ্ছে “৭১ এর স্মৃতি “ নামে , সেটি লিখতে গিয়েও ,বেশ কয়েকটি পর্বের অনেক গুরুত্ববহ তথ্য লিটনের মারফতে পেয়েছি , যেমন এই পর্বের সংযুক্ত ছবিটাও তার দেওয়া এবং এই ছবিটির জন্যই পর্বটা সম্বৃদ্ধ হয়েছে , যার ফলে
ছবির ব্যক্তি তিনজনের মুক্তিযুদ্ধের অবদানের কথা উঠে এসেছে ।
ছবিটিতে তিনজন ধ্রুব তারা কে আমরা দেখতে পাচ্ছি , তিন জনই ছিলেন তখন অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ের ৭১ সালের রিয়েল হিরো ,
আর কেঊ যদি একবার হিরো হয় তো আজীবন তার নামের পাশে হিরোযুক্ত হয়ে থাকে ।
১) বামদিক থেকে শুরু করে প্রথমজন হচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক মোঃ আব্দুল লতিফ খান ,
জন্মগ্রহন করেন ও বড় হয়েছেন বরমচাল ইউনিয়নের নন্দগ্রামের খান বাড়িতে , পড়ালেখা শেষ করে কর্মজীবনের শুরুটা ছিল পাকিস্তান আর্মিতে ,কিছুদিন চাকরী করার পর তিনি চাকরী ছেড়ে নিজ গ্রামে এসে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং জনকল্যানে নিজেকে নিয়োগ করেন এবং কুলাউড়ার সম সাময়িক সংগঠকদের নিয়ে দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় হন ।
৭১ এর ২৬ শে মার্চের পর থেকেই চলতে থাকে জনগনের ভারত যাত্রা , হাজার হাজার লোক , বিভিন্ন শ্রেনীপেশার নারীপুরুষ , শিশু, কিশোর ,যুবক, যুবতীসহ ,আবাল- বৃদ্ধ ,সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের আগরতলা , কুকিতল , কৈলাশহর , ধর্মনগরের শরনার্থী শিবিরে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিল ,দেশকে শত্রুমুক্ত করতে
তখন আগ্রহী যুবকদেরকে কিছু অবসর প্রাপ্ত পুলিশ , আনসার ও সামরিক বাহিনীর লোকদের সম্ননয়ে অশ্রচালনা ও যুদ্ধকৌশল প্রশিক্ষনের ব্যবস্তা করা হয়েছিল সেই প্রশিক্ষন ক্যাম্পের নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল লতিফ খান , পাক মিলিটারীরা কুলাউড়া আসলে পরে তিনি ভারতের ধর্মনগরে চলে যান এবং সেখান থেকে বিভিন্ন অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেন ।, তিনি ১৯৭৭ ইং থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কুলাউড়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ।
আব্দুল লতিফ খান প্রথম ১৯৬৫ সালে বরমচাল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং জনকল্যানে নিরলস ভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন ।স্বাধীনতার পরও ১৯৮৪ সাল হইতে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত পর পর দুই দফায় তিনি বরমচাল ইউনিয়নের সফল চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ।
২) ছবিটিতে ২য় জন হলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক জয়নাল আবেদিন ।তিনি জন্মগ্রহন করেন সিলেট অন্চলের বিয়ানী বাজারে , তিনিও অন্যান্যদের সাথে ঐপারে শরনার্থী শিবিরে মিলিত হয়ে পাশেই প্রশিক্ষন ক্যাম্পে মুকতিকামীদের প্রশিক্ষিত করে এদেশে এসে মুক্তি বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে বিভিন্ন অপারেশনের সফল নেত্রৃত্ব দানের মাধ্যমে নিজের দেশকে শক্রুমুক্ত করতে সচেষ্ট হোন , তিনি দীর্ঘদিন কুলাউড়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন । তাছাড়াও জয়নাল আবেদিন ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী , ষ্টার এজেন্সীর মালিক ।
৩) ৩য় জন হলেন জুবেদ মামা বা আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী , যিনি ছিলেন কুলাউড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠকদের অন্যতম , মুক্তি যোদ্ধাদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষন কালে তিনি ভারতের কৈলাশটিলা ও ধর্মনগরে অবস্তান করেন , রাজা সাহেব , জব্বার মামা , সৈয়দ জামালসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, সংগঠিত করতেন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ,কিভাবে কুলাউড়াকে শত্রু মুক্ত করা যায় তার পরিকল্পনা করতেন ,যুদ্ধের সময়কার সংগ্রামী একজন অগ্রনায়ক ছিলেন এই মুকতাদির চৌধুরী বা জুবেদ মামা ,তিনি কৌলার কানিহাটী চৌধুরী বাড়ীর সন্তান ,
এমনি অনেক মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের নিয়ে আগামীতে আরো লেখার আশা রাখি । ( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি – পর্ব ৩১- (মুরইছড়া ,কর্মধা )
সৈয়দ শাকিল আহাদ
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সারাদেশের বিভিন্ন স্হানে সর্বস্তরের সাধারন জনগনের উদার সম্পৃক্ততা, তাদের অপরিসীম অবদান ও নিস্বার্থ পরিশ্রমের ফলে দ্রূত এদেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও আভ্যন্তরীণ মদদ দাতাদের কবলথেকে শত্রমুক্ত করতে দারুনভাবে সহায়তা করেছিল ,বিশেষ করে কৃষক ,মজুর,ছাত্রছাত্রী ,নারী,
পুরুষসহ আপামর জনসাধারণ, উল্লেখ্য,এদের মাঝে অনেক স্থানে স্হানীয়ভাবে অনেকেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাদের নাম পরবর্তীতে তেমন আলোচনায় আসে নাই এবং তারা ছিলেন প্রচার বিমুখ সেই সকল সহযোদ্ধাদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে, অল্পবিস্তর জ্ঞানের আলোকে এই স্মৃতিচারণে আরো কিছু কথা বলার সুযোগ নিচ্ছি ,এতে হয়তো এই স্মৃতিচারণ কিছুটা দীর্ঘায়িত হবে তবে আমার বিশ্বাস বর্তমান এবং পরবর্তী প্রজন্মের কেউ কেউ দারুণভাবে উৎফুল্লিত হবেন ।
আজ কুলাউড়া থানার কর্মধা ইউনিয়নের কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করছে , ১৯৭১ সালে এই ইউনিয়নের গুরুত্ব ছিল অনবদ্য । এটি মৌলভীবাজার জেলার বর্তমান কুলাউড়া উপজেলার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন ,যার উত্তরে কুলাউড়া ও রাউৎগাঁও ইউউনিয়ন ,দক্ষিনে ভারত সীমান্ত, পূর্বে ফুলতলা ইউউনিয়ন ও পশ্চিমে পৃথিমপাশা ইউনিয়ন অবস্থিত।
বর্তমানে ঢাকা থেকে কুলাউড়ায় বাস বা ট্রেনে এসে আবার বাস বা সি এন জিতে রবিরবাজার পর্যন্ত এসে রবিরবাজার থেকে সি এন জি বা অটো রিক্সায় চরে কর্মধা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন গন্তব্যে ঘুরে আসা আসা যায় ।
যা এক সময় অর্থাৎ যুদ্ধের সময় অকল্পনীয় ছিল ।
সম্প্রতি বেশ কয়েক জন পূরোনো মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলে একমত হই যে ,
১৯৭১ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে সেই ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে ভারতীয় ক্যাপ্টেন হামিদের নেতৃত্বে মাত্র ২৮ জন মুক্তিযাদ্ধা নিয়ে ভারতের টিলা বাজার থেকে মুরইছড়া পাকিস্তানী ক্যাম্প আক্রমনের পরিকল্পনা করেন এবং সেই মোতাবেক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন ।
মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী হিসাবে মৌলভীবাজারের সাবেক এমপি আজিজুর রহমান এবং অধ্যাপক ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে হাল্কা অস্রহাতে রাত দেড়টার পরে মুরইছড়ার কাছে একটি হাওড়ে এসে পৌছান ।
সকলেই রওয়ানা হয়েছিলেন অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে আক্রমন করার উদ্দ্যেশ্যে ভারতের টিলা বাজার ক্যাম্প থেকে মুরইছড়া’র পাকিস্তানীদের ক্যম্পের দুরত্ব ছিল মাত্র তিন মাইল ।
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পরিশ্রান্ত দেহে ছনক্ষেতের উঁচু ঢিপির পিছনে নিজেদেরকে লুকিয়ে রেখে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করে নেন সকল সদস্য ।তার পর ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকলে রাত আনুমানিক আড়াইটা থেকে তিনটার দিকে মুক্তি যোদ্ধারা পাকিস্তানী ক্যাম্প লক্ষ্য করে কিছু গুলি ছুঁড়ে এবং সকলেই স্বীয় অবস্তানে থেকে পজেশান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ।অতঃপর ১৫-২০ মিঃ পর পাক হানাদারেরা তাদের ক্যাম্প থেকে নিজেদের অবস্তান বোঝাতে গিয়ে পাল্টা গুলি ছোড়ে ,ক্ষনিক পরে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সাহসী দল সামনে এগিয়ে ক্যাম্পের কাছাকাছি নিজেদের অবস্তান শক্ত করতে সচেষ্ট হয় , মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্তান উপস্থিতি টের পেয়ে ক্যাম্পের পাকিস্তানী সেনারা কৌশলে ডানে বামে এগিয়ে গিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে , তাৎক্ষনিকভাবে বিপদ উপলব্ধি করতে পেরে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত সংকেত পাঠায় তাদের অপেক্ষমান দলের কাছে , বিপদ সংকেত পেয়ে তৎক্ষনাৎ দ্রুত এগিয়ে এসে ভারতীয় ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে অপেক্ষমান দলটি অতর্কিত আক্রমন করে পাকিস্তানী সেনাদের উপর ,হটাৎ এমন আক্রমনে হতভম্ব হয়ে দিশেহারা হয়ে পরে পিছু হটে পাকিস্তানীরা ,তাদের বেশ কয়েকজন আহত হয় ।সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় একদল মুক্তিসেনা ।সংগত কারনেই ইতিহাসের অগ্নিস্বাক্ষী হয়ে আছে কুলাউড়ার এই দুর্গম সীমান্তঘেরা পাহাড়ীয়া এলাকা “ মুরইছড়া “ , সকলেই এই মুরইছড়া ইকোপার্কে বেড়াতে আসেন , উপভোগ করেন প্রাকৃতিক সৌন্দের্যের লীলাভুমি , তবে এদের জানা উচিত এই এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটনা সমুহ ।
কর্মধা ইউনিয়নের আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য , যেমন
১) আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ , পিতা মোঃ আব্দুস সাত্তার , গ্রাম ভাতাইয়া , তিনি স্থানীয় শ্রমিক ও যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্য প্ররোচিত করেন ।তার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নং হলো ০৫০৪০৪০৫৩৪।
২)মকবুল আলী , পিতা আরজদ আলী , গ্রাম ভাতাইয়া , তিনি স্থানীয় শ্রমিক ও যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্য প্ররোচিত করেন ।তার মতে আমরা দেশকে রাহুমুক্ত করেছি এটা আমাদের সান্তনা ।তিনি বিশ্বাস করেন নতুন প্রজন্ম এদেশকে উন্নতির শিখরে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।তার মুক্তি নং ০৫০৪০৪০৪৩৯।
৩) মোঃ আবুল মান্নান , পিতা আব্দুস সমদ , গ্রাম কর্মধা , মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নং :- ০৫০৪০৪০৪৪০।
মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের দরুন রাজাকারেরা মান্নানের পরিবারের
ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে ।
৪) সনাতন সিংহ , পিতা বাবু ছানা সিংহ , গ্রাম নলডরি , মুক্তিযোদ্ধা অন্তর্ভুক্তি নং :- ০৫০৪০৪০৪৪৮ ।
তার ভাষ্যে পাকিস্তানীরা এই এলাকায় এসেই আমাদের সম্প্রদায়ের বাড়ীঘরের উপর হামলা চালায় , আমরা পাক সেনাদের আসার আগেই সপরিবারে ভারতে চলে যাই , সেখানে যুদ্ধের ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন অপারেশানে অংশগ্রহন করি , বহুবার মৃত্যুর মুখামুখি হয়েছি ।মৃত্যুর চেয়ে দেশের স্বাধীনতা আমাদের কাছে বড় ছিল ।
৫) রাম সুন্দর গোপাল , পিতা -রাম জনম গোপাল , বাড়ী ঃ- রাঙ্গিছড়া চা বাগানে তিনিও মুক্তি যুদ্ধে অনবদ্য ভুমিকা রাখেন ।তার মুক্তি যোদ্ধা নং ০৫০৪০৪০৪৫০
৬) গানেশ রুহি দাশ , পিতা -শুকুয়া রুহি দাস , বাড়ী ঃ- কালুটি চা বাগানে তিনিও মুক্তি যুদ্ধে অনবদ্য ভুমিকা রাখেন ।তার মুক্তিযোদ্ধা নং ০৫০৪০৪০৪৫১।
এই কয়জন ছাড়াও অনেকের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে যা আগামীতে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি ।
সেই ইউনিয়নের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেকে মধ্যে একজন সহায়তাকারী মহান ব্যক্তির কথা বিশেষভাবে মনে হচছে ,তিনি হচ্ছেন ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান , যিনি হলেন হোসনাবাদ গ্রামের জনাব ইয়াকুব আলী , যিনি ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যনের দায়িত্ব পালন করেন , পরবর্তীতে তার ছেলে আব্দুস শহীদ বাবুল ও দীর্ঘদিন এই কর্মধা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন ।এবং কুলাউড়াতে এই মহান ব্যক্তির নামে “ইয়াকুব তাজুল মহিলা মহাবিদ্যালয়” নামে একটি বেসরকারী কলেজ ও পরিচালিত হচ্ছে ।
হিন্দু মুসলমান সহ চা বাগান ও সীমান্তঘেরা পাহাড়ীয়া এলাকা এবং চা শ্রমিক ও স্বল্প সংখ্যক উপজাতীয় দের সহাবস্থান সমন্নয়ে এই এলাকার গুরুত্ব অনেক বেশী ।
কর্মধা ইউনিয়ন ভুক্ত গ্রাম ও এলাকার মধ্যে বিশেষভাবে
কর্মধা, মলডরী, টাট্টীউলী,মনসুরপুর,মুরইউড়া, পাট্টাই,বুধপাশা, হাসিমপুর,ফটিগুলি,ভাতাইয়া,
রাঙ্গীছড়া,কাটাপুন্জি, ঝীমাই ,লম্বাছড়া,মনছড়া,এওলাছড়া,দোয়ালগ্রাম, কুকিজুরুী,মৈশামারী,নুনা,বরুয়াকান্দি,ভান্ডারীগাও,গুতুমপুর,মহিষমারা,রুষনাবাদ,উগারছড়া,মেঘাটিলা,কালিটি,লক্ষীপুর ,
আসগরাবাদ, কাটাবাড়ী ইত্যাদি পাহাড়ীয়া এলাকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।
অনেক অনেক স্মৃতি ময় কুলাউড়ার সেই ৭১ এর কথা সরাসরী সম্পৃক্ত কেউই কখনও ভুলতে পারবে বলে আমার মনে হয় তবুও নতুন প্রজন্মের কাছে সেই সংগৃহীত কিছু স্মৃতি ও গুটি কয়েক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির তথ্য তুলে ধরে কিছুটা আনন্দ এবং স্বস্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি ।
এ পর্বটি তৈরীতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ‘মুক্তিযুদ্ধে কুলাউড়া’ বইটির লেখক জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদকে ।( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি —( ৪)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
সেদিনের কথা ইহজীবনে কখনও ভুলতে পারবো কিনা জানিনা তবে স্মৃতিময় উজ্জিবীত সেই ঘটনা , দিনটা ছিল ১৯৭১ সালের আগষট মাসের কোন এক শুক্রবার , তারিখটা মনে নেই , হয়তো মা ভাষাসৈনিক ছালেহা বেগম বলতে পারতেন , কারন তিনি প্রতিদিনই ডায়রি লিখতেন তার ছোটবেলা থেকেই এবং বছর শেষে ঐ ডায়রিটা যত্ন করে আলমারীতে তুলে রাখতেন আর নতুন বছরে নতুন ডায়রিতে জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো রাতে সব কাজ সেরে এশার নামাজের পর ঘুমাতে যাবার আগে প্রতিদিনই ডায়রি লিখে ঘুমাতে যেতেন কিন্তু তিনি তো আজ বেচে নেই , আর এত গুরুত্ব দিয়ে কখনও তার কাছে জানতেও চাইনি সেই তারিখটার কথা এবং তার ৭১ এর ডায়রিটা কোথায় আছে তাও পরিবারের কেউ বলতে পারবে কিনা সেটাও আমি নিশ্চিত নই ।
তবে যতদুর মনে পরে আমাদের পরিবারে খাবার টেবিলে প্রায়ই আলোচনা হতো সেই সময়ের উল্লেখ যোগ্য ঘটনাগুলো নিয়ে এবং আমার দিকে আংগুল উচিয়ে প্রায়ই বিশেষ করে বড়মামাকে বলতে দেখেছি
“ এই সেই বীর বাহাদুর যে না বুঝেই অনেক বেশি সাহস দেখিয়েছিল সেদিন ।”
যতদুর স্বরণে আছে ,
সেদিন সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল ,
কেউ তেমন একটা ঘর থেকে বাইরে বেরুতে আগ্রহী ছিল না ,আমি কাউকে কিছু না বলেই বাড়ীর বাইরে বেরিযেছিলাম , সেটা ছিল আমাদের নানাবাড়ী, সিলেট জেলার কুলাউড়ায় , উছলাপাড়া খান সাহেবের বাড়ী ,অত্র অনচলের নাম করা বাড়ী সমুহের একটি , এ বাড়ীর সামনেই বিরাট দীঘি ও তার সামনেই মহাসড়ক এবং বাড়ীতে ঢোকার মুখেই ছিল একটি বটগাছ এখন ও কুলাউড়ার অনেকের ই মনে আছে সেই বট গাছের কথা এবং তার বিপরীতে একমাত্র ফুটবল খেলার মাঠ ।এবং আমি ঐ বট গাছের নীচে বসে খেলছিলাম , এমন সময় হটাৎ ঠুস ঠাস শব্দ , আমি তাড়াতাড়ি গাছের পিছনে কাঁচুমাচু হয়ে আশ্রয় নেই ,চার পাঁচ জন খাঁকি পোশাক পরা লোক বন্দুক হাতে ( পরে জেনেছি ওরা ছিল পাক আর্মি) দুইজন লোককে আমাদের বাড়ীর দিকে ধাওয়া করে নিয়ে আসছে ।
বটগাছের নিচে আসতেই একজনকে ধরে ফেললো , একজনকে ধরতেই অন্যজন দক্ষিনের রাস্তা ধরে প্রাণপনে স্কুল চৌমুহনির দিকে দৌড়ে পালালো , তার পিছু আর কেউ যায়নি ।
যাকে ধরেছিল তিনি অনেক কসরত করছিলেন ছুটে প্রান বাচানোর জন্য , তখনই ঐ ধসতা ধসতির সময় একটি রাইফেল ছিটকে এসে পড়ে আমাদের বটগাছের কাছের খাই তে ( সড়কের পাশের খাল এ ) ঠিক আমার সামনেই ।
আবার ও ঠুস ঠাস শব্দ ,
কোথায় কে কাকে গুলি করছিল তা উপলব্ধি করিনি , মনেও নেই , তবে মনে আছে আমাকে তখন পিছন থেকে শুয়ে থাকা এক লোক বলেছিল “বাবু তোমাকে চকলেট দেবো , যদি তুমি ঐ বন্দুকটা এনে দিতে পারো ? “
আমি এক মুহুর্ত ও দেরি করি নাই । খালের পাশে পরে থাকা রাইফেল টি এনে দিলাম , তখন ঐ লোকটি ( মুক্তিযাদ্ধা ) আমাকে বললো , বাবু তোমাদের বাড়ী কোথায় ?
আমি দেখালাম ,
ঐ যে , ঐটা ,
সে তখন বললো ,
“বাবু তুমি দেরি করো না ,
আস্তে আস্তে বাড়ী যাও
এখানে গোলা গুলি হচ্ছে ,
যে কোন সময় যে কেউ মরতে পারে ,
আমি একটু পরে তোমার জন্য চকলেট নিয়ে আসবো । “
আমিও ঐ লোকটির কথামত তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম ।
আমার মুখে সবকথা শুনে আমমা ও বড়মামা আমাকে জরিয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিলেন ।এবং বলেছিলেন “ আজ যদি তোর কিছু হয়ে যেত তো আমাদের কি অবস্তা হতো ? “
ছোট মামা বলেছিল “ তুই তো বাঘের বাচ্চা , আমরাই ঘর থেকে বের হয়নি আর তুই যুদ্ধের ময়দান থেকে এলি “
তবে অনেক দিন পথপানে চেয়েছিলাম ঐ লোকের জন্য , চকলেটের জন্য ,
কেউ চকলেট নিয়ে আসে নি । এখন বুঝি সেদিনকার ভয়াবহতা , একটা গুলি এসে আমার বুকটাও ঝাঁঝড়া করে দিতে পারতো ।
বেচে গেছি , আর বেচে আছি বলেই ঐ দিনের কথা মনে করে শিহরীত হই ।যুদ্ধ আমি করিনি ঠিকই কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রান বাজী রেখে সহযোগীতা করেছি । আমি একজন সহযোদ্ধা । ( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি —-( ৯)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
এত ভয়াবহ সেই সকল দিন ও রাত গুলো কেটেছে যা মনে হলে আজও শরীর শীউরে উঠে ,গা ছিম ছিম করে , বিশেষ করে দিনের বেলা তো কোন রকমে কেটেছে অজানা শংকায় ,কিন্তু রাত হলেই সবাইকে থাকতে হতো আতংকে ,যেহেতু আমাদের বাড়িটি ছিল মহা সড়কের কাছে , একটু রাত হলেই দরজা জানালা লাগিয়ে হারিক্যান , কুপি ইত্যাদি নিবিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়তাম , ঘরের বাইরে কোন শব্দ হলেই মনে হতো এই বুঝি পাকিরা এসে পড়েছে , কিম্বা তাদের দোসর রা এসেছে দেখতে বাড়িতে কে কে আছে ?
বা নিশ্চই এখনই দরজায় লাথি মারবে এবং ঘরে ঢুকে এসে সবাইকে গুলি করে মারবে ।
কয়েক বার এমনও হয়েছিল রাতের বেলা দম বন্ধ করে চুপটি করে থাকতে হয়েছে , এমনকি ভয়ে প্রাকৃতির ডাকে সারা দিতেও কাউকে দরজা খুলে বেরুতে দেওয়া হয়নি ।
১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল , সেবছরও বাঙালি মুসলমানের জীবনে এসেছিল পবিত্র রমজান মাস।
মুসলিম বিশ্বে মাসটি যথারীতি পালিত হচ্ছিল ইবাদত-বন্দেগির মাস হিসেবে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা মাসটি পার করেছে ভয়-উৎকণ্ঠা আর বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।
যথারীতি দীর্ঘ একমাস রোজা শেষে ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ অর্থাৎ শাওয়ালের চাঁদ উঠেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পশ্চিমাকাশে, কুলাউড়া শহরে ।
পরদিন ২০ নভেম্বর, শনিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর পালিত হয় , নতুন কাপর পরতে পেরেছিলাম কিনা মনে নেই , শুধু মনে আছে মনুর ( মনসুর ) এর ঈদগাহে নানা ও ছোট মামা নামাজ পড়তে গিয়ে ছিলেন ,
আর আম্মা সকাল বেলায় সেমাই ও খেজুরের গুড়ের ক্ষীর রান্না করেছিলেন , আমাকে নামাজে নেয়নি , পান্জাবীরা ছোট ছেলেদের ও ছারছে না মেরে ফেলতে পারে এই কারনে ।তাছারা ওরা কিনতূ আমার নাম ও জানতো , ঐ যে একদিন ওদের গার্লস স্কুলের ক্যাম্পে গিয়েছিলাম তখন কাছাকাছি অস্রহাতে বারান্দায় পাহারারত একজন সিপাহী আমাকে ডেকে আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিল,
“এই বাবু “তোমারা নাম ক্যায়া হ্যায় “এবং বলেছিলামও । ‘ইধার আও ‘ বলে কাছে ডাকতেই সেখান থেকে ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছিলাম।
বাড়ী আসতেই নানী বলেছিলেন
“ঊতুগুনি ফুয়ার, সাহস কত দেখ ?
আস্তা দিন কেউরে না কইয়া খালি ওবায় হবায় যায় , আইজ যুদি পাইন্জাবীরা দরিয়া মারি লাইতো তো আমরা কৈ তুকাইলাম এনে ?”
এমন বিবর্ণ, নিরানন্দ-বেদনা বিধুর ঈদ বাঙালি জীবনে আর কখনো এসেছে কিনা আমার জানা নাই , তবে পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যাযজ্ঞ, নীপিড়ন-নির্যাতনে বিপর্যস্থ পুরো কুলাউড়া , পুরো বাংলায় ই রণাঙ্গন, শরণার্থী শিবির ও দেশের ভেতরে থেকে যাওয়া মানুষেরা ছিল আতঙ্ক এবং জীবনের চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে। বীর বাঙালিরা মাতৃভূমিকে দখলদার বাহিনির কবল থেকে মুক্ত করতে লড়াইয়ে লিপ্ত।
পবিত্র ঈদের দিনেও পাকিস্তানি হানারদাররা এই বাংলায় হত্যা, বাড়িঘরে লুণ্ঠন ও আগুন দেয়।
অনেক জায়গায় মা-বোনেরা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়। যে দেশের জন্মই পবিত্র ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে, সেই দেশেরই কেন্দ্রীয় সরকার বাহিনি স্বাধীনতাকামী নিরীহ মানুষদের উপর বর্বরতা চালায় পবিত্র ঈদের দিনেও।
মুসলমান সম্প্রদায়ের পবিত্র দিনে এমন নিন্দিত ঘটনার নজির মুসলিম বিশ্বে আর কোথাও নেই।
পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে থাকা বাংলার আকাশে ঈদের চাঁদ মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী বাঙালির মুখে হাসি ফুটায়নি সেবছর।কুলাউড়া বাসী তথা সিলেট জেলার আপামর জনগনের মনে আছে সেই বছর
কত কষ্ট করে ঈদ উদযাপনের কথা ।( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি— ১৭ (জয়পাশা-২)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কুলাউড়া রেল ষ্টেশনে দাড়িয়ে বহুবার ভেবেছি কবে স্থাপিত হয়েছিল এই ষ্টেশন ?
তথ্য অনুসন্ধান করে জেনেছি ১৮৯২ – ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আখাউড়া – কুলাঊড়া রেলপথ যা ১৮৯৬ সালে করিমগঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে , পরবর্তীতে ১৯০৪ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জন প্রায় ১২০৭ কিলোমিটার রেলপথ উদ্ভোধন করেন তখনই কুলাউড়া সিলেট রেল লাইনের কাজ শুরু হয় ।১৯১২,সালে সিলেট জেলার সাথে সংযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে তৎকালীন আসাম বেঙ্গলের গভর্নর আসেন কুলাউড়ার অন্যতম জমিদার জনাব সৈয়দ কেফায়েত উল্লার কাছে , কুলাউড়া শাহবাজপুর ও কুলাউড়া সিলেটের সংযোগ স্থলে একটি
জংশন তৈরীর প্রয়োজনীতা ও জমি দানের প্রস্তাব রাখেন সৈয়দ কেফায়েত উল্লা সাহেবের কাছে , তিনি তখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তার বাড়ীর পশ্চিমের দিকের বিশাল এলাকা দুরে কয়েক হাজার কিয়ার জমি ও বিশালকায় দীঘি দান করেন ষ্টেশন তৈরীর কাজে ।
তৈরী হয় কুলাউড়া জংশন ।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে এই পথে ট্রেন চলাচল করে ।পরবর্তীতে কুলাউড়ার পূর্বদিকের গুগালীছড়া থেকে সুপেয় পানি ও বিদ্যুৎ এর সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে আবারও শরনাপন্ন হতে হয় রেল কর্তৃপক্ষকে তার জমি ব্যবহারের জন্য ।সৈয়দ কেফায়েত উল্লাহর পুত্র সৈয়দ হেদায়েত উল্লার নিকট বাৎসরিক খাজনা ও দেয়া হতো ঐ জমি ব্যবহারের কারনেই । উল্লখ্য সর্বদা সম্মান প্রাপ্ত এই বাড়ীর লোকজনের চলাচলের জন্য কুলাউড়ার স্টেশনে একটি সেলুন বগি সংরক্ষিত অবস্তায় অপেক্ষমাণ থাকতো কুলাউড়া রেল ষ্টেশনে ,এই বাড়ির কেউ চলাচল করতে চাইলে তখন ষ্টেশন মাস্টার সাহেবকে জানালেই তিনি সেই সেলুন বগি ট্রেনে সংযোগের ব্যবস্তা করে দিতেন ।
উল্লেখ্য পুরোনো লোকজনের মাধ্যমে জানা যায় , কুলাউড়ার প্রায় ৭০শতাশ জমির মালিকই ছিলেন কুলাউড়ার সিংহপুরুষ সৈয়দ কেফায়েত উল্লাহ সাহেব ।
৭১ সালে যখন কুলাউড়ার জয়পাশা জমিদার বাড়ীতে যেতাম তখন বিশেষ করে রেলস্টেশন এর উত্তর পুর্বপাশ দিয়ে সাহেব বাড়ীর নিজস্ব রাস্তা দিয়ে যাওয়া যেতো বাড়ীতেই , রাস্তার পাশেই ছিল একটি গভীর খাল , কিছুদুর গেলে পরে ঐ খালের উপর বড় কাঠের তক্তা দিয়ে পাটাতন তৈরী করা ছিল সহজে বাড়ী পৌছানোর জন্য , এটা ও হাঁটা পথ তার পর বাহিরের বাংলোর পিছনেই ছিল অন্দর মহলে প্রবেশের পথ , দুই পাটাতনের সিঁড়ির ধাপ পেরুলেই লম্বা টিনের ঘর ঐ ঘরটিকে নানা কাজে ব্যবহার করা হতো , তার পশ্চিমেই ছিল কারুকার্য খচিত মুল বাড়ীর বড় দাদা অর্থাৎ সৈয়দ মাহবুব উল্লাহ দাদা বা মবুব দাদার অংশ ।
বড় দাদা যুদ্ধের সময় সপরিবারে ঢাকায় ছিলেন এবং তার দক্ষিন দিকেই ছিল মেঝো দাদা বা মাখন দাদার অংশ , তিনি তখন আমাকে খাতির করতেন আমার প্রিয় সেই মেঝো দাদা এখন আর বেচে নেই তবে তার আত্বা ঘুর ঘুর করছে , আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তিনি আমার সামনে এবং আমাকে লক্ষ্য করছেন ,যাকে মাখন দাদা বলেই জানতাম , তার নাম ছিল সৈয়দ মাহমুদুল্লাহ , তিনি ছিলেন তিন মেয়ে তিন ছেলের গর্বিত পিতা , মাখন দাদার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবার বড় ছিল ঃ-
১) সৈয়দা নিলুফার বেগম বা কোহিনুর ফুপু , তিনিও আমাকে অত্যানত্য আদর করেন । ২) সৈয়দা কানিজ আয়শা মুক্তা
৩) সৈয়দ সৈয়ফুল্লাহ জুনেদ
৪) সৈয়দা নিগার সুলতানা
৫) সৈয়দ বাকিউললাহ শিবলী
৬) সৈয়দ মোঃ আলী সোহেল মাখন দাদা অত্যান্ত ধার্মিক ছিলেন প্রায়দিনই বিকাল বেলা এই দাদা বসতেন বাড়ীর ভিতরের উত্তরের কোনায় অন্দর মহলের লম্বা বারান্দার ইজি চেয়ারে ,
তার একটা পিতলের হুক্কাদানী ছিল , তিনি ইজি চেয়ারে বসে হুক্কা টানতেন আর ভাল মন্দ জানতেন আমার কাছ থেকে , সাদা ধবধবে চেহারার দাড়ীওয়ালা এই মাখন দাদাকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠতো ।
তিনি ছিলেন দীর্ঘদিনের কুলাউড়া ইউনিয়নের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি চেয়ারম্যান, দাদী হোসনে আরা চৌধুরী ছিলেন খুউব ই মিশুক ও পরহেজগার , সবসময় মাথায় ঘোমটা থাকতো , মোটা গ্লাসের চশমা পড়তেন , দাদীর বাবা ছিলেন সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ থানার কানিশাইল ( উত্তর বাড়ির ) জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তৎকালিন সময়ে সমগ্র জেলার তিনজন শিক্ষিত ব্যাক্তির একজন ।
সিলেট শহরের মীরের ময়দানে তার ছোটছেলে এখনও বিদ্যমান আছেন এবং বাড়িঘর রয়েছে ।
জয়পাশা সাহেব বাড়ি আমার জীবনে নানা ভাবে স্বরনীয় হয়ে আছে , যুদ্ধের সময় তো প্রচুর যাওয়া হয়েছে এবং তার পরও বিভিন্ন সময়ে অনেক ,অনেকবার গিয়েছি ।
জয়পাশা জমিদার বাড়িতে যুদ্ধের সময় যতবারই আম্মাকে নিয়ে গিয়েছি, আম্মা যখন দাদীদের ফুপুদের সাথে কথা বলতেন আমি তখন ছলে বলে ছুটে যেতাম সৈয়দ ওলীউল্লাহ দাদার তৃতীয় ছেলে , সৈয়দ রানা ডালিম বাবু চাচার কাছে , উনি আমি ও পারভেজ চাচা বাড়ীর দেউরিতে মার্বেল খেলতাম , বাবু চাচার সাথে পারতাম না তার পরও তিনি খেলার জন্য ডেকে নিয়ে মার্বেল ধার দিতেন এবং বার বার জিতে নিতেন , বাবু চাচা এখন বর্তমানে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ীতেই থাকেন । উনারা ভাই বোন মোট সাতজন
দাদা সৈয়দ ওলীউল্লাহ বিয়ে করেছিলেন , ভাটিপাড়া জমিদার বাড়ির খান বাহাদুর গোলাম কিবরিয়া সাহেবের নাতি মাহমুদুল হক চৌধুরীর মেয়ে সালেহা খানম চৌধুরীকে ,
ওলি দাদার ছেলেমেয়েরা হলেন ঃ-
১) সৈয়দ আহসান উল্লাহ সোয়েব
২) সৈয়দ আমানউল্লাহ খোকন
৩) সৈয়দ কানিজ রাবেয়া জলি
৪) সৈয়দ রানা ডালিম বাবু
৫) সৈয়দা জান্নাতুল ফেরদৌসী পান্না
৬) সৈয়দ মোহাম্মদ ইশতিয়াক
৭) সৈয়দা শামীমা সুলতানা ।
যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই জেনেছি ঐ বাড়ী আমার আব্বার মামার বাড়ী ,আর ঐ বাড়ীর সব মুরব্বীরা আমার দাদা অর্থাৎ মবুব দাদা , মাখন দাদা , অলি দাদা ও হবিব দাদা আমার আব্বার মামা মানেই আমার দাদা ।
আর ঐ বাড়িতে আমার আব্বা সৈয়দ আব্দুল আহাদ মশকুর যেখানে ৫০ এর দশকের শেষে এবং ৬০ এর দশকের শুরুতে প্রচুর সময় কাটিয়েছেন , সেখানে ঐ বাড়ীটির সাথে সম্পৃক্ততাকে ভুলে গেলে চলবে কি করে ?
বিশেষ করে ৬০ এর দশকের শুরুতে আব্বা সৈয়দ আব্দুল আহাদ মশকুর যখন তার মামাতো বোন অর্থাৎ সৈয়দ মাহবুব উল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে সৈয়দা রাশিদা বেগমের সাথে বর্তমান কিশোরগন্জ জেলার বাজিত পুর নিবাসি জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম বাচ্চু মিয়ার সাথে বিয়ে হয় , এই বাচ্চু মিয়া যিনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সবচেয়ে বড়লোক হিসাবে খ্যাত ইসলাম গ্রুপের কর্নধার প্রয়াত জহিরুল ইসলাম সাহেবের ছোটভাই , বাচুচু মিয়াও ইসলাম গ্রুপের একজন পরিচালক এবং অত্যন্ত বিনয়ী ও পরোপোকারী এবং বিনয়ী ছিলেন ,তাদেরই বিয়ে উপলক্ষে মাসব্যাপি আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহন করেছিলেন । আব্বার লেখালেখীর হাত ছিল অনেক ভাল ইতিমধ্যে বাংলা ও ইংরেজীতে “ জয়পাশার খন্দেগার পরিবারের “ নামক গ্রন্থ রচনা করে আব্বা ঐ পরিবারের কাছে সুলেখক , সাহিত্যিকে পরিনত হয়েছিলেন এবং রশিদা ফুপুর বিয়ে উপলক্ষে “ ফুল ও ভ্রমর “ নামে একটি উপহার পত্র লিখে ব্যপক জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করেন তার উপর আবার আব্বার গানের গলা অনেক মিষ্টি ছিল তিনি যতেষ্ট সুন্দর গান করতেন এবং প্রতিদিনই সন্ধার পর এই বিয়ে উপলক্ষে জমজমাট গানের আসর বসতো , আশে পাশের অনেক আত্বীয় স্বজনের আসা যাওয়ায় মুখরিত থাকতো প্রতিদিনই ,তেমনি একদিন সন্ধায় বেড়াতে এসেছিলেন আমার নানী মরহুম মনিরুন্নেছা খাতুন , গান শুনে অনেক তারিফ বা প্রশংসা করেছিলেন , আর সেই সুবাদেই আমার প্রিয় লাকসামের লনী দাদী প্রস্তাব দিয়ে বসেন আমার নানীর কাছে ,
আম্মাকে তার ভাগিনা বউ হিসাবে পেতে চান ।
নানী প্রস্তাব গ্রহন করে বাড়ীতে এসে নানার সাথে কথা বলে সম্মতি জানান এবং অল্পদিনের মধ্যেই সৈয়দ মাহবুব উল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে রসিদা বিবির বিয়ের পরপরই মহাধুমধামে তাদের ভাগিনা সৈয়দ আব্দুল আহাদ মশকুরের সাথে বিয়ে সম্পন্ন হয় উছলাপারা খান বাহাদুর আমজদ আলীর বড়ছেলে খান সাহেব আশরাফ আলীর ছোট মেয়ে তখনকার কুলাউড়া গার্লস হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা ভাষাসৈনিক ছালেহা বেগমের সাথে ।পরপর দুইটি বিয়ে জয়পাশা সাহেব বাড়ীতে সমপন্ন হওয়াতে তখন ছোট্ট শহরের কুলাউড়ার সবচেয়ে আলোচিত ও উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ছিল , যার ফলে ঐ বাড়িতে উৎসবমুখর এ
আনন্দঘন পরিবেশ বজায় ছিল দীর্ঘদিন । রশিদা ফুপুরা ছিলেন ১০ ভাইবোন ।দাদা সৈয়দ মাহবুবুল্লাহ বিয়ে করেছিলেন অত্যান্ত সুন্দর পুতুলের মত এক রাজকন্যাকে , যিনি চাঁদপুরের বিখ্যাত রুপসা জমিদার বাড়ীর কন্যা ।
সৈয়দ মাহবুবুল্লাহ ওরফে মবুব দাদার সন্তান গন হলেন ঃ-
১) সৈয়দ ওবায়েদউল্লাহ মাসুম
২) সৈয়দা হুমায়রা বেগম
৩) সৈয়দা রাশিদা বেগম
৪) সৈয়দ শাব্বির উল্লাহ
৫) সৈয়দ বেবী বেগম বেবী
৬) সৈয়দা রেহানা বেগম খুকী
৭) সৈয়দা যুগনু বেগম
৮) সৈয়দ আহলুল্লাহ উজের
৯) সৈয়দা মুসাররাত বেগম
১০) সৈয়দা নাহিদ বেগম ।
উল্লেখ্য সর্বদা হাসিখুশী সবার বড় ছেলে মাসুম চাচা এই ইহজগতে নেই , ইন্নাল্লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন ।
এই বংশের অন্যতম সৈয়দ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বর্তমানে জীবিত আছেন এবং পরিবার পরিজন নিয়ে সুদুর আমেরিকাতে অবস্তান করছেন । তার সন্তান গনের নাম হচ্ছে ঃ-
১) সৈয়দ মোঃ পারভেজ
২) সৈয়দ মোঃ জারজিস
৩) সৈয়দ মোঃ সাদিক
৪) সৈয়দ মোঃ হাদী
৫) সৈয়দ রওশন জাহান বেগম রুবা
৬) সৈয়দা তাসলিমা বেগম রুনা
উল্লেখ্য মবুব দাদা , দাদী , মাখন দাদা , দাদী , ওলী দাদা ও দাদী এবং তাদের বোনেরা সহ সকল কয়েকজন মেয়ের জামাই ও কয়েক জন ছেলে সহ হারিয়ে যাওয়া বংশধরদের জন্য জান্নাত কামনা করছি । আমিন । ( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি -১০
সৈয়দ শাকিল আহাদ
৭১ সালের মে মাস টা কোন ভাবেই ভোলার মত নয় , যখন কুলাউড়াতে পাকিস্তানী মিলিটারীরা এলো ,ঢাকা সহ সারাদেশেই পাকিস্তানী মিলিটারীরা ঢুকে পড়েছিল আগেই এবং ঢুকেই ঐ সকল এলাকার মুক্তি কামী বীর সেনাদের ধরে ধরে ক্যাম্পে এনে নির্মম ভাবে হত্যা করতো , যেহেতু যুদ্ধের বছর তখন সকলেই ছিলেন সতর্ক ,
প্রয়োজন ছাড়া কেউই তেমন কারো বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন না , তবে আমাদের কুলাউড়ার উছলাপারা নানা বাড়ীতে প্রায়শই কৌলা থেকে আসতেন আমাদের এক মামা খুউব সুন্দর চেহারা , চোখে চশমা থাকতো ,ছিম ছাম গড়ন , তার ছিল একটি সুন্দর সাইকেল ও তিন ব্যাটারীর টস লাইট , তিনি ঐ সাইকেল যোগে কুলাউড়া শহরে আসার প্রাক্কালে বটগাছের নীচ থেকেই টিং টিং শব্দ করে এসেই ডাক দিতেন , ফুফু ফুফু বলে , আমার নানা বাড়ীর সামনে অর্থাৎ কুলাউড়ার ফিল্ডের পশ্চিম দিকে বাড়িতে ঢুকার মুখেই ছিল একটি বিরাট বট গাছ ,সেই রাস্তার মুখেই যখন সাইকেলটি ঢুকতো জুনেদ মামা তখন রিং বাজাতেন ,সাইকেলের ঐ রিংয়ের শব্দ শুনেই নানী দৌড়ে বেরুতেন , ব্যস্ত হয়ে পরতেন কৌলার মামাতো ভাইয়ের বড় ছেলে আব্দুল মুসাবিবর চৌধুরী ওরফে জুনেদ চৌধুরী কে দেখতে উনাদের মূল বাড়ী কানিহাটিতে , কৌলা উনাদের নানা বাড়ী ,জুনেদ মামা নিয়ম করেই আত্বীয় স্বজনদের খেয়াল রাখতেন , আমাদের বাড়িতে সকলের খোঁজ খবর শেষে যেতেন তাদের মাগুরাস্ত বাসায় , জুবেদ মামার বাসায় ,সময় কাটাতেন হেসাম ভাই , তাহরাম , তারাজ দের সাথে , আরো সময় কাটতো তার কুলাউড়ার অন্যান্য অনেক আত্বীয় স্বজন দের সাথে ,রামগোপাল ফার্মেসী র উপরে ঐ দোতালা বিল্ডিং এর উপরের তলায় চেয়ার ফেলে কুলাউড়ার তৎকালীন তার সমসাময়িক স্বজনদের নিয়ে আড্ডা মারতেন , তার পকেটে থাকতো বনেদী লোকদের মত ক্যাপস্টেন সিগারেটোর সিগার ও ছোট্ট কাগজের বক্স ,তিনি সেই প্যাকেটি খুলে একহাতে সিগারেট তৈরী করে মনের সুখে টান দিতেন , কি যেন মিষ্টি একটা ধুয়ার গন্ধে আসে পাশে ছড়িয়ে যেত তার উপস্থিতি।
আমার নানী ছিলেন ভানুগাছের
করিমপুর চৌধুরী বাড়ীর কমরুল হাসান চৌধুরী ,কমরু মিয়া চৌধুরীর ছোট মেয়ে মনিরুন্নেছা খাতুন ওরফে কুটি বিবি , নানী সব সময় একটু গর্ব করেই বলতেন আমরা ভানু নারায়নের বংশধর ,আর তার মামাতো ভাই ছিলেন কানিহাটির এক প্রতাপ শালী “আব্দুল মান্নান চৌধুরী “উনার আর এক চাচাতো ভাই ছিলেন নাম করা ,তিনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরী ,যিনি মৌলভীবাজার মহকুমার তথা সিলেট জেলার রাজনীতির উজ্জলতরদের মধ্যে অন্যতম। তার কিছু বিশেষত্ব ছিল।যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা ।
কুলাউড়ার উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের কানিহাটিতে জন্ম নেয়া এই প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হজরত শাহ্ জালালের (রঃ) ঘনিস্ট সহযোগী হজরত শাহ্ হেলিম উদ্দিন নারলুলী (রঃ) এর বংশধর ।
ইটার রাজবংশের সাথে তার আত্মীয়তা ছিল।
তার পিতা খান বাহাদুর তজমুল আলি আমার জানা মতে প্রথম মুসলিম বাঙালি জেলা প্রশাসক। তিনি প্রথম জীবনে মৌলানা ভাসানির একজন ঘনিস্ট জন ছিলেন। তার সাথে হুসেন শহীদ সোরওয়ারদির যোগাযোগ ছিল খুবই অন্তরঙ্গ।
১৯৬২ সালে তিনি প্রথম কুলাউড়া বড়লেখা ও শ্রীমঙ্গলের একাংশ নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকার এম এন এ নির্বাচিত হন।
মৃত্যুপূর্বে সোহরোয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে পরামশ দেন যাতে মুন্তাকিম চৌধুরীকে তার দলে অন্তরভুক্ত করেন। ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু তাকে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু যোগ্য লোকদের তখন দলীয় নেতা হিসাবে নির্বাচন করছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি পুনরায় এম এন এ হিসাবে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ৪ নং সেক্টরের রাজনৈতিক সমন্বয়কের ভুমিকা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব জোনের অফিস পরিচালনা ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।
১৯৭২ সালে প্রথমে তিনি সংবিধান কমিটির গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন । পরে জাপান ও জার্মানির রাষ্ট্রদুত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী কালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। তিনি বহুদিন সৌদি আরব ও অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী জীবন যাপন করেন ।তার ঘনিস্ট রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন জনাব আজিজুর রহমান একসময় মৌলভী বাজারের জেলা পরিষদ প্রশাসক ছিলেন ,
আরো ছিলেন নবাব সফদর আলী খান রাজা সাহেব ,জয়নাল আবেদিন, লতিফ খান, আব্দুল জব্বার, নওয়াব আলী সরওয়ার খান চুন্নু , জুবেদ চৌধুরি, মুকিমুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ জামালুদ্দিন সহ আরো অনেকেই ..
বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই ভুলতে বসেছে তাদেরকে ইদানিং , কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে কে এই এই ব্যারিষটার মুন্তাকিম চৌধুরী ?
অথচ সকলেরই জানা উচিত তার কথা , জুবেদ চৌধুরীর কথা, এম. পি জব্বার মামার কথা , জয়নাল আবেদিনের কথা, সৈয়দ জামালের কথা,আকমল হোসেনের কথা , আলাউদ্দিন চেয়ারম্যানের কথা, রাজা সাহেবের কথা , আব্দুল গফুরের কথা , নাগেন্দ্র মালাকারের কথা, অনুপম কান্তির কথা , রসন্দ্র ভট্টের কথা , মুক্তিযুদ্ধে যাদের বলিষ্ঠ অবদানের কথা , যোগ্য নেতৃত্বর কথা , যাই হোক বলছিলাম তার ভাতিজা জুনেদ চৌধুরীর কথা যিনি প্রায়শই সকালে অথবা বিকালে তার ফুপুরবাড়ি উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ীতে আসতেন এবং ছোটবড় সকলের খোঁজ খবর নিতেন সখ্যতা ছিল বড় মামা আমির আলী ও ছোট মামা মুনির আলমের সাথে , আমাদের নানা বাড়ীর সামনের ঘরটি ফটিক বা বৈঠক খানা , ঐ ফটিকের সামনে ছিল শতবর্ষী বিরাট দিঘী আকৃতির একটি পুকুর যা এখন একজন বিতর্কিত জনপ্রতিনিধির লোলুপ কুদৃষ্টির ফলে পনবিহীন জাল দলিল ও জালিয়াতির মাধ্যমে একজন বিপথগামী বংশধরের সহায়তায় বিক্রিত জমি দেখিয়ে প্রশাসন ও স্থানীয় জনগনের চোখের সামনেই বিলীন হওয়ার পথে ‘এজমালী ‘ঐ পুকুরটি যে পুকুরটির স্বচ্ছ পানি পান করেছেন মুক্তি যোদ্ধারা , তা ছাড়াও যে কোন ফুটবল খেলা হলেই ঐ পুকুরে গোসল করতে দেখেছি , স্থানীয় ও আশে পাশের দুর দুরান্তের অনেক খেলোয়ার দের ,ঐ সময় অনেক বিশাল ব্যক্তিত্ব রাও ঐ পুকুরের পানি পান করেছেন ।
বলছিলাম জুনেদ মামাদের কথা উনারা ছিলেন তিন ভাই , জুনেদ মামা , জুবেদ মামা ও জিন বিজ্ঞানী আব্দুল মুসাকাব্বির চৌধুরী বা আবেদ মামা । জুবেদ মামা বা আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী ছিলেন কুলাউড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠকদের অন্যতম , মুক্তি যোদ্ধাদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষন কালে তিনি ভারতের কৈলাশটিলা ও ধর্মনগরে অবস্তান করে , রাজা সাহেব , জব্বার মামা , সৈয়দ জামালসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, সংগঠিত করতেন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ,কিভাবে কুলাউড়াকে শত্রু মুক্ত করা যায় , তার পরিকল্পনা করতেন ,যুদ্ধের সময় সংরামী একজন অগ্রনায়ক ছিলেন এই মুকতাদির চৌধুরী বা জুবেদ মামা , তার একটি ল্যানডরোভার জীপ ছিল , আর একটি জীপ পোস্ট অফিসের গেট পার হয়ে ,দক্ষিন বাজার মসজিদের প্রবেশপথের আগখানেই বহুবছর পরিত্যাক্ত অবস্তায় পরে ছিল । ঐ জীপে চড়ে আমরা ছোটবেলায় আমি , সাফি ,তহশীলদার সাহেবের ছেলে , (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ), রহমান ( বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী )ও ডাকবাংলোর লিটন ( বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ) উত্তর বাজারের বুলন , মতিন সহ অনেকেই বি এইচ স্কুলে পড়ার সময় , আসা যাওয়ার পথে খেলতাম ,বন্ধ জীপের স্টিয়ারীং ঘুরিয়ে গাড়ী চালাতাম । আহা কি দারুন স্বরনীয় ৭১ এর সেই ছোট বেলার দিন গুলির কথা । (চলবে )
ছকাপন ——
সৈয়দ শাকিল আহাদ
আখাউড়া থেকে ট্রেন যোগে সিলেট যাওয়ার পথে
ছকাপন রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন , এই ষ্টেশনের পাশে একটি স্কুল ও মসজিদ মাদ্রাসা রয়েছে , কুলাউড়া ও বরমচাল ষ্টেশনের মধ্যবর্তী ছোট এই স্টেশনটিকে ঘিরে রয়েছে অনেক সম্ভাবনা ।
জনবল সংকটের কারণে বর্তমানে স্টেশনটি বন্ধ আছে৷ সিলেট এবং কুলাউড়ার মধ্যে ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সালেরেললাইন নির্মাণ করা হয়।
এসময় কুলাউড়া-সিলেট লাইনের স্টেশন হিসেবে ছকাপন রেলওয়ে স্টেশন তৈরী করা হয়।
ছকাপন রেলওয়ে স্টেশনের উপর দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:
পাহাড়িকা এক্সপ্রেস
পারাবত এক্সপ্রেস
উদয়ন এক্সপ্রেস
জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস
উপবন এক্সপ্রেস
কালনী এক্সপ্রেস
সুরমা এক্সপ্রেস
জালালাবাদ এক্সপ্রেস
কুশিয়ারা এক্সপ্রেস
সিলেট কমিউটার , উল্লিখিত ট্রেনে চলাচল কারী সকল যাত্রীরাই কমবেশী ছকাপন স্টেশনকে চিনে থাকবেন ।একমাত্র সিলেট থেকে ছেড়ে আসা
লাতু র ট্রেন খ্যাত লোকাল ট্রেন ও আখাউড়া গামী মিক্সড ট্রেন আসা যাবার সময় এই ছকাপন স্টেশনে দাড়াতো ।আর অন্য কোন ট্রেন এই ষ্টেশনে দাড়াতো না । আশে পাশের গ্রামের লোকজন এই স্টেশন ব্যবহার করে অতীতে অনেক বেশি যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করেছেন , বিশেষ ভাবে ছকাপন , কিয়াতলা, ফরিদপুর , গোপীনাথপুর , রাফীনগর ,কৌলারশী, কাদিপুর , গোবিন্দপুর , হাসিমপুর , মনসুর , আমতৈল , মৈন্তাম, ভাগমতপুর, ইত্যাদি গ্রাম ঊল্লেখ যোগ্য বর্তমানে সড়ক পথের উন্নয়নের ফলে রেলপথে ভ্রমন বা ছকাপনের মত রেল ষ্টেশন এর গুরুত্ব নাই বললেই চলে । তবে অনেক স্মৃতি বিজরিত এই স্টেশন কে দেখলে আজও সিলেট বাসীর হৃদয়ে স্পন্দন জাগে ।
৭১ এর স্মৃতি -পর্ব – ২৭ ( তরফী সৈয়দ বাড়ী, পৃথিমপাশা)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
১৯৭১ সালের আগস্টের শেষের দিকে একদিন বড় মামা বাড়িতে এসে ভীষন খুশী মনে আমাদের সবাইকে জানালেন “ পাকিস্তানীরা পৃথিমপাশার সৈয়দ ছয়ফুল হোসেনকে ধরে আবার ছেড়ে দিয়েছে , এর আগেও একবার ধরেছিল এবং ছেড়ে দিয়েছে , তাৎক্ষনিক ভাবে তখন বুঝতে পারিনি কে ঐ সৈয়দ ছয়ফুল হোসেন , তবে তার কথা বিভিন্ন জনের কাছে শুনতে শুনতে তখন থেকেই তাকে দেখার এবং তার বাড়িতে যাবার ব্যাপারে আমার আগ্রহ তৈরী হয়েছিল ।
সেই আগ্রহ থেকেই সৈয়দ ছয়ফুল হোসেন এবং তার পরিবার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি , তিনি ছিলেন অত্যান্ত সাহসী তার জন্ম হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৪ ঠা জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৩ সালের ১২ ই অক্টোবর ।
জনদরদী এই নেতা বিরল প্রতিভার বিনয়ী ব্যক্তিত্ব, জনগনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সিক্ত হয়ে নিজের ,শ্রম মেধা,ও বুদ্ধি দিয়ে আপামর জন সাধারনদের মন জয় করেছিলেন । সেই সিংহপুরুষ সৈয়দ ছয়ফুল হোসেন ছাত্রাবস্তায় ই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলীম ছাত্র ফেডারেশন এর কর্মী পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মৌলভীবাজার মহকুমার প্রতিটি থানায় গন সংযোগের কাজে উপস্থিত থেকে আত্বনিয়োগ করেন । তিনি ভারত পাকিস্তান দেশ ভাগের পর তৎকালিন স্বৈরাচারী শাসক দের শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এই বৃহত্তর সিলেটের অন্যতম নেতা ছিলেন ।অন্যান্য নেতাদের সাথে নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের তেভাগা আন্দোলনে।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি এই অন্চলের জনগনের মধ্যে সকল শ্রেনীপেশার মানুষের কাছে বাংলা ভাষার দাবীর স্বপক্ষে উল্লেখ্যযোগ্য ভুমিকা পালন করেন ।১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ।৫৮ সালে আয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে তিনি কিছুদিন আত্মগোপনে থাকেন ।তিনি আয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনের এবং ফুলবাড়ি কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক ও নেতা ছিলেন ।৬২ র আয়ুব বিরোধী আন্দোলন , ৬৬ সালের ১১ দফা আন্দোলন , ৬৯ এর গন অব্যুথ্থান ও ৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন ।
১৯৭১ সালের সেই দিনের পর বুঝতে পেরেছিলাম , কোন না কোন ভাবে আমার মামা আমির আলী ও নানুর সাথে এবং আমার নানা বাড়ীর সাথে ঐ পৃথিমপাশা তরফী বাড়ীর সৈয়দ ছয়ফুল হোসেনের সংযোগ ছিল ।
কুলাউড়ার পৃথিমপাশাজমিদার বাড়ি. ইতিহাস আর ঐতিহ্যে টইটম্বুর এক জনপদের নাম হচ্ছে সিলেট।
সিলেটের রয়েছে নৈসর্গিক প্রকৃতিক সৌন্দর্য,ইতিহাস , ঐতিয্য ,লেখক ,সাধক , গায়কের আবির্ভাব ,রয়েছে বৃটিশ ও জমিদারী আমলের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যকীর্তি। জমিদারী আমলের স্মৃতি বিজড়িত এরকম এক ঐতিহাসিক এবং অপূর্ব স্থাপনার নাম এবং অসাধারন অলৌকিক ক্ষমতাধর বুযুর্গানদের ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে এই সিলেটে আগমন এবং বিভিন্ন অন্চলে অবস্তান ।সিলেটের পৃথিমপাশাজমিদার বাড়ি ও তেমনি একটি গুরুত্বপুর্ন ওঅর্থবহ বাড়ি ।এই বাড়ি সংলগ্ন তরফী বাড়িতেই জন্মেছিলেন সৈয়দ ছয়ফুল হোসেন ।
প্রায় দুইশ’ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে টিকে আছে কুলাউড়ার পৃথিমপাশাজমিদার বাড়ি বা নবাব বাড়ি । মৌলভীবাজার মহকুমা বা বর্তমানে জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার পূর্বে এবং কুলাউড়া থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিন পুর্বে এই জমিদার বাড়ির অবস্থান।
এই জমিদার বাড়ির কারুকার্যময় আসবাবপত্র, মসজিদের ফুলেল নকশা, ইমামবাড়া, সুবিশাল দীঘি যে কাউকে আকৃষ্ট করতে যথেষ্ট।
স্বাধীনতা যুদ্ধে এই পৃথিমপাশা নবাববাড়ি র ভুমিকা স্বরনীয় , পৃথিমপাশা নবাব বাড়ি নিয়ে একটি আলাদা পর্ব লেখা তৈরি করে রেখেছি যা অনেক তথ্যে সম্বৃদ্ধ রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস ।
এই নওয়াব বাড়ি সংলগ্ন তরফী সাহেব বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ ময়েজউদ্দিন ,
যিনি ছিলেন সিলেটের সুপরিচিত রাজ পরিবার তরফের অন্যতম শাখা ,নরপতি সাহেব বাড়ির অন্যতম জমিদার সৈয়দ আমিনউদ্দিন সাহেবের পুত্র ।
সৈয়দ ময়েজ উদ্দিনের বোনের নাম সৈয়দা ফাতেমা বানু , এই সৈয়দা ফাতেমা বানুর বিয়ে হয় পৃথিমপাশা র জমিদার নবাব আলী আমজাদ খানের সাথে ।যিনি ছিলেন নবাব আলী আমজাদ খানের প্রথম পত্নী ।জনশ্রুতি রয়েছে তিনি অত্যান্ত রুপসী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন ।
নবী বংশীয় এবং রাজ পরিবারের ঐতিয্য থাকার কারনে পৃথিমপাশার জমিদার নবাব আলী আমজাদ খান নরপতি র পশ্চিম হাবেলীতে এই পরিবারে সম্পর্ক স্হাপনে আগ্রহী হন ।নবাব আলী আমজাদ খান বাংলার শ্রেষ্ট পরাক্রমশালী জমিদার দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন । বৃটিশ শাসনআমলে তার ষ্টেটের ম্যানেজার ছিল একজন বেতনভুক্ত ইংরেজ ।পাহারাদার ছিল নেপালী ,সবসময় বাড়িতে ১০০ টি বন্দুক ছিল এবং বন্দুকধারী বাহিনীরা পাহারায় থাকত ।তিনি যখন নরপতি পশ্চিম হাবেলীতে সুন্দরী কন্যা সৈয়দা ফাতেমা বানুর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন নরপতির সৈয়দ রা সেই প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হন নাই যেহেতু নবাবেরা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায় , পরবর্তীতে রাজি হন এবং মহাধুমধামে বিয়ে সম্পন্ন হয় । ঐ বিয়েতে অতিথী হয়ে বরযাত্রীর বহরে ছিলেন বহু ইংরেজ , উপমহাদেশের বিভিন্ন গন্যমান্য পরিবারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা “ রাধা মানিক্য বাহাদুর “।
তখন চল্লিশটি হাতি নিয়ে বিরাট বরযাত্রী নরপতি এসে প্রায় একসপ্তাহ অপেক্ষা করে সৈয়দ সাহেবদের কে রাজি করিয়ে সৈয়দা ফাতেমা বানুকে বিয়ে করে পৃথিম পাশা নিয়ে আসেন ।
সেই ঘটনা সমগ্র উপমহাদেশে বিরাট চান্চল্য সৃষ্টি করে এবং বিলাত পর্যন্ত চাউর হয় যা বর্তমান যুগে অকল্পনীয় , সে কি ধৈর্য ? বিশাল বরযাত্রী নরপতি সাহেব বাড়ির সামনে অপেক্ষমাণ ,
না কোন যুদ্ধ জয়ের জন্য নয় , বিয়ে করার জন্য ,তা ও আবার
এক দুই দিন নয় – সাত দিন , ভাবতেও শীহরন জাগে যেখানে বর্তমান যুগে এখন কারও বিয়েতে শালা শালী দের আব্দার রক্ষার্থে গেইটে বরসহ মধুর বাকবিতন্ডায় একটু অপেক্ষা করতেই বরপক্ষ এবং অন্যান্য মুরব্বীরা অস্থির হয়ে উঠেন ।
যাই হোক সেই ঘটনায় নরপতি সৈয়দ সাহেব বাড়ি ও তখন অনেক শৌর্যবীর্যে মারাত্বক প্রতাপশালী ছিল যা অনুমেয় , যে বাড়ির সামনে অপেক্ষমাণ বরযাত্রীদের গ্রহনে দিনের পর দিন তারা সম্মত ছিলেন না । পরবর্তীতে অবশ্য তা মহা ধুমধামের সাথেই সম্পন্ন হয় ।এই সৈয়দা ফাতেমা বানু তার ভাই সৈয়দ ময়েজউদ্দিন হোসেনকে নবাব আলী আমজাদ খানের বোন লতিফা বানুকে বিয়ে দেওযার মাধ্যমে আত্বীয়তার বন্ধনকে আরো মজবুত করেছিলেন ।তৎপরবর্তিতে
নওয়াব আলী আমজাদ খান তার প্রিয় বোন লতিফা বেগমকে নরপতির সৈয়দজাদা , সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাসিরউদদিন (রঃ) এর উত্তরসুরী সৈয়দ ময়েজউদ্দিন হোসেনের সাথে বিয়ে দিয়ে পৃথিমপাশা নবাব বাড়ির পশ্চিমপাশ্বে অত্যানত্য সম্মানের সাথে আদরের বোনকে এক বিরাট বাড়ি তৈরী করে জমিদারীর থেকে বোনের অংশ দেন । যেহেতু সৈয়দ ময়েজউদ্দিন তরফ থেকে আগত এবং ঐ বাড়ীতে তাদের নরপতি থেকে প্রায়শই লোক সমাগম ঘটতো এবং তরফের আত্বীয় স্বজনেরা প্রথমে এখানে এসে বিশ্রাম নিয়ে পরে নবাব বাড়িতে তাদের মেয়ে সৈয়দা ফাতেমা বানুর কাছে যেতেন সেই হেতু এই বাড়িটিকেই অত্র অন্চলে “তরফী সৈয়দ বাড়ি “ বলে । এই সৈয়দ ময়েজ উদ্দিন হোসেনের তিন ছেলের একজন হচ্ছে সৈয়দ নুরুল হোসেন অপর দুই ছেলে হচ্ছে সৈয়দ সগিরুল হোসেন এবং সৈয়দ শামসুদ্দিন হোসেন । সৈয়দ নুরুল হোসেনের চার ছেলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ ছয়ফুল হোসেন ।
সৈয়দ সয়ফুল হোসেন সাহেবরা ৪ ভাই ১বোন ছিলেন।
উনাদের নাম হচ্ছে ঃ-
১.সৈয়দ বেনজির হোসেন উনি এমসি কলেজে ছাত্রাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।
২.সৈয়দ আমিরুল হোসেন ।
৩.সৈয়দ ছয়ফুল হোসেন ।
৪.সৈয়দ মকবুল হোসেন ।
৫.সৈয়দা সাকিনা বানু।
স্বামীঃসৈয়দ জামিলুর রহমান
অবঃ সি,ও(উন্নয়ন)রামশ্রী(সাহেব বাড়ী)চুনারুঘাট,তরফ,হবিগঞ্জ।
সৈয়দ ছয়ফুল হোসেনের স্ত্রীর নাম ছিল মমতাজুন্নিসা খাতুন।
তিনি ছিলেন ইলিয়াস আলী স্টেট এর ছোট সাহেববাড়ী/পৃথিমপাশা এর এর মেয়ে ।
সৈয়দ মকবুল হোসেন বিয়ে করেন উনার চাচাতো বোন সৈয়দ শামসুদ্দিন হোসেনের মেয়ে সৈয়দা আফতাবুন্নিসা বানুকে।
সৈয়দ আমিরুল হোসেন বিয়ে করেছিলেন নরপতি,মুড়ারবন্দে।উনার নাম এই মুহুর্তে স্বরণ নেই ।
এই তরফী সৈয়দ সাহেব বাড়ির বংশধরেরা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন , স্বল্প পরিষরে এই লেখাটি তৈরীতে অনেক সুযোগ্য নিকট আত্বীয়দের নাম উল্লেখ করতে পারি নাই , অনিচ্ছাকৃত এই চ্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখার অনুরোধ রইল ।
- এই পর্ব তৈরীতে ছবি সৌজন্যে সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন , সাবেক কাউন্সিলার ও নজরুল গবেষক , উপশহর সিলেট এবং আংশিক তথ্য সহায়তায় সৈয়দ এনায়েতুর রহমান – রামশ্রী সাহেব বাড়ী ও গবেষক ড. এস এম ইলিয়াস সাহেব ও ঢাকা নওয়াব বাড়ির সৈয়দ ইলিয়াস হোসাইন এর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই ।
( চলব)
৭১ এর স্মৃতি – পর্ব -৩৩ ( চাতলাপুর )
—- সৈয়দ শাকিল আহাদ
কানিহাটি পরগনার ১৯ টি মৌজা নিয়ে ৭৬৯২ একর জমি পরিবেষ্টিত একটি অন্যতম ইউনিয়ন হলো শরীফপুর , যা কুলাউড়ার অন্য ইউনিয়ন সমুহের চেয়ে একটু ভিন্ন , এই শরীফপুর ইউনিয়নের অনেকগুলো গ্রামের মধ্য অন্যতম একটি প্রসিদ্ধ এলাকা হচ্ছে “ চাতলাপুর “ ,
কুলাউড়ার দক্ষিনপুর্বদিকে চাতলাপুরে একটি চা বাগান রয়েছে । এই চা বাগান সম্বৃদ্ধ পাহাড়িয়া এলাকাটি ভারতীয় সীমান্তবর্তী এই ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সবুজে ঘেরা একটি স্থলবন্দরযুক্ত সুন্দর নয়নাভিরাম এলাকা ।
১৯৬৫ ইং থেকে দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন সন্জরপুর গ্রামের “ নৌসা মিয়া “.
এই ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ,চুয়াল্লিশপাট্টা,তিলকপুর,পালকিছড়া,দত্তগ্রাম,নিশ্চিন্তপুর,মাদানগর,দাউদপুর(সোনাপুর),হরিপুর,খিদিরপুর,মানগাও,মনোহরপুর,ইটারঘাট,চরিয়ারঘাট,কালবৈয়ারচর,তেলিবিল,চান্দপুর,পুর্বভাগ,সংগ্রামসিং,লালারচক,সন্জবপুর,বাগজুরা,নসিরগন্জ,বেরিগাও এবং শরীফপুর উল্লেখযোগ্য …
এই শরীফপুরের পুর্বভাগে বিশিষ্ট দরবেশ “ হাজী খা” এবং দত্তগ্রামে “ দেওয়ান শাহ “ এর মাজার রয়েছে ।
১৯৭১ সালে ভারত সীমান্তবর্তী এই গ্রামের উপর বয়ে যাওয়া অবাঞ্ছিত ঘটনা , রক্তপাত ,বিভিষীকাময় আতংকের বর্ননা ও ভয়াবহ পরিস্থিতি যারা মোকাবিলা করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দুএকটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না ,
পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এই চাতলাপুরের বি.ও.পি ক্যাম্প নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে অবস্তান নেয় ।
উল্লেখ্য যে চাতলাপুরের বিপরিতে ভারতীয় অংশে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি প্রশিক্ষন শিবির বা ক্যাম্প ছিল , দুই ভুখন্ডের দুইটি ক্যাম্প কাছাকাছি থাকাতে দুইটি ক্যাম্পের সকলকেই নির্ঘুম ,তটস্থ ও আতংকিত থাকতে হতো সর্বদা ,যে কোন সময় যে কোন পরীস্থিতি মোকাবেলার জন্য । তখন ভারতীয় ভুখন্ডের ক্যাম্প দুই দিক থেকে দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৩ জন করে সদস্যসম্বলিত দলে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকতে শোনা যায় , যার এফ এফ দলের নেত্বৃত্বে ছিলেন সৈয়দ মখলিছুর রহমান আর অন্যদিকে ১৩ জন সদস্যের এম এফ দলের নেত্বৃত্বে ছিলেন ই পি আরের অন্যতম সদস্য জনাব আবুল কাশেম যারা ।
আলীনগর বিএপির ক্যাম্পের নিকটবর্তীএকটি বাড়ীর জনৈক উস্তার আলীর দেওয়া তথ্যমতে,তার পিতা আব্দাল মিয়া ও ভাই মাসুক মিয়ার হত্যাকালীন বর্ননা রীতিমত লোমহর্ষক ।
আলীনগর বিওপি ক্যাম্পে দুইজন পান্জাবী ই পি আর সদস্যকে দুইজন বাঙ্গালী ইপি আর সদস্য হত্যা করে পালিয়ে গিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেয় ।
পরবর্তীতে পাক হানাদারদের নিয়ে চারটি জীপে করে স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের সহযোগীতায় তাদের মধ্যে পৃথিমপাশার ছতু মিয়া এবং খালিক মিয়া , পাস্ববর্তী ধলিয়া গ্রামের মনির এবং গলই ও তাদের পিতা ওয়াহিদ মিয়া সহ আরো কয়েকজন মিলে ক্যাম্প দখল করে নেয় ।
উস্তার আলীর মতে সেদিন পাক বাহিনীর সদস্যরা এসে উর্দুভাষায় জানতে চায় ,পান্জাবী বিওপি সদস্যদের কে কে হত্যা করেছে ?
সেই মুহুর্তে স্বাধীনতা বিরোধী পাক দোসরেরা আমার ভাই মাসুককে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে বলে আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেয় , মাসুক তখন বাবুর্চীর সহযোগী হিসাবে ক্যাম্পে কাজ করতো ।
ওদের কথামত পাকিস্তানী হানাদারেরা আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে আমার বাবা আব্দাল মিয়া ওরফে আব্দুল জব্বার এবং ভাই মাসই মিয়া ওরফে মাসুক কে ধরে হাত পা বেধে ক্যাম্পে নিয়ে বেধরক পিটাতে থাকে , বন্দুকের বাট দিয়ে মারতে থাকে আর জানতে চায় কে তাদের লোককে মেরেছে তাদের আর্তচিৎকার ও চেটামেচিতে গগন বিদির্ন হয় ।অসহ্য যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে আমার ভাই বলছিল “আমি জানিনা ,আমি সন্ধার আগে কাজ শেষ করে বাড়ি চলেগিয়েছি “ কিন্তু পাকিরা আমার ভাইয়ের কথায় কর্নপাত করেনি ,আরো জোরে লাথি গুতা মারতে থাকে , তাদের কে লুকলুকি গাছের সাথে বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন করে মেজর মোঘলের নির্দেশে গুলি করে নির্মম ভাবে হত্যা করে ,সেদিন গ্রামের আরো অনেককে ধরে এনে সারি বেধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হ্ত্যা করেছিল ।
উল্লেখ্য সেদিন সবাইকে লাইন ধরে দাঁড় করানোর পর লাইন থেকে আমাদের গ্রামের শক্ত সামর্থ মফিজ মাস্টার , গনি মিয়া , ও ওয়াব আলীকে দিয়ে ক্যাম্পের উত্তর পাশ্বে গর্ত করিয়ে সেই গর্তে মৃতদের মাটি চাপা দেয় ,সেদিন গর্তে মাটিচাপা দেবার সময় আমার বাবা শহীদ আব্দাল মিয়ার মৃতু হয়নি , অজ্ঞান অবস্তায় তখন তিনি পানি খেতে চেয়েছিলেন , যারা গর্তে মৃতদেহ ফেলছিল তাদের ইচ্ছা ছিল আমার বাবার নাক উপরে থাকুক যাতে তিনি স্বাসপ্রস্বাস নিতে পারেন , তখন এক বন্দুকধারী বিষয়টি অর্থাৎ আব্বা জীবিত উপলব্ধি করে তাৎক্ষনিক ভাবে তার হাতে থাকা বন্দুক থেকে গুলি করে আব্বার মৃত্যু নিশ্চিত করে ।
চোখের সামনে ভাই ও বাবাকে হারানোর দু:খ উস্তার মিয়া কখনওই ভুলবে না আর তাকে শান্তনা দেবার ভাষাও আমাদের নেই ।
তবে এই ইউনিয়নের পল্কি সেতু ধ্বংস করার মাধ্যমে পাক সেনাদের প্রতিহত করার সত্য ঘটনা সহ বেশ কিছু ঘটনা অন্য আর একটি পর্বে আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে ।অনেক মুক্তিযোদ্ধা সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন যাদের অবদান চির স্বরনীয় , তাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ না করে পারছি না ,যেমন :-
ক) মুরল বাউরি , পিতা :~ কালা বাউরি , গ্রাম :-৪৪ পাট্টা , মুক্তি নং ০৫০৪০৪০০০৬ ইউ:- শরীফপুর।
খ) দুলভ মিয়া ,পিতা :~ ওয়াহিদ আলী , গ্রাম :-চানপুর , মুক্তি নং ০৫০৪০৪০০০৭ ইউ:- শরীফপুর।
গ) আরশদ আলী পিতা :~ আরজু মিয়া , গ্রাম :-সনজবপুর, মুক্তি নং ০৫০৪০৪০০০৮ ইউ:- শরীফপুর।
ধ) মো: আতাউর রহমান পিতা :~ মো: আব্দুর রহিম , গ্রাম :-মানগাও , মুক্তি নং ০৫০৪০৪০০০৯ ইউ:- শরীফপুর।
এই আলোচনায় অনেক বেশী অবদান রাখার জন্য যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা ছিল যা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা বাতুলতা মাত্র , কৃর্তিমানদের আত্বত্যাগ এবং তাদের অবদান অপরিসীম যা অনস্বীকার্য।(চলবে)
“কালা পাহাড় “
সৈয়দ শাকিল আহাদ
সিলেটের পাহাড় নিয়ে অনেক দিন যাবত ভাবছি কিছু একটা লিখবো , কিন্তু শুরুটা কখন কিভাবে করবো ভাবতে ভাবতে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে ,
১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচিত্র সাপুড়ে তে কাননদেবীর কন্ঠে গাওয়া বিখ্যাত নজরুল গীতি “ আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ ..
ছোটবেলায় আমাদের হয়বতনগর দেওয়ানবাড়িতে একটি গ্রামোফোন ছিল , সবাই মিলে বিশেষ করে আমার চাচা সৈয়দ আব্দুল হাদী ওরফে মন্জুর মিয়া যখন আমাদের সবাই কে ডেকে এনে রেকর্ডে বাজিয়ে গান শুনাতেন তখন ঐ গানটি একটু বেশিই শুনতাম ,শুনতে শুনতে বড় হয়েছি আর ভেবেছি পাহাড় আবার ঘুমায় কিভাবে , যদি সুযোগ পাই তবে দেখবো সেই ঘুমের দৃশ্য .. আবার অন্য আর এক গান ছিল এ রকম ,,
রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি পড়ে ,
খাসিয়ারা বাঁশি বাজায় ঐ পাহাড়ে ..
এই মধুক্ষনে প্রিয়া তোমায় মনে পড়ে … হো হো হো… প্রিয় বন্ধু কামরুন নুর চৌধুরীর এই গানটি যতবার শুনেছি মনটা ছুটে গিয়েছে পাহাড়ে , তাও আবার কুলাউড়া অন্চলের কর্মধা ইউনিয়নের ঐতিহাসিক “কালা পাহাড়ে “
যাকে কুলাউড়ার পাহাড় ও বলে থাকেন কেউ কেউ ।
কুলাউড়া পাহাড় বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের বেগুণছড়া পুঞ্জিতে অবস্থিত একটি পাহাড় যাহার উচ্চতা ১০৯৮ ফুট। কালাপাহাড় সিলেট বিভাগের সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়া। এটা মূলত খাসিয়াদের গ্রাম। খাসিয়ারা গ্রামকে “পুঞ্জি” বলে। এর এক পাশে কুলাউড়া, অন্য পাশে জুড়ি উপজেলা ও ভারত সীমান্ত। এখানে আরো অনেক পুঞ্জি আছে। তাছাড়া এখানে ছোট বড় আরো বেশ অনেকগুলো পাহাড় আছে। আরো আছে চা বাগান সহ ছোট ছোট পরিষ্কার পানির ছড়া।
এই পাহাড়ের উচ্চতা সর্বোচ্চ বিন্দু এক হাজার ৯৮ ফুট (সমুদ্র স্তর থেকে) পরিমাপ করা হয় । কালাপাহাড়কে স্থানীয় ভাষায় লংলা পাহাড় নামে ডাকা হয়।
বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে, কালাপাহাড়টি ‘হারারগঞ্জ পাহাড়’ নামেও পরিচিত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় অবস্থান করা এই পাহাড়ের ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে পড়েছে এবং বাকি অংশ ভারতের উত্তর ত্রিপুরায় অবস্থিত।
ত্রিপুরায় এই পাহাড়টির বাকি অংশের রঘুনন্দন পাহাড় । ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ধর্মীয় স্থান ঊনকোটি এই পাহাড়টির পাদদেশে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে কালাপাহাড়ের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে হাকালুকি হাওরের নীল পানি দেখা যায়।
এখানে বলে রাখা ভাল সিলেট জেলার উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় বিদ্যমান আছে আর সিলেট জেলায় অনেক গুলো ছোট বড় পাহাড় রয়েছে যার মধ্যে নিম্নলিখিত পাহাড় গুলোর কথা
না বললেই নয় ,
১) পল্ডহরের বা সরষপুরের পাহাড় : – এই পাহাড়টি সিলেট জেলার পুর্ব দিকে সিলেট ও ভারতের কাছাড় জেলার মধ্যে অবস্থিত ।
এই পাহাড়টি উত্তর দক্ষিনে প্রায় ৫০ মাইল লম্বা আর প্রস্তে কোন কোন জায়গায় ১২-১৩ মাইল ।এর পুর্বদিকে ভারতের কাছার জেলা , পশ্চিমে পল্ ডহর , এগারসতী ও চাপঘাট পরগনা ইহার উচ্চ স্হান বা শৃঙ্গ ২০৩০ ফিট ।
২) দু আলিয়া বা প্রতাপগরের পাহাড়:-প্রতাপগড় পরগনার মধ্যে , উত্তরে ও দক্ষিনে প্রায় ৩০ মাইল , এই পাহাড়টি পল্ডহরের প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এর উচ্চতা সর্ব্বোচ্চ ১৫০০ ফিট ।
৩) আদম আইল বা পাথারিয়া পাহাড় :- এই পাহাড়টি দুআলিয়া পাহাড়ের কয়েক মাইল পশ্চিমে , উত্তর দক্ষিনে লম্বায় প্রায় ২৮,মাইল প্রস্তে কমপক্ষে ৭-৮ মাইল ।পুর্বে প্রতাপগড়, জফরগড় ও রবিনগর পরগণা আর পশ্চিমে পাথারিয়া ও শাহবাজপুর ।সর্বোচ্চ চুড়া ৮০০ ফিট উপরে , মাধবকুন্ড নামের জলপ্রপাত এই পাহাড়ের এক কোনে অবস্থিত ।
- ৪) ষাঁড়ের গজ বা লংলার পাহাড়
- এই পাহাড়টি আদম আইল পাহাড়ের পশ্চিমদিকে কয়েক মাইল দুরে অবস্থিত ।ইহার উত্তর দক্ষিনে প্রায় ১২ মাইল লম্বা , এই পাহাড়ের পু্র্বে পাথারিয় পরগনা এবং পশ্চিমে লংলা উচ্চতা ১১০০ ফিট ।
৫) আদমপুরের পাহাড় : লংলা পাহাড়ের দক্ষিন পশ্চিমদিকে উত্তরে দক্ষিনে প্রায় ২৩ মাইল লম্বা এই পাহাড়ের পুর্বদিকে আদমপুরে ইটা ও পশ্চিমে চোয়ালিশ , এই পাহাড় লংলা পাহাড় হতে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত । এর উচ্চতা ৬০০ ফিট ।
৬) বড়শী যোড়া বা বালিশিরার পাহাড় : এই পাহাড়টি আদমপুর পাহাড়ের দক্ষিন পশ্চিমে , এর দৈর্ঘ ২২ মাইল আর প্রস্ত ৪ মাইল এর পুর্বদিকে ভানুগাছ ও ছয়চিরি পরগণা পশ্চিমে বালিশিরা ও চুয়ালিশ এই পাহাড়ের উঁচু টিলার নাম চুড়ামনি টিলা যার উচ্চতা সমতল ভুমি হইতে ৭০০ ফিট ।
এই পাহাড়ের পাশ ঘিরে অনেক চা বাগান রয়েছে ।
৭) সাত গাঁও বা বিষ গাওয়ের পাহাড় :~ এই পাহাড়টি বালিশিরার পাহাড় হইতে ৮ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত , লম্বায় ২২ মাইল সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা ৭০০ ফিট ।এই পাহাড়ের পুর্বদিকে বালিশিরা সাতগাঁও ও পচাউন প্রভৃতি পরগণা ও পশ্চিমে তরফ ফৈজাবাদ ইত্যাদি পরগণা বিদ্যমান ।
৮) রঘুনন্দন পাহাড় :~ এই পাহাড়টি বৃহত্তর সিলেট জেলার দক্ষিন পশ্চিম দিকে অবস্থিত এটি বিষগাও পাহাড় থেকে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ।উচ্চতা ৭০০ ফিট ।
উপআলোচিত পাহাড় ছাড়াও আরো অনেক ছোট বড় পাহাড় , টিলা এই সিলেট বিভাগকে প্রাকৃতিক নৈস্বর্গীক সৌন্দর্যে সম্বৃদ্ধ করে রেখেছে , যেমন ইটার পাহাড়, লাইড়ের পাহাড় , মিনারের টিলা , দেউলির টিলা , ইত্যাদি ।
পাহাড়ের সৌন্দর্য আমাদের সিলেট এর অহংকার এবং পর্যটক দের কে আরো বেশি আকৃষ্ট করে থাকে ।
সিলেট কে সকলেই পীর ফকির অলী আওলীয়াদের বিচরনে বিশেষ করে বাবা হযরত শাহজালাল ( রঃ) এবং উনার সাথী ৩৬০ আওলিয়ার পুণ্যভুমি হিসাবে পবিত্রতার সাথে চিন্হিত হয়ে আসছে ।
( তথ্য কৃতজ্ঞতায় :~ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত – অচ্যুতচরন চৌধুরী)
৭১ এর স্মৃতি – পর্ব ২৮ ( পৃথিমপাশা)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
১৯৭১ সালে এই অন্চলের একজন অন্যতম বিশ্বস্থ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ‘রাজা সাহেব ‘। রাজা সাহেব কে আমি কখনও দেখি নাই তবে তার সম্পর্কে আমার বড় মামা আমির আলী ও পরিবারের অন্যান্য সকলের কাছে ছোট বেলায় এত শুনেছি যার বদৌলতে শুনতে শুনতে তার প্রতিকৃতি ও অস্তিত্ব মনের মাঝে গেথে আছে এবং তার সেই পৃথিমপাশা নবাব বাড়ি সম্পর্কে এত বেশি ভাল কথা শুনেছি যা বলে বা লিখে শেষ করতে পারবো না তারপর ও একটু চেষ্টা করে দেখি ,
কথায় আছে ,
“বেটা থাকলে আলী আমজাদ
আর সব পুয়া
হাওড় থাকলে হাকালুকী
আর সব কুয়া !”
সিলেটের এই বিখ্যাত প্রবাদ দিয়েই এই পর্ব শুরু করছি ,
পৃথিমপাশা নবাববাড়ী মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে ৪৭ কিলোমিটার পূর্বে ২৫ একর বিস্তৃত সাজানো-গোছানো জমিদার বাড়ির অবস্থান ।পুরোনো কয়েকটি স্থাপনার সঙ্গে রয়েছে জমিদার নির্মিত শিয়া সম্প্রদায়ের একটি চমৎকার নকশা খচিত ইমামবাড়া।
প্রত্যেকটি স্থাপনাতেই আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।
পাশেই রয়েছে চমৎকার শান বাঁধানো ঘাটসহ সুবিশাল দীঘি।
পৃথিমপাশা জমিদার বাড়ি
যা পৃথিমপাশা নবাব বাড়ি নামেও
পরিচিত , সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় জমিদারী আমলের স্মৃতি বিজড়িত এক ঐতিহাসিক এবং অপূর্ব স্থাপনার নাম পৃথিমপাশা জমিদার বাড়ি। পৃথিমপাশায় রয়েছে দু’টি জমিদার বাড়ি। এই জমিদার বাড়ির মতো জীবন্ত জমিদার বাড়ি বাংলাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই ।
ইরানের রাজা রেজা শাহ পাহলভি এই বাড়ি সফরে আসেন তখন তার সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা দিতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রধান হুকুম জারি করলে আইয়ুব খান কে পাঠানো হয়।
পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে এই আইয়ুব খান ই
মার্শাল’ল জারি করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হোন।
এই এলাকাটি এক সময় ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার পাহাড়ি এলাকায় নওগা কুকি উপজাতির বেশ প্রতাপ ছিল। শ্রীহট্ট সদরে যা বর্তমানে সিলেট ,সেই সময় একজন কাজী ছিলেন যার নাম মোহাম্মদ আলী। ১৭৯২ সালে ইংরেজ শাসকদের পক্ষ হয়ে নওগা কুকিদের বিদ্রোহ দমনে মোহাম্মদ আলী গুরত্বপূর্ন ভূমিকা রাখেন।
ইংরেজ সরকার এতে খুশি হয়ে মোহাম্মদ আলীর পুত্র গাউস আলী খাঁনকে ১২০০ হাল বা ১৪,৪০০ বিঘা জমি দান করেন।
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রাম থেকে হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী সৈন্য সিলেট আসলে তার সমর্থন চান।
তিনি সরাসরি সাহায্য না করে তাদেরকে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান করার পরামর্শ দেন।
যুদ্ধ শেষে গাউস আলী খানকে বিদ্রোহে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে ,তবে প্রমানের অভাবে ছেড়ে দেয়া হয়।উত্তরাধিকার সূত্রে এউ জমিদারীর মালিক হন তার ছেলে আলী আহমদ খান।
আলী আহমদের সময়ে জমিদারীর আয় ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ব্রিটিশ আনুকুল্যও লাভ করেন। তার সময়ে চাদনীঘাট এবং সুরমা নদীর তীরে সিলেট শহরের গোড়াপত্তন হয়। ১৮৭২ সালে ছেলে আলী আমজাদ খানের নামে একটি ক্লক টাওয়ার স্থাপন করেন যা এখন আলী আমজাদের ঘড়ি নামে বিখ্যাত। নবাব আলী আমজাদ খাঁন তখনকার সময়ে বৃহত্তর সিলেটের মধ্যে সবচেয়ে স্বনামধন্য এবং প্রভাবশালী জমিদার ছিলেনে। । সিলেটের বিখ্যাত সুরমা নদীর তীরে চাঁদনীঘাটের সিঁড়ি সমাজসেবায় তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। ঐ সময় পৃত্থিমপাশা জমিদার বাড়িতে ত্রিপুরার মহারাজা রাধা কিশোর মানিক্য বাহাদুরসহ বহু ইংরেজ ভ্রমণ করে গেছেন। ইরানের রাজাও ভ্রমণ করে গেছেন। জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য ধরে রাখতে আলী আমজাদ খাঁন মৌলভীবাজার ও কুলাউড়ায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং সুপেয় পানির জন্য দীঘি খনন করেন।
উল্লেখ্য,
সিলেটের সুপরিচিত রাজপরিবার তরফের অন্যতম শাখা ,সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাসিরউদদিন (রঃ) এর উত্তরসুরী নরপতি সাহেব বাড়ির অন্যতম জমিদার সৈয়দ আমিনউদ্দিন সাহেবের পুত্র ।
সৈয়দ ময়েজ উদ্দিনের বোনের নাম সৈয়দা ফাতেমা বানু , এই সৈয়দা ফাতেমা বানুর বিয়ে হয় পৃথিমপাশা র জমিদার নবাব আলী আমজাদ খানের সাথে এবং অপর বোন সৈয়দা রহিমা বানুর বিয়ে হয় কুলাউড়ার আর এক জমিদার বাড়ি জয়পাশা খন্দেগার বাড়ীতে , , সৈয়দা ফাতেমা বানু যিনি ছিলেন নবাব আলী আমজাদ খানের প্রথম পত্নী ।জনশ্রুতি রয়েছে তিনি অত্যান্ত রুপসী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন ।
নবী বংশীয় এবং রাজ পরিবারের ঐতিয্য থাকার কারনে পৃথিমপাশার জমিদার নবাব আলী আমজাদ খান নরপতি র পশ্চিম হাবেলীতে এই পরিবারে সম্পর্ক স্হাপনে আগ্রহী হন ।নবাব আলী আমজাদ খান বাংলার শ্রেষ্ট পরাক্রমশালী জমিদার দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন । বৃটিশ শাসনআমলে তার ষ্টেটের ম্যানেজার ছিল একজন বেতনভুক্ত ইংরেজ ।পাহারাদার ছিল নেপালী ,সবসময় বাড়িতে ১০০ টি বন্দুক ছিল এবং বন্দুকধারী বাহিনীরা পাহারায় থাকত ।তিনি যখন নরপতি পশ্চিম হাবেলীতে সুন্দরী কন্যা সৈয়দা ফাতেমা বানুর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন নরপতির সৈয়দ রা সেই প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হন নাই যেহেতু নবাবেরা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায় , পরবর্তীতে রাজি হন এবং মহাধুমধামে বিয়ে সম্পন্ন হয় । ঐ বিয়েতে অতিথী হয়ে বরযাত্রীর বহরে ছিলেন বহু ইংরেজ , উপমহাদেশের বিভিন্ন গন্যমান্য পরিবারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা “ রাধা মানিক্য বাহাদুর “।
তখন চল্লিশটি হাতি নিয়ে বিরাট বরযাত্রী নরপতি এসে প্রায় একসপ্তাহ অপেক্ষা করে সৈয়দ সাহেবদের কে রাজি করিয়ে সৈয়দা ফাতেমা বানুকে বিয়ে করে পৃথিম পাশা নিয়ে আসেন। নবাব আলী আমজাদ ছিলেন এই বাংলার প্রথম মুসলিম টি প্ল্যান্টার বা চা বাগান মালিক।এই নবাব বাড়ীর প্রধান ফটকের সামনে দুই পাশ্বে দুইটি বাঘের খাঁচা ছিল । সেখান থেকে জীবন্ত বাঘের তর্জন, গর্জন শোনা যেত ।
আলী আমজাদ খানের পুত্র নবাব আলী হায়দার খান ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। পৃথিমপাশা নবাব পরিবারের আলী সরওয়ার খান আওয়ামী লীগের টিকেট পেয়ে প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন ।এই পরিবারের অন্যতম সদস্য ও ভাসানী ন্যাপের অন্যতম সিনিয়র নেতা নবাব আলি সফদর খান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম একজন বলিষ্ঠ সংগঠক ও স্থানীয় জনগনের অত্যান্ত আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য নেতা ছিলেন ।
তিনি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করেন ।তাকে হত্যা করার জন্য পাক বাহিনী বহুবার বিভিন্ন স্হানে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় ।
আবার এই নবাব পরিবারের আর এক উশৃংখল সদস্য পাকিস্তানপন্থী হানাদার বাহিনীর একজন যোগসাজশকারী হিসাবে সর্বত্র গন্য ছিলেন ।
তারই আহব্বানে নবাব বাড়িতে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল এবং পাক হানাদারদের দ্বারা বেশ কিছু মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে ।
এমনকি নবাব আলী সফদর খানের বসত বাড়ীতে একজন পাক আর্মি অফিসারের আস্তানা গড়ে উঠেছিল তিনি তখন সপরিবারে ভারতে অবস্তান করছিলেন ,
তার স্ত্রী পুত্রদের ভারতের আগরতলায় আত্বীয়ের বাড়ীতে রেখে তিনি মুক্তিযাদ্ধা শিবিরে সংগঠক হিসাবে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন, তাদের খাবারের ব্যবস্তা করে দিতেন ।
তিনি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করেন ।তাকে হত্যা করার জন্য পাক বাহিনী বহুবার বিভিন্ন স্হানে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় ।
অন্যায়ের সাথে ‘রাজা সাহেব’ কখনই আপোষ করেন নাই ।
তিনি সংগ্রাম করেছেন জমিদার পিতার বিরুদ্ধে , অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এই জননেতা ১৯৭৪ সালের ১৬ ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন ।
পৃত্থিমপাশা জমিদার পরিবারের পরবর্তী সন্তানগন ও সমাজসেবা ও জনহিতকর কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন ,রাজা সাহেবের ছেলে ‘নবাব আলী আব্বাস খান ‘ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ এবং তিন বার সংসদ সদস্য ছিলেন , আপামর জনসাধারণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন । তিনি এই নির্বাচনী এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ছোট ছেলে ‘নওয়াব আলী নকী খান’ এই ইউনিয়নের দীর্ঘদিন জনপ্রিয় চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বর্তমানে বাড়িতেই অবস্তান করছেন ।
সারাদেশের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে রয়েছে এই পরিবারের আত্বীয়তা এবং সুসম্পর্ক ।
এই বাড়ির ভেতর সবকিছু পুরানো আমলের কারুকাজ খচিত মনে হলেও সেগুলো পরিষ্কার ঝকঝকেই আছে এখনো। জমিদারদের ব্যবহার করা অনেক জিনিসপত্র রয়েছে এ বাড়িতে। রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এখানে লোক রয়েছে। নবাব আলী আমজাদ খাঁর উত্তসুরিরাই বর্তমানে দেখাশুনা করেন জমিদার বাড়িটি এবং দেশে বিদেশে প্রচুর বংশধর ও আত্বীয় স্বজনেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্তান করছেন , অগনিত বহু বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তির আগমন ঘটেছে এই বাড়িতে , সেই উছিলায় কুলাউড়াতে , বাংলার ইতিহাসের অগ্নিস্বাক্ষী এই নওয়াব বাড়ির কথা লিখে শেষ করার মত নয়।
বহু ইতিহাস বিদ , গবেষকগন নানা ভাবে , নানা বইতে এই বাড়ি ও এই বাড়ির কৃতিমান দের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন , এমন কি গুগুল , উইকিপিডিয়া তে ও ব্যাপক আকারে পৃথিমপাশা নবাব বাড়ির কথা উল্লেখ রয়েছে , বিভিন্ন মাধ্যম থেকে টুকিটাকি তথ্য সংগ্রহ করে এই পর্বটি তৈরী করেছি , উইকিপিডিয়া সহ সকলকে কৃতজ্ঞতাজানিয়ে এই পর্ব শেষ করছি, ছবি সৌজন্যে সৈয়দ মিসবাহউদ্দিন , সিলেট। (চলবে)
৭১ এর স্মৃতি (১৪ )
সৈয়দ শাকিল আহাদ
আমির আলী ও মনির আলম নামে আমার দুই মামা ছিলেন , দুইজনই প্রয়াত ,বড় মামা আমির আলী ছিলেন অত্যান্ত্ সাহসী , অনর্গল ভাল ইংরেজী বলতে পারতেন , খুবই সৌখিনতায় ভরপুর ছিল তার জীবন তার সাথে সখ্যতা ছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে প্রায় সকল সংগঠকদের সাথেই , তিনি সরাসরি যুদ্ধ করেনি কিন্তু তাদের সাথে ছিলেন তবে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মত কখনই বাহাদুরী করেন নাই বা মুক্তিযাদ্ধা হিসাবে কোথাও নিজেকে জাহির করেন নাই , তবে জুবেদ মামা , জব্বার মামা , জয়নাল মামা ও আত্তর আলী মামা দের সাথে বর্ডার ক্রস করে , ধর্মনগর ক্যাম্পে গিয়েছ্লেন , আবার দেশের মাটিতে মা বোনদের অবস্তান ও নিরাপত্তার স্বার্থে ফিরেও চলে এসেছিলেন ,এমনকি যখন কুলাউড়াতে পাকিস্তানীদের হটিয়ে প্রশিক্ষন ক্যাম্প হয়েছিল তখন কি কারনে জানি কমান্ডারের সাথে কথা কাটাকাটি করে বড় মামা তাকে চড় মেরে বেড়িয়ে পড়েন আর ক্যাম্পে যান নাই তবে সার্বিক ভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছিলেন ক্যাম্পের সকলকেই ,উছলাপারার খান সাহেবের ছেলে আমির আলীকে চিনতো না এমন লোক খুউব কমই ছিল , তার সহযোগীতার জন্যই তখন অনেক বর্ষীয়ান নেতা ও সংগঠকদের দেখেছি আমাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতে , এবং ঐ সময় যখনই কুলাউড়ার কোন নামী দামী লোক , মুক্তিযুদ্ধের সংগঠককে বড় মামা বাড়িতে নিয়ে আসতো সাথে সাথেই
নানীকে দেখতাম ব্যস্ত হয়ে যেতে , তেমনি একদিনের ঘটনা , বাড়িতে আসলেন জব্বার মামা ও হোসেনপুরের আত্তর আলী মামা, বসলেন ফটিকে , তাদের সাথে ধুতি পরা একজন লম্বা হিন্দু নেতাও ছিলেন , উনাদের দেখে নানী কি খাওয়াবেন ব্যস্ত হয়ে পরলেন ,উনি বাড়ীর পিছনের পুকুর ঘাটের কাছে গিয়ে
ডাক দিলেন ,একবার পশ্চিম দক্ষিনকোণে মুখ করে “ হেরে বে সাফিয়ার বউ “ হলে আও ,
আরেক বার পশ্চিম উত্তর কোণে মুখ করে “ ওগো মৌলা’র মা “ রুশে আও ,বাড়িত মেমান আইছোইন, বাড়ির পশ্চিম দিকের দেওয়ার ( মাটির সীমানা প্রাচীর )পেরিয়ে ছুটে এসেছিলেন ,, সাফিয়া মামুর বউ এবং ইদ্রিস মামুর বউ ‘ মৌলা ভাইয়ের আম্মা ,
তারা দ্রুত নানুকে সহযোগীতা করেছিলেন,সকলকে আপ্যায়ন করার জন্য ,
তখন আমাদের বাড়িতে আলাদা গরুর ঘর ছিল , চা বানানোর জন্য সেদিন গরুর দুধ দোহানোর দৃশ্যও মনে পরে ,আর একটি বিষয় রং চা বা লিকার চা আপ্যায়ন করতে অনেক বেশি বিব্রত বোধ করতো সকলেই কারন লিকার চা খেত কিছুটা অসচ্ছল ও গরীব লোকেরা এই জাতীয় একটা ধারনা সর্বত্র বিরাজ মান ছিল ,
রান্নাঘর বা উন্দাল ও দুরত্বে ছিল , এখনকার মত এটাচ্ড বাথরুম বা রান্নাঘর কারো বাড়িতেই তেমন একটা দেখা যেতো না ,
হ্যা, বলছিলাম
জব্বার মামা’র কথা ,আত্তর মামার কথা ,
সেদিন বড় মামা উনাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ,
, “ওগু অইল আমার বাইগনা ,
ছুটো আফার ফুয়া , “
সেই থেকে উনাদের” মামা মামা” বলেই ডাকতাম ,
জব্বার মামা ছিলেন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সাবেক সংসদ সদস্য,তিনি ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা, ঊনসত্তরের অভ্যূত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সংঘঠক ও যোদ্ধা।
তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সভাপতি ও ১৯৬৪ সালে কুলাউড়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক।
বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার প্রতিবাদ করায় ১৯৭৭ সালে ১১মাস কারাবদ্ধও ছিলেন আমাদের এই
আব্দুল জব্বার মামা
আব্দুল জব্বার মামার জন্ম হয়েছিল ২৭ শে নভেম্বর ১৯৪৫ সালে আলাল পুর গ্রামে , তার পিতা ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ।
তিনি ২৮ আগস্ট ১৯৯২ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারে তাকে ২০২০ সালে মরনোত্তর একুশে পদক প্রদান করে।
১৯৭১ সালে মাতৃভূমির মুক্তির স্বার্থে বাংলার অন্যান্য সব দামাল ছেলেদের মতই ২৬ বছরের টগবগে যুবক আক্তার আলী চৌধুরী আত্তর মিয়াও ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে।
যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেকটাই নিভৃতচারী ছিলেন তিনি ,যুদ্ধ শেষ হলেও সোনার বাংলা গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। দেশের নিপীড়িত ও নিগৃহিত মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন আমৃত্যু। দেশপ্রেমী এই বীরের জন্ম মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ার কাদিপুর ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর বাবার নাম ইদ্রিস আলী ও মাতার নাম লতিফা বিবি, চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট ।আত্তর আলী উচাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ চুকিয়ে ভর্তি হন নবীনচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে পড়াশুনা শেষ করেন তিনি। ওই সময় ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে।
৬৬’র দিকে তৎকালীন মন্ত্রী দেওয়ান বাছিত নিজ এলাকায় সফরে আসলে ওইসময় পাক সরকারের দুঃশাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি এবং তাঁর সহযোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর আতিক কালো পতাকা তুলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এর দায়ে পাক পুলিশ বাহিনী তাকে এবং তার বন্ধু ওমর আতিককে গ্রেফতার করে মৌলভীবাজার জেলে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁরা বেশ কয়েকদিন জেল খেটে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন। এভাবেই তৎকালীন সরকারের দুঃশাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি।
১৯৭১ সালে জুলাই মাসের দিকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের ধর্মনগর শহরের ভাগপুর স্কুল ক্যাম্পে যোগ দেন।
সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৪নম্বর সেক্টরের কমান্ডার সি আর দত্ত’র অধীনে কৈলাশহর হয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে শমসেরনগর, পতনউষারসহ কয়েকটি স্থানে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন।
এসব যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের পরাজিত করে এসকল এলাকা পাকবাহিনী মুক্ত করেন।
নভেম্বর মাসের শেষের দিকে মৌলভীবাজার সরকারি স্কুলে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন তিনিসহ তাঁর সহযোদ্ধারা। সেখান থেকে পাক বাহিনীকে হটিয়ে ওই স্কুলটি মুক্তিযোদ্ধারা দখল নেন এবং সেখানে তাদের ক্যাম্প গড়ে তুলেন।
ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ওই ক্যাম্পে পাক বাহিনীর যুদ্ধে ব্যবহৃত ল্যান্ড মাইন ও মর্টার সেল বিষ্ফোরণ ঘটে ।
এতে সেখানে অবস্থানকারী বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। ভাগ্যক্রমে ঘটনার সময় আত্তর আলী ও তাঁর কিছু সহযোগী সেখানে অবস্থান না করায় ওই সময় বেঁচে যান।
কুলাউড়া থেকে যে কয়জন ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শ পেতে পারতেন, তাদের মাঝে তিনি ছিলেন অন্যতম।
চুন্নু নওয়াব, রাজা সাহেব, আলাউদ্দিন চৌধুরী এ সব ব্যক্তিবর্গের সাথে ছিলো প্রতিদিনের চলাফেরা।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসাদুর রহমান, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা লাল মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক কুলাউড়া উপজেলা কমান্ডার আজহার আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক চেয়ারম্যান মুকিমুদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর আতিক, আলাউদ্দিন চৌধুরীদের সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তার আলী ওরফে আত্তর মিয়া , তিনি
পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন।
মৃত্যুর আগে তিনি আলহাজ্ব কমরউদ্দিন ওয়াকফ এস্টেটের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
২০০২ সালে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক বছর বার্ধ্যক্যের সাথে যুদ্ধ করে ২০০৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কুলাউড়ার কাদিপুরের হোসেনপুর গ্রামে পারিবারিক কবর স্থানে এই বীরযোদ্ধাকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়। আত্তর আলী ছিলেন পরপোকারী মানুষ। যুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু পল্টনে তাকে দোতলা একটি বাড়ি উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি না নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু ফেনী পুলিশ কোয়ার্টার পরিদর্শনে গেলে, সেই কোয়ার্টারে অবস্থান করছিলেন আত্তর আলীর মেজ ভাই (পুলিশ) আজমল আলীর স্ত্রী।
তখন বঙ্গবন্ধুর সাথেই গাড়ী থেকে বের হয়ে এসেছিলেন হালকা পাতলা গড়নের আত্তর আলী।
যা দেখে মরহুমের ভাবী অবাক হয়ে হয়েছিলেন। সিলেটের গৌরব মরহুম দেওয়ান ফরিদ গাজী, মরহুম সামাদ আজাদ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মরহুম আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদের সাথেও ছিলো খুবই ভালো সম্প্রীতি। এলাকার মানুষ তার হাসি মুখ ছাড়া কখনওই গোমড়া মুখ দেখেন নি। ঢাকাস্থ রামপুরার নীজ বাসভবনের এলাকাতেও সকলের প্রিয় পাত্র ছিলেন তিনি।
আমরা তাদের বিদ্বেহী আত্বার শান্তি কামনা করি । আমিন ।
(এই আত্তর আলী মামার পর্বটি তৈরীতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন আত্তর আলি মামার ছেলে আনিসুর রহমান লিটু।)
( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি ৩৮ ( কুলাউড়া -৪)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
১৯৭১ সালের ৬ ই মে র কথা , যখন পাকিস্তানি হানাদারেরা কুলাউড়া এসে পড়েছে , সেদিন সবাই হন্তদন্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটছিল তখন ১০ টা ১১টার দিকে আমার ছোট মামা মনির আলম কাকে যেন বলে দক্ষিন বাজার থেকে একটি রিক্সা নিজে চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন , বাড়ি থেকে মুল্যবান ট্রাংক গুলো নিরাপদ স্থান অর্থাৎ আমাদের এক নানা মানে হাসিমপুরের মকবুল আলী (মহরী )নানার বাড়ীতে পৌছানোর জন্য । তিনটি বড় বড় ট্রাংক , জমিজমার দলিলাদি মুল্যবান কাগজপত্র , গয়নাগাটি সহ , আমাকে সাথে নিয়ে ছোট মামা রিকশাওয়ালা সেজে পাকিদের সামনে দিয়ে এই দক্ষিন বাজারের উপর দিয়ে হাসিমপুর মকবুল আলী নানার বাড়িতে গিয়েছিলাম , যুদ্ধের সময় বেশ কিছুদিন আমরা সেখানে নিরাপদে ছিলাম ।
দক্ষিন বাজারকে তাই সর্বদাই মনে পড়ে ।কুলাউড়াতে কাটানো শৈশবের সেই দিনগুলোতে তো আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় তবে সেই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আমার সাথে অনেকেই আছেন যারা ঘাপটি মেরে চুপচাপ বসে আছেন , মাঝে মাঝে নিজেদের মোবাইল বা সেলফোনটি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে থাকেন শৈশবের স্মৃতি মনে করে , বন্ধু বান্ধবদের খোঁজেন , কিছু কথা বলার জন্য এবং পুরোনো স্মৃতি রোমমন্থন করো আনন্দ নেবার জন্য , কোন একটা ভাল লাগা নিয়ে তো সময় কাটাতে হবে ? তাদের জন্য কিছু একটা করতে ইচ্ছে হয় , সেই দায় থেকেই আমার চেষ্টা , কিছু একটা লিখে রাখতে পারলে হয়তো আগামীতে কারো না কারো কাজে লাগবে । কি কাজে লাগবে ? কিভাবে লাগবে ? কেন লাগবে ? কখন লাগবে সেটা ভেবে কোন সুরাহা করতে পারবো বলে মনে হয় না । কিন্তু আমি বিশ্বাস করি কিছু লেখে রাখা ভাল , কিন্তু লিখবো কি করে ? লেখা তো আসে না , লিখতে হলে পড়তে হয় । সময় করে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় , কখন পড়বো ? পড়ার সময় কোথায় ? গত কিছু কালে যে পরিমান বই পেয়েছি পড়ার জন্য , যদি আজ থেকেই পড়া শুরু করি ,এক নাগাড়ে পড়লেও কমপক্ষে বিশ বছর সময় লাগবে শেষ করতে , এর ভিতর তো আগামীতে আরো বই সংগ্রহ হবে , মাঝে কয়েক বছর আগে ভেবে রেখেছিলাম এক নাগারে প্রথমে এক সপ্তাহ বই পড়বো তারপরে এক মাস তার পর তিন মাস তারপর এক বছর ক্রমান্নয়ে বই পড়বো , কি হবে জানিনা ইহজীবনে সেই ইচ্ছার “ বই পড়া হবে কিনা ? বই পড়ার ইচ্ছা ছিল ছোট বেলা থেকে , পারিনি তা পুরন করতে , আগামীতে তা পুরণ হবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই ।
একটু একা থাকলেই শুধু মনে পড়ে অতীতের কথা , পুরোনো দিনের কথা ঃ-
কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “
“পুরানো সেই দিনের কথা
ভুলবি কিরে হায়
ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা
সে কি ভোলা যায় ?”সত্বিই ভোলা যায় না , যেমনি ভুলতে পারছি না কুলাউড়ার পাঠশালার কথা , পাঠশালা বলতে দক্ষিন বাজার বি.এইচ ( বশিরুল হুসেন ) প্রাইমারী স্কুলকেই বুঝাতে চেষ্টা করছি ।
১৯৭২ সালে আমার নানা মরহুম এ এম আশরাফ আলী খান সাহেব যাকে কুলাউড়ার জনগন সাবরেজিষ্টার সাহেব বলতো , আমাকে ঐ স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করান ও ভর্তি করিয়ে ফেরত আশার সময় একটি কাঠের শ্লেট ও চকপেন্সিল এবং কমলা / গোলাপী রংগের বাল্যশিক্ষা বই কিনে দিয়েছিলেন ।ফেরার পথে মোড়ে মোমিনের দোকান থেকে কাঁচের বয়ামে রক্ষিত ছিল , লুডুর ছক্কার মত রং বেরং এর ছোট ছোট কয়েকটি চকলেট ও লেবেন চুস কিনে দিয়েছিলেন । সেই মমিন সাহেবের দোকানের সামনেই রাস্তার মুখে একটি ছোট কালভার্ট ছিল যা অনেকের হয়তো মনে আছে , দুই পাশ্বে চারজন লোক বসার উপোযোগী একটু উচুকরে বাঁধানো পাকা করা ওয়ালও ছিল । মমিন সাহেবেরা দুই ভাই ঐ দোকানে বসতেন , উনাদের ব্যবহার অনেক ভাল ছিলো এবং সব ভাল ভাল জিনিষ পাওয়া যেতো তাদের দোকানে , উনারা নোয়াখালীর লোক ছিলেন এবং কুলাউড়ায় এসে ব্যবসা শুরু করেন এবং ঐখানে অনেক দিন ভাল ব্যবসা করেছেন , হারিস নামে তাদের দোকানের একজন সহযোগী ছিল যিনি পরবর্তীতে দুইটা দোকান পরে আরেকটি দোকান শুরু করেছিলেন । যুদ্ধের সময় একমাত্র উনাদের দোকানই সবসময় খোলা পাওয়া যেতো এবং তারা সকলকেই ততকালীন সেই কঠিন সময়ে কুলাউড়াবাসীদের অনেক সহযোগীতা করেছেন । এই রাস্তাই ঐ দিকে অর্থাৎ মনুর , মইন্তাম , আমতৈল , কাদিপুর , ব্রাহ্মনবাজার ,কিয়াতলা , পেকুর বাজার , হাসিমপুর ,বরমচাল , ভাটেরা ইত্যাদি জায়গায় যাবার জন্য অন্যতম রাস্তা ছিল , তাও ইঁটের হেরিংবুন দেওয়া রাস্তা মাগুরার পর্যন্ত ছিল এর পরে তা সম্পুর্নই মাটির রাস্তাই ছিল ।মমিনের দোকানের পুবপাস্বে মক্তোদিন নানার রাইস মিল ও রেশনের দোকানের পাশ দিয়ে একটি চিপা গলি রেল ষ্টেশনের দিকে গিয়েছে , ঐ রাস্তায় ও রেলের খালের উপর একটি কালভার্ট ছিল , সেই ইঁটের রাস্তা যোগে রেলওয়ে হাসপাতালের পাশদিয়ে সহজে ষ্টেশনে গিয়ে পৌছানো যেত ।
মমিনের দোকানের পরেই কয়েকটি দোকান ছিল তারপর ছিল কালীবাড়ী পাশ্বেই ছিল একটি টিউবঅয়েল যা থেকে স্বচ্ছ খাবার পানি বের হতো এবং আঁশে পাশের বেশ কয়েকটি বাড়ী দোকানপাট ও হোটেল সমুহে এই টিউবঅয়েল এর পানি নিয়ে পানির চাহিদা পুরণ হতো । সাপ্লাই থেকেও সারাক্ষন খাবার পানি আসতো এমনি একটি কল ছিল ইউনিয়ন অফিসের পশ্চিম পাশে কুলাউড়া থানার উত্তরে মোবারকের হোটেলের পাশ্বে ।
বিপরীতে দক্ষিন বাজার বা সকালের বাজার ছিল , বিকাল বেলা বাজার বসতো উত্তর বাজারে । দক্ষিন বাজারের গলির মুখে লাগোয়া একটি ছোট্ট মিষ্টির দোকান ছিল , যেখানে গরম গরম পরটা সুজীর হালুয়া বা তুষা শিরনী ও রং বেরং এর বুন্দিয়া বা বুরিন্দা পাওয়া যেতো ।
মাঝে মাঝে জিলাপী ও সমুচা ও বিক্রি হতো । সেই দোকানের সামনেই ছিল লাকড়ীর চুলা । সবসময় একটা ধুয়া ধুয়া পরিবেশ লক্ষ্যনীয় ছিল ।
বি এইচ স্কুলের সাথীদের মধ্যে , বুলন , নান্টু , মতিন এরা উত্তর বাজারের দিক থেকে আসতো আর আমাদের পাশ্বের বাড়ীর ফখরু ( মোকাবি্বর হোসেন ) সাফী , ও লষ্করপুরের মামুনের কথা বেশ মনে আছে । মনে আছে কনা স্যারের কথা , মুনিম স্যারের কথা , শহীদ স্যারের কথা , শহীদ স্যার একটু গাট্টাগুট্টা টাইপের ছিলেন , হাটতেন বেত হাতে নিয়ে । তিনি রেলওয়ে স্কুল থেকে বদলী হয়ে বি এইচ স্কুল বা পাঠশালায় এসেছিলেন ।
আরো মনে আছে বড় দা র কথা এবং আমিরুননবী সারের কথা , তিনি অনেক ফিটফাট থাকতেন এবং আরবী পড়াতেন ।
স্কুল থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে মিষ্টির দোকান থেকে জিলাপী কিনতাম তাও আবার বাকিতে , মামা পরে পয়সা দিয়ে দিবেন এই রকম প্রতিশ্রুতিতে বাকি পাওয়া যেতো আর তখন সব দোকানীরাই কুলাউড়ার সকলকেই চিনতো । একটি বেকারীর বিস্কিট ই ছিল ভাল কিছু খাবার । যা কিনে বাড়িতে এনে খেতে হতো , তাও মচা বা ঠোংগায় ভরে , তখন তো আর পলিথিনের ব্যাগ ছিল না , খাকী কাগজের ঠোংগাই ছিল অন্যতম ভরসা ।
শৈশবের সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে টাকার অভাবে অনেক স্বপ্ন পুরন করা হয়নি , ইতিমধ্যে অনেক স্বপ্নই মরে গেছে, আজ টাকা আছে বটে কিন্তু সেই স্বপ্নও নেই এবং তা পূরণের ইচ্ছেটা আর নেই ।
ফেলে আসা সেই শৈশবের সময় যেন বিকেলের স্মৃতি, এখন সময় চলে একমুখী হয়ে এক দেয়ালের ভেতরে সারাক্ষন মোবাইল টিপে মাঝে মাঝে খোলা আকাশের দিকে তাকালে মন ছুটে যায় বৃষ্টি ভেজা সেই দিনে যেদিন টাকার অভাবে ফুটবল কিনতে পারি নাই আমরা অনেকেই , মাঠে খেলায় নাম লেখাতে পারি নাই বুট কেনা ছিল না বলে , আমাদের অনেক স্মৃতি , বৃষ্টিতে ভিজে জাম্বুরা কে ফুটবল বানিয়ে কামাল ভাই , মলাই ভাই , রহমান ( লন্ডন প্রবাসী ) , রুমেল , সুলতান দের সাথে নিয়ে কাদায় ফুটবল খেলতাম বাড়ীর পিছনের বন্দে । আহারে কি সেই মধুর স্মৃতি
খুব ইচ্ছে হয় শৈশবের সেই বেলায় ফিরে যেতে। ইচ্ছে হয় সেই সব সাথী বন্ধুদের ডেকে বলি , চলনা আবার হারিয়ে যাই স্মৃতিগুলো কুড়িয়ে সঙ্গে করে সেই শৈশবে।
আসলে শৈশবকাল হল মানুষের এমন একটি সময় যেখানে থেকে যায় শুধু স্মৃতি এবং সেই সময়েই একটি শিশু চায় তার জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে যাওয়ার সঠিক পথ বেছে নিতে। আমার মনে নেই তখন কেউ কি আমাদেরকে বলেছিল কিনা যে তোমরা এই পথ বেছে নাও .. এভাবে চল .
শুধু সবাই বলতো ভাল করে পড়ালেখা কর , বড় হও , বড় হলে ডাক্তার ইন্জিনিয়র হতে পারবে , মানুষের মত মানুষ হতে পারবে ।
কুলাউড়ার সেই ময়মুরব্বী , বড়দের কথা , উপদেশ আজও কানে বাজে , তাদের অধিকাংশরাই আজ বেচে নেই , তাদের আত্বার শান্তি ও জান্নাত কামনা করছি । আমিন ।( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি পর্ব – ৩৯ ( কুলাউড়া-৫)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কুলাউড়া শুধু বর্তমান সময়ের একটি মোটর সাইকেল বা অটোরিক্সার উঁচ্চ শব্দের শহর নয় , এদেশের একটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর , সীমান্তঘেষা সম্ভাবনাময় উন্নত , শিক্ষিত উপজেলা , যেখানে রয়েছে বহু উজ্জল নক্ষত্রের জন্মভুমি , পীর ফকির অলী আওলীয়াদের পুন্যস্থান ,হাওরে পাহাড়ে ঘেরা সবুজে বর্নীল শ্যামল ভুমির ও চা বাগানের সমাহার , বিশাল জনগোষ্ঠির সমন্নয়ে সংগঠিত , ভাতৃত্ব ও সম্পৃতির বন্ধনে আবদ্ধ ,জাতি ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সমুউন্নত বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য প্রিয় এই শহর ছোট্ট যা আমাদের গর্বের স্থান ,
“কুলাউড়া “ যার নামকরণের ইতিহাস জানতে ইচ্ছে জেগেছিল , বেশ কিছু তথ্য ও জনশ্রুতি পাই, ইতিহাস গবেষক হোসেনপুরের বাবু হীরেন্দ্র চন্দ্র দাসের লেখা ১৩৩৭ বাংলায় প্রকাশিত “ কুলাউড়ার জয়পাশার খন্দেগার পরিবার “ বইটি থেকে জানা যায় ,মনসুর গ্রামের প্রখ্যাত “দেওয়ান মামন্দ মনসুরের পিতামহ বা দাদা দেওয়ান মামন্দ মনোয়ারের ভাই মামন্দ কুলওয়ার বালক থাকাকালেই কুমার অবস্তায় মারা যান । তার স্মৃতি রক্ষার্থে তার ভাই জমিদার ‘মান মনোহর ‘তার জমিদারির পুর্ব অংশে একটি বাজার তৈরী করেন । সেই কুলা ওরের বাজার ই কালক্রমে “ কুলাউড়া “ রুপান্তরিত হয়েছে ।
এই এলাকার অধিকন্ত ইতিহাস জানার জন্যেও একটু আগে গিয়ে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করা যেতে পারে।
ব্রিটিশরা এই অঞ্চলটিকে প্রায় দুইশ বছর শাসন-শোষণ করেছে। তাদের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গিয়েছে। ১৯৪০ সালে ‘লাহোর প্রস্তাব’-এ ঠিক করা হয়েছিল ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমান বেশি, সেরকম দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে আর একটি দেশ তৈরি করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে এলাকা দুটিতে মুসলমানরা বেশি সেই এলাকা দুটি নিয়ে দুটি ভিন্ন দেশ না হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চলটিকে ভারত নামে অন্য একটি দেশে ভাগ করে দেয়া হলো। পাকিস্তান নামে পৃথিবীতে তখন অত্যন্ত বিচিত্র একটি দেশের জন্ম হলো, যে দেশের দুটি অংশ দুই জায়গায়। এখন যেটি পাকিস্তান সেটির নাম পশ্চিম পাকিস্তান এবং এখন যেটি বাংলাদেশ তার নাম পূর্ব পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব এবং সেখানে রয়েছে ভিন্ন একটি দেশ- ভারত।
আরো উল্লেখ্য
“ মানুষের যতগুলো অনুভুতি আছে তার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর অনুভুতি হচ্ছে ভালোবাসা। আর এই পৃথিবীতে যা কিছুকে ভালোবাসা সম্ভব তার মাঝে সবচেয়ে তীব্র ভালোবাসাটুকু হতে পারে শুধুমাত্র মাতৃভূমির জন্যে। যারা আজ কুলাউড়ায় বেচে নেই তাদের আত্বার শান্তি কামনা করছি যারা বর্তমানে বিদেশে কখনো নিজের মাতৃভূমির জন্যে ভালোবাসাটুকু অনুভব করেনি তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আমাদের খুব সৌভাগ্য আমাদের মাতৃভূমির জন্যে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল তার ইতিহাস হচ্ছে গভীর আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল এক অর্জনের ইতিহাস। যখন কেউ এই আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাস জানবে, তখন সে যে শুধুমাত্র দেশের জন্যে একটি গভীর ভালোবাসা আর মমতা অনুভব করবে তা নয়, এই দেশ, এই মানুষের কথা ভেবে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে।
আমাদের দুঃখী এই দেশটি আমাদের বড় ভালোবাসার দেশ, বড় মমতার দেশ।
যাঁরা জীবন বাজি রেখে এই স্বাধীন দেশটি আমাদেরকে এনে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞাতার শেষ নেই।
৭১ এর সেই ভয়াবহ সময়ে যারা কিংবদন্তী হয়ে আছেন তাদের অন্যতম কয়েক জন হলেন ,রাজা সাহেব , জুবেদ চৌধুরী , জব্বার মিয়া , জয়নাল আবেদিন , আব্দুল লতিফ , গিয়াস উদ্দিন , সৈয়দ জামাল উদ্দিন প্রমুখ । আজকে যারা কুলাউড়ার নেতা , পিতা এরা বা এদের মাতা পিতা এক সময় কুলাউড়া থেকে দুরে
ভিভিন্ন গাঁও /পুর থেকে , পায়ে পেক মাথায় লুংগী হাতে জুতা নিয়ে কুলাউড়ায় এসে বিভিন্ন পুকুরে হাত পা ধুয়ে মজলীসে বসতে দেখা যেতো ।
আর তখন যেসব স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধাপরাধী এই স্বাধীন রাষ্ট্রটিকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে তাদের জন্যে রয়েছে অত্নহীন ঘৃণা। আজ থেকে একশ বছর কিংবা হাজার বছর পরেও যতদিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে, এই দেশের মানুষ স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করবে না।
আমরা চাই বর্তমান প্রজন্ম ঐ সকল জঘন্য ঘৃনিত ব্যাক্তিদের নিন্দা জানাক কিন্তু এই নিন্দা জানাতে গিয়ে তাদের পরবর্তী নিরঅপরাধ উত্তরসুরীদের অবজ্ঞা বা অবহেলা করাটা বোধ হয় সঠিক হবে না ।
আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের নতুন প্রজন্ম মাতৃভূমিতে ঘুরে ঘুরে অভিমানী মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে তাদের হাত স্পর্শ করে বলবে, আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দেয়ার জন্যে তোমরা যে সংগ্রাম করেছো যে ভালোবাসা দেখিয়েছে তাতে আমরা গর্বিত এবং তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বলবে, আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি, তোমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলে আমরা সেই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব।
তোমাদের রক্তের ঋণ আমরা শোধ করব।
এই কুলাউড়ার এক কৃতি সন্তান যিনি সামরিক বাহিনীর অবসবপ্রাপত মেজর নুরুল মান্নান চৌধুরী ( তারাজ ) এমনি একটি মহৎ কাজ করে যাচ্ছেন , গবেষনা করছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি যখনই সময় পান , ছুটে যান তার কুলাউড়ার প্রত্যন্ত্য অন্চলে , খুঁজে ফিরেন জীবিত বা মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের , ভাল মন্দ খোঁজ খবর নেন তাদের পরিবারের , শ্রদ্ধা জানাই তার এই উদ্দোগকে ।
আমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা দরকার আমাদের চারপাশে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া স্বাধীনতার সপক্ষের বীরদের সামনে মোটর সাইকেলের উচ্চশব্দের হর্ন বাজিয়ে বীরত্ব দেখানো আর আগাছা পরগাছার মত হটাৎ গজিয়ে উঠা হাইব্রীড নেতাদের সাথে সেলফী তুলে নিজেকে ভাইরাল হওয়ার সংস্কৃতি পরিহার করে নিজের এবং পরিবারের অতীত ইতিহাস ঐতিয্যকে ভুলে বিবেক বর্জিত কার্যকলাপে জড়িত থাকার মাঝে কোন বাহাদুরী নেই , তাই আমি বিশ্বাস করি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুগঠিত হবে , কতিপয় অসাধু উসৃংখল উঠতি তরুণদের সামাজিক শালীনতায় সুশৃংখল পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবে ।( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি — (৬)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার দের বর্বর আক্রমন , ক্রমেই তা ছড়িয়ে পরে সারাদেশে , তারই ধারাবাহিকতায় মৌলভীবাজার মহকুমা শহর থেকে ১৯ মাইল দুরে সিলেট জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য থানা ‘কুলাউড়া’য় হানাদার বাহিনীরা আসে ৪১ দিন পরে ৬ই মে সোমবার রাতে , এই ৪১,দিন কুলাউড়া ছিল শত্রু মুক্ত ,
এসেই ওরা অবস্তান নেয় ও ক্যাম্প তৈরী করে কুলাউড়া হাসপাতালে , গার্লস স্কুলে , নবীন চন্দ্র স্কুলে এবং পৃথ্বিমপাশা নবাব বাড়ির একাংশে ।
কুলাউড়া আসার পথে পাকিস্তানী সৈন্যদের বহনকারী বহর ব্রাম্মনবাজার পৌছালে সেখানকার ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ কে এম ইউসুফ আলী কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী ও একদল সাধারন লোকজন নিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ , পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে দিতে পাকিস্তানী পতাকা হাতে নিয়ে ঐ বহরের সাথে যোগ দেন ও কিছু সংখ্যক সিপাহীর সমন্ন্বয়ে বাজারের হিন্দু মালিকানাধিন দোকান গুলি ভাংচুর ও লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করে ।তার কিছু সময় পরেই সেই সৈন্যবহর কুলাউড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে ।
ইতিমধ্যে কুলাউড়ায় পৌছে যায় পাকিস্তানী মিলিটারীদের কুলাউড়া আগমনের সংবাদ ।
প্রসংগত উল্লেখ্য কুলাউড়ার কয়েকজন সাহসী বীর সন্তানের অবদানের কথা আত্বত্যাগের কথা উল্লেখ না করে পারছি না যাদেরকে সব সময় স্যালুট জানাই।যারা বীরত্বের সাথে তৈরি করেছিলেন প্রতিরোধ বাহিনী
নেতৃত্বে ছিলেন বেশ কয়েক জন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন , জুবেদ চৌধুরী ,জয়নাল আবেদিন,ব্যরিষটার আব্দুল মোন্তাকিম চৌধুরী , আব্দুল জব্বার ,আব্দুল লতিফ খান ,নওয়াব আলী সরওয়ার খান চুন্নু ,নওয়াব আলী সফদর খান রাজা সাহেব ,মছাদুর রহমান , আব্দুল মতিন ,তজম্মুল আলি ,সৈয়দ জামাল উদ্দিন ,আজির উদ্দিন আহম্মেদ , মুকিম উদ্দিন আহম্মেদ , অমিয়াংসু সেন ,লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল , মতি উদ্দিন আহম্মেদ, আসকির মিয়া সহ আরো অনেকেই ।
মৌলভীবাজার থেকে পাক বাহিনী কুলাউড়া আসছে শুনে সেদিন প্রতিরোধ বাহিনীর পুর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্দেশমতে, কামারকান্দি গ্রামের মুজাহিদ সদস্য আসকীর আলী , রামপাশা গ্রামের হাবিবউল্লাহ যিনি জীপ চালাচ্ছিলেন এবং রহিম খান ,চাতলগাও এলাকার কাফুয়ার পুলের সামনে এরাই প্রথম মুখামুখি হন এবং পাক বাহিনীর কুলাউড়া প্রবেশে বাঁধা দেন , আছকীর মিয়া যিনি অস্রচালনাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন প্রচন্ড সাহসীকতার পরিচয় দেন , ঐ মুহুর্তে ,শুরু হয় গোলাগুলি ,
তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের অফিস থেকে এসে যোগ দেন আব্দুল জব্বার , মছাদুর রহমান মুকিমউদ্দিন আহম্মেদ,
ঐ সম্মুখযুদ্ধে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে আসকীর মিয়া ও
হাবিব উল্লাহর জীপ উল্টে যায় । ঘটনা স্থলেই শহীদ হন হাবিব উল্লাহ ,আসকীর মিয়া গুলিবিদ্ধ অবস্তায় গাজিপুরের দিকে যাওয়ার পথে শাহাদত বরণ করেন । মুক্তি যুদ্ধে কুলাউড়ার এই দুই জনই প্রথম শহীদ হোন ।রহিম মিয়া ও অন্যান্যরা কোন রকমে পাশ্ববর্তী গ্রামে দৌড়ে পালিয়ে বেঁচে যান ।
প্রতিরোধকারীদের হত্যার পর মিলিটারীরা পাশ্ববর্তী চাতল গাঁও গ্রামে ঢুকে অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার আশায় ঐ গ্রামের অনেকেই পাকিস্তানী পতাকা হাতে নিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ , পাকিস্তান জিন্দাবাদ, স্লোগান দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন , কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি ।সবাই কে ধরে এনে ,এক সারীতে দাঁড় করিয়ে এর মধ্যথেকে পাঁচজনকে মসজিদের সামনে এনে হত্যা করে মিলিটারীরা ,হতভাগ্য এই পাঁচ জন ছিলেন চাতলগাঁওয়ের কটু মিয়া ,ও আব্দুল কুদ্দুস ,টেংরা এলাকার দুজন ও হিংগাজিয়া এলাকার একজন ।
পাকিস্তানী আর্মিরা তান্ডব শেষে কুলাউড়ার দিকে এগুলে পরে আস্তে আস্তে বেড়িয়ে এসে গ্রামবাসী চারজন শহীদদের লাশ পাশবর্তী একটি গোরস্তানে নিয়ে সমাহিত করেন।হিঙ্গাজিয়া এলাকার অপর শহীদের লাশ গ্রামবাসী গ্রামে এসে নিয়ে তাদের গ্রামে কবর দেন।
ইতোমধ্যে পাক বাহিনী কুলাউড়াতে প্রবেশ করে ।সেখানে পলায়নপর অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে ছাত্রলীগ নেতা নূরুল ইসলাম ভুইয়া ও অপর একজন ছাত্রলীগ কর্মীকে , কুলাউড়া সিলেট রেলপথের সিগন্যাল পোস্টের কাছে এই দুই সম্ভাবনা ময় তরুনকে কবরস্ত করা হয়েছিল , যে কবরটির চিন্হ আজ বিলীন হয়ে গেছে ।
আওয়ামী লীগ করতেন হোটেল ব্যবসায়ী মোবারক আলী , পাকিস্তানীরা তাকে খুঁজে না পেয়ে তার ম্যানেজার আব্দুর রহমানকে ধরে নিয়ে হাসপাতালের সামনে গুলি করে হত্যা করে ।একই সাথে হত্যা করে ছলিম উল্লাহ কে ঐ দিনই কয়েকজন অতি উৎসাহী মীরজাফরের সহায়তায় বাড়ি থেকে ধরে আনে কুলাউড়ার পশ্চিমদিকের হোসেনপুর গ্রামের নানু মিয়া ও ধীরেন্দ্র শীলকে ,হস্তান্তর করে জল্লাদদের কাছে , পরিণামে তাদেরও মৃত্যু হয় ।এ ভাবেই হত্যার খেলা চলতে থাকে কুলাউড়া মুক্ত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত ।
কুলাউড়ায় গঠিত হয়েছিল তথাকথিত শান্তি কমিটি ,কমিটির অন্যতম সদস্যের মধ্যে ছিল মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী ,এ,কে,এম ইউসুফ ,বাতিন মিয়া , বদরুদ্দিন আহম্মেদ বদই মিয়া ,চেরাগ আলী ,আব্দুল বারী , ইউসুফ মিয়া ,মমরোজ মিয়া ,দরজ মিয়া , আলী ইয়াত্তর খান ,ছালেকুর রহমান , রিয়াজুল্লাহ মাস্টার , আফ্তাব উদ্দিন চৌধুরী সহ বহু পাকিস্তান পন্থিরা এই কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন
দেশ স্বাধীনের পর আমার মনে আছে কুলাউড়া রেল ষ্টেশন থেকে কোন ট্রেন লংলা হয়ে আখাউড়ার দিকে গেলে শেষ সিগন্যালটি অর্থাৎ নবীনচন্দ্র স্কুল থেকে গাজিপুর গামী রাস্তার পয়েন্ট এর পুর্ব পাশ্বে চিড়ল নামক অতিক্রমের সময় যাত্রীরা জানালা দিয়ে দেখাতো , ঐ যে ,ঐ জায়গায় পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের গুলি করে মারতো , সারা ট্রেনের যাত্রীরা তখন খুউব আক্ষেপ করতো ,, ঠিক তেমনি বিপরীত দিকে কুলাউড়ার উত্তর দিকের শেষ সিগন্যাল পয়েন্টেও , যে রেলপথটি বরমচাল হয়ে সিলেট গিয়েছে ,সড়ক পথটি জুড়ি বড়লেখার দিকে গিয়েছে ঐ পয়েন্টে অনেক কেই গুলি করে মেরেছে এবং এদের অনেকের ই অন্যান্য আপনজনদেরকেও ধরে এনে হত্যা করা হয়েছিল যাদের লাশ তাদের স্বজনদের কাছে পৌছায়নি ,এখন আর কেউ ঐ সিগনাল পয়েন্ট অতিক্রম কালে ৭১ এর বধ্য ভুমির কথা বলে না।( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি -পর্ব – ৩৬ (দক্ষিন বাজার )
সৈয়দ শাকিল আহাদ
৭১ সালের অনেক কথাই এখন অনেকের মনে নেই , তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের কথা এবং তার পরবর্তী সময়ের বেশ কিছু স্মৃতি , উল্লেখযোগ্য ঘটনা , স্থান, স্থাপনা , ব্যক্তির কথা ইত্যাদি স্বরণ করে মনে কিছুটা স্বস্তি পাই বলেই ততকালীন সময়ের কথা বার বার বলতে চেষ্টা করছি ।
কোন রকম ভুলত্রুটি হলে অবশ্যই তা ক্ষমার চোখে দেখার জন্য অনুরোধ রইল ।সেই সময়ের অনেক কথা কিছুটা সম সাময়িক এবং অনেক সিনিয়রদের সাথে কথা বলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমুহের সত্যতা যাচাই করে কিছু কিছু সময়ে তাদের মতামত সহ , তা তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছি , এবং সত্বিই ৭০ এর দশকের শুরুর দিকের কথা লিখে অনেক পুলকিত হই তাই কিছু কথা না বললেই নয় ,তখন কুলাউড়ায় ছিলাম তাই কুলাউড়ার কথাই বলছি ..
কুলাউড়া জামে মসজিদের বিপরীতেই ছিল আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী , যিনি একাধারে ১০ বছর কুলাউড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন উনার আরেক ভাই ছিল গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ বা জননেতা গিয়াস ভাই ৭১ এর ৭ ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ভাষনের পর ৮ ই মার্চ ঢাকা থেকে কাগজের তৈরী এই স্বাধীন বাংলার পতাকা কুলাউড়ায় নিয়ে আসেন এবং ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে কুলাউড়ার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘরে , বাড়িতে সৈয়দ জামালউদ্দিন , গিয়াসউদ্দিন সহ আরো কয়েক জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা উত্তোলিত হয় ।ছাত্রলীগ নেতা গিয়াস ভাই পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর জাসদের রাজনীতিতে সক্রিয় হন । কুলাউড়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে গিয়াস উদ্দিনের কথা তার পরিবারের কথা না লিখে তা পরিপুর্নতা পাওয়া সম্ভব নয় ।
কুলাউড়ার সকলেই বাচ্চু মিয়ার বাড়ী বললেই সকলেই এই বাড়িটিকে চিনতো . বাড়ীর সামনে দুইটি দোকানের কথা হয়তো এখনও অনেকের মনে আছে “ আহমেদ ক্লথ ষ্টোর এবং রিয়াজ ক্লথ ষ্টোর , তবে আমরা বাচুচু মিয়ার বাড়ী বা বাবুল কামরুলদের বাড়ী হিসাবেই চিনতাম ।বাচ্চু মিয়ার ছেলে কামরুল বা ইফতেখারই আমার সাথে বি এইচ স্কুলে পড়তো , খুউব মিস্টি হাসির একটি হেংলা পাতলা ছেলে ছিল । সেই সুবাদে ঐ বাড়ীর ভীতরে যাওয়া আসার সুযোগ হয়েছিল , একে বারেই
ভোলার মত নয় তাদের বাড়ীর সুন্দর পরিবেশ, ভেতরটা ছিল খুবই চমৎকার , ভীতরে একটি পুকুর ও ছিল , খালাম্মা খুউব আদর করতেন ,খালাম্মার নাম ছিল আংগুরী খালা , তিনি সবসময় ঘোমটা দিয়ে থাকতেন ,উনার এক বোন ছিল যার নাম মনে আছে , তিনি হলেন “খেজুর খালা “বরমচালে থাকতেন । ইফতেখারদের এক বোন ছিল , সম্ভবত উনার নাম চামেলী , খালাম্মাদের বাড়ী ছিল বরমচাল এলাকায় । আর ইফতেখার দের চাচাতো চাচা ছিলেন হাজী জহির আলী এবং ইরফান আলী মামা ,উনারা মোটর গাড়ীর ব্যবসা করতেন তখন উনাদেরই বাস চলতো কুলাউড়া মৌলভীবাজার রুটে ,উনারা দক্ষিন বাজার মাগুরাতে বাসা তৈরী করে থাকতেন মুল বাড়ী ছিল সম্ভবত ভুকশীমইল। উনাদেরকে ও মামা ডাকতাম , তবে ইরফান আলী মামাকে দেখি নাই , তিনি চাতলগাও এলাকায় বাড়ী করেছিলেন এবং তার চেহারাও মনে নাই উনার ছেলেদের কথা মনে আছে , ফজলু ভাই , ফয়সল ভাই , মুনসী, ও রুমেল ।জহির আলী মামা একটু মোটা ছিলেন , প্রচুর পান খেতেন এবং মোটরষ্ট্যান্ড এ উনার গাড়ী ( বাস ) থাকতো , মোটর স্স্ট্যান্ড এ বেশ কয়েকটি দোকানের মধ্যে আলালপুরের হাফিজ সাহেবের ছোট ছেলের একটি চায়ের দোকান / হোটেল ছিল এবং মসজিদের পাশে কনা মিয়ার একটি রেষ্টুরেন্ট ছিল যাকে সবাই নাজমা হোটেল বলে চিনতো মোমিন মিয়ার ভুষি মেইলের দোকান , মক্তদির নানার রেশনের দোকান ইতাদি ,
জহির আলী মামার একটি পার্টস এর দোকান ছিল ,উনার বড়ছেলে মতলিব ভাই সেটি চালাতেন উনাকে পীর সাহেব বলে জানতো কুলাউড়ার জনগন , দীর্ঘদিন কুলাউড়া জামে মসজিদের কোষাধক্ষ ছিলেন তিনি ,মতলিব ভাইয়ের ছেলের নাম ছিল লিটন , সে এখন যুক্তরাজ্যে। জহির আলী মামার অপর ছেলেরা হলেন মাক্কু ভাই ও মহিব ভাই , মাসুম ।
মাক্কু ভাই এলাকার কাউন্সিলর হিসাবে অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন , তিনি ও একজন দারুন ক্রীড়া অনুরাগী ছিলেন ।জায়েদা আপা নামে জহির আলি মামার এক মেয়ের সাথে এখনও যোগাযোগ আছে , তিনি আমার বড় বোন এডভোকেট সৈয়দা ফেরদৌস আরা লাকীর বান্ধবীদের অন্যতম একজন । এই পরিবারের ভাইদের মধ্যে কে যে কোন মামার ছেলে ? তা নিয়ে প্রায়ই আমার গন্ডোগোল হয়ে যেতো , হয়তো এখনও লেগেছে ।
আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেব এর পাশের বাসার আর এক বোনের কথা মনে আছে তিনি হলেন আলেয়া আপা বা আইলা আপা , বহুবছর পর ফেস বুকের কল্যানে এবং এই গ্রুপে লেখালেখীর সুবাদে উনার সাথে যোগাযোগ হয়েছে । তবে অদ্যাবধী উনার সাথে দেখা হয়নি , বর্তমানে ঐ “ আলেয়া আপা বা আইলা আপা “ ব্রাম্ব্রনবাড়ীয়াতে আছেন , শীঘ্রই তার সাথে দেখা করবো সংকল্প করেছি । আইলা আপার আব্বা পুলিশের কর্মকর্তা ছিলেন ,আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর পুর্বদিকে রেলওয়ে কোলোনীতে থাকতো আরো দুইটি বোন , তাদের এর কথা ও মনে পড়ছে উনারা হলো নাদিরা আপা ও সেতারা আপা , নাদিরা আপার ভাইদের কথাও মনে আছে একজন হলেন মকবুল ভাই ওঅন্যজন হলেন হাবিব ভাই , উনাদের আব্বা “ আবুল ফজল “ টি টি ই “ অনেক ফর্সা সুন্দর ও একজন ভাল লোক ছিলেন , উনাদের কোয়ার্টারের পাশেই ছিলেন , আসাদুল হক ( গার্ড) নানার বাসা , তিনি ও রেলে চাকরী করতেন , ট্রেনের পরিচালক ( গার্ড) ছিলেন । পরবর্তীতে আমাদের বাড়ীর পাশে রহমান দের কাছ থেকে জমি কিনে বাড়ী তৈরী করে স্থিত হন । তার ছেলে মেয়েদের কথাও মনে আছে , এরা হলো লাবলু , লিটু , জলি , ডলি , লুসি ও হ্যাপি । এরা সকলেই এখন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বাসিন্দা ।
কুলাউড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন রামগোপাল ফার্মেসীর কথা বার বার মনে হয় । কারন এই ফার্মেসীতে ডুকেই দুই দিকে দুইটি হাতাওয়ালা কাঠের বেন্চ ছিল । এই ফার্মেসীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অত্যন্ত্য বিনয়ী একজন মানবতাপরায়ন ব্যক্তি , নাম তার শ্রী রসেন্দ্র কুমার ভ্ট্টাচার্য্য , এই ফার্মেসীর মাধ্যমে এই এলাকার অর্থাৎ সমগ্র কুলাউড়া , জুড়ি , ব্রাম্বনবাজার , টেংরা , রবির বাজার , শমশেরনগর ,লংলা , টিলাগাঁও , ভাটেরা, বরমচাল ইত্যাদি এলাকার এবং সকল চা বাগান সমুহের ঔষধ এই রাম গোপাল ফার্মেসী থেকেই যেতো , রামগোপাল ফার্মেসী ফেনীর জেনিথ ল্যাবরেটরী থেকে ঔষধ আনতো ॥
কুলাউড়া মসজিদের কিছুটা পিছনে পশ্চিমে ছিল রসেন্দ্র ভটের বিশাল বাড়ি যাকে সবাই ভটের বাড়ী বলেই জানতো ।
তার এক ছেলে ছিল চুনু ভট , তিনি চিকিৎসা শাস্ব্রে নিয়োজিত ছিলেন , অত্যন্ত্য দক্ষতার সাথে রোগীদের রোগের বর্ননা শুনে ফার্মেসীর ভীতরে পর্দা সরিয়ে কাঁচের শিশিতে মিকচার তৈরী করে দিতেন । মিকচারের শিশিতে দাগ কাটা থাকতো , সেই দাগ কাটার ঔষধের দুই তিন দাগ খাওয়ার পর রোগ ভাল হয়ে যেতো , আঁশে পাশের দশ গ্রামে এই মিকচারের খ্যাতি ছিল প্রচুর ।রসেন্দ্র ভটের তিন ছেলে ও সাত মেয়ে ছিল । বড় ছেলে ইন্ডিয়াতে থাকতেন , দ্বিতীয় ছেলে ছিলেন ঐ চুনু ভট আর ছোট ছেলের নাম ছিল ভানু ভট্টাচার্য , ভানু ভট একটু লাজুক প্রকৃতির ছিলেন ।
ঐ বাড়ীর এক দিদির নাম ছিল পম্মাদি , উনাদের আম্মা অর্থাৎ পম্পাদির আম্মা বা কাকিমা খুউব সুন্দরী ছিলেন সম্ভবত উনিই সজল দার আম্মা , উনিই পুরো সংসার চালাতেন , উনাদের বাড়ীতে অনেক কামলা ( কাজের লোক ) থাকতো ।আলাদা অনেক গুলো ঘর ছিল , বাড়ীতে গোলাপ ফুলের গাছ , পাতা বাহার , জবা মেহেদী ইত্যাদির গাছ ছিল । একজন ঠাকুমা ও ছিলেন তবে তিনি কখনই বারান্দা বা উঠানে বের হতেন না ।
ছোট বেলায় বহুবার শুনেছি রসেন্দ্র ভট তার সাত মেয়ের সাথে একজন পালক মেয়েকে ও বাডিতে রেখেছিলেন । বিভিন্ন এলাকার অনেক পীসি মাসি ও বিধবা এই ভটের বাড়ীতে থাকতেন, রসেন্দ্র ভট তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্তা করতেন ।এবং পুরো পরিবারের সকল চাপ সামাল দিতেন কাকিমা অর্থাৎ পম্পাদীর আম্মা ।তা ছাড়াও অনেক বিপদ গ্রস্ত লোকের আস্রয়স্থল ছিল ঐ ভটের বাড়ী ।
উনার অনেক মানবিক গুনাবলীর মাঝে একটি গল্প আমি বহুবার বহু লোকের মুখে শুনেছি যা উল্লেখ না করে পারছি না । কুলাউড়াতে এস এস সি পরীক্ষা উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন বাড়িতে মেস করে থেকে পরীক্ষা দিতো । এবং তা পরীক্ষার কিছুদিন আগে থেকেই এসে থাকা শুরু করতো । এক মেট্রেকুলেশন বা এস এস সি পরীক্ষার্থী মেয়ে টাইফয়েডের কারনে হটাৎ হটাৎ অস্বাভাবিক আচরণ করায় ফলে বিরক্ত হয়ে ,তার রুমের অন্যান্য মেয়েরা মেয়েটিকে ট্রাংক ও বিছানা পত্র সহ বের করে দেয় । এবং মেয়েটি বি এইচ স্কুলের বারান্দায় ট্রাংক সহ এসে কান্না শুরু করে ।ঐ দিন স্কুলে বড় দা সহ সকল শিক্ষকেরা মিলে মেয়েটিকে বুঝিয়ে শান্ত করে , সিদ্ধান্ত নিলেন তাড়াতাড়ি মেয়েটির অভিভাবককে গাজীপুর বা ঐদিকের কোন এক গ্রামে খবর দেবেন ।
ইতিমধ্যে ঐ ঘটনা আঁশে পাশে জানাজানি হওয়াতে রসেন্দ্র ভট্ট মেয়েটির কথা শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলতে লাগলেন “ এত বড় ঘটনা ঘটে গেলো আমি জানলাম কেনে ? আমারে কেউ কুনতা কইলো না ?
আমরা সবাই তার পিতার মত , পিতা হয়ে কি তার নিরাপত্তা দিতে পারবো না ? এই মেয়েটি এখন চলে গেলে তার শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যাবে , না আমরা তা হতে দেবো না , একে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি , আমার মেয়েদের সাথে থাকবে , তখন বড়দা ইতস্থত করছিলেন এই বলে “ কি বলেন দাদা ?
মেয়েটি তো মুসলমান !!এবং সে সম্পুর্ন সুস্ত ও নয় ।
রসেন্দ্র ভট্ট তখন বলেছিলেন । তাতে কি ? সে আর আমি আমরা সকলেই মানুষ , মানুষ বলেই কথা ,
তিনি আর কথা না বাড়িতে একটি রিক্সা ডেকে মেয়েটির ট্রাংক ও বিছানা সহ তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন । কিছুক্ষন পর মেয়েটিকে তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্তা করে দিয়ে স্কুলে এসে শিক্ষক “বড়দা “কে বলেছিলেন “ বড়দা আজ আমরা একজন পিতার দায়িত্ব পালন করেছি । তোমাকে ধন্যবাদ তুমি খবরটি তার পিতার কাছে পৌঁছায় নি “তা হলে হয়তো আমি এই দায়িত্ব নিতে পারতাম না । উল্লেখ্য মেয়েটি এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েছিল ।
এক বার রসেন্দ্র ভট্ট ফেনী থেকে ফেরার পথে একটি এতিম ছেলে ও মেয়েকে বাড়িতে এনে থাকার ব্যবস্তা করেছিলেন ।
তার মহানুভবতার কথা বলে শেষ করার মত নয় ।
আজ তিনি নেই তার সম সাময়িক বা আগে পরে অনেকেই নেই , কুলাউড়া কুলাউড়ার জায়গায় রয়ে গেছে , কুলাউড়াতে বেড়েছে অনেক অচেনা লোকের দাপট , উঁচু উঁচু বাড়ীঘর , নতুন নতুন রাস্তা ঘাট , গাড়ী , বাড়ী , দালান কোঠা , রংবেবং এর মোটর সাইকেল , হোন্ডা ও পান্ডা বাহিনী , নতুন নতুন অফিস আদালত , বেড়েছে রেস্তোরা , রিসোর্ট ,স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রসা, মন্দির , গির্জা ইত্যাদি তবে
যুদ্ধ কালীন সময়ে হাতে গোনা কয়েক টি পরিবারের কথা , কিছু স্থাপনার কথা ,অনেক জনের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কিছু ব্যক্তি বর্গের কথা
বিশেষ করে রসেন্দ্র ভট্ট ,গিয়াস উদ্দিন , মোমেন মিয়া দের সহ জব্বার মিয়া , জুবেদ চৌধুরী , জয়নাল মিয়া , মবুব মিয়া ইত্যাদি বীরদেরকে শ্রদ্ধা জানাই , তাদের বিদ্বেহী আত্বার শান্তি এবং জান্নাত কামনা করছি । আমিন । ( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি —(৭)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কুলাউড়ায় ৭১ এর মে মাসের ৭ তারিখের পর, পুরো শহরেই ছমছমে ভুতুড়ে ভাব , প্রয়োজন ছাড়া কেউ রাস্তায় বের হয় না ,হাসপাতাল , থানা , ডাকবাংলো ,রেল ষ্টেশন ,হাই স্কুল সর্বত্রই পাকিস্তানী মিলিটারীদের দখলে ,
২৬ শে মার্চের পর থেকে স্বাধীনতার স্বপক্ষে কুলাউড়ায় গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ গোষ্টির প্রতিরোধ কমিটির লোকজনও গা ঢাকা দিয়েছিল , কেউ কেউ পালিয়ে সীমানার ওপারে গিয়ে ভারতের কৈলাশহর , আগরতলা , কুকিশহর প্রভৃতি স্থানের শরনার্থী শিবিরে আস্রয় নিয়ে অন্যান্য দের সংগঠিত করে দেশকে শত্রূমুক্ত করার লক্ষ্যে অস্রচালনা ,যুদ্ধের কৌশল ,প্রশিক্ষন ইত্যাদি শুরু করেছিল ।
এদিকে তখন কুলাউড়াতে তথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্যদের ও পাকিস্তানপন্থী নেতাদের পাকশিবিরে অনেক বেশি কারণে ,অকারণে ,আনাগোনা করতে থাকাতে মারাত্বক ভাবে মুক্তিকামি জনগনের মনে ভয়ের উদ্রেক হতে লাগলো ,আবার ঐ সকল চিন্হিত পাকিস্তানপন্থী দের অতিমাত্রায় চাটুকারীতার ফলে বিশেষ করে এলাকার অধিকাংশ গন্যমান্য পরিবারের কর্তা ব্যক্তি মেধাশুন্য হয়ে পরেছিলেন ।
রাজাকারদের আর শান্তি কমিটির প্রদত্ত তথ্যমতে প্রতিদিনই
বিশেষ করে হিন্দু পরিবারের কর্তা এবং পুরুষ সদস্যদেরকে বাড়ি থেকে ধরে এনে হাসপাতাল , গার্লস স্কুল ,নবীন চন্দ্র স্কুলের ক্যাম্পের টর্চার সেলে নিয়ে নির্যাতন ও পরবর্তীতে রেল লাইনের সিগনাল পয়েন্টে নিয়ে হত্যা করতো , বিভিন্ন এলাকার লোকজনদের ধরে এনে মিথ্যা অপরাধের অজুহাতে , জয় বাংলা বলার অপরাধে ,সাজানো বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা হতো ,কাউকে কাউকে সারাদিন আটকে রেখে , পিঠমোড়া করে বেঁধে রেখে ,হাত পা ভেংগে ,কারো কারো গোপনাঙ্গের সাথে পাথর বেঁধে তারা আনন্দ পেতো এবং অমানবিক নির্যাতন করতো ।
কুলাউড়ার ক্যাম্প গুলিতে মেজর আব্দুল ওয়াহিদ মোঘল ও ক্যাপ্টেন দাউদ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন ।
আমাদের নানা বাড়ী উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ীর উত্তর পশ্চিমে কোনেই ছিল আব্দুস সত্তার মামার বাড়ী , উনাদের বাড়ীর পিছনেই ছিল চটই মামার বাড়ী , এই দুই বাড়িকে তখন মনাউল্লাহ ও কালাই মিয়ার বাড়ী বলতো , কালাই মিয়া বা আব্দুল খালেক ছিলেন ছত্তার মামুর বাবা , আর মনাউল্লাহ ছিলেন মজাইমিয়া বা চটই মামুর বাবা ,একদিন শান্তি কমিটির কয়েকজন সহ দুইজন মিলিটারী এসে ছত্তার মামুকে ধরে নিয়ে নবীনচন্দ্র হাই স্কুল ক্যাম্প সারাদিন আটকে রাখে , আমরা ও তার ছেলে রহমান বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী আমার চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের বড় ও হান্নান ভাই যিনি ১৯৯৫ সালে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা হুম হন , ঐ দুই ভাই, তাদের আমমা সহ আমার আম্মা, নানী , সকলেই সারাদিন কান্না কাটি করি , আল্লাহকে ডাকি , সারাদিন অনেক নির্যাতনের পর সন্ধায় তারা কি কারনে জানি সম্ভবত এলাকার অনেক মুরব্বীরা গিয়েছিলেন সত্তার মামাকে ছাড়িয়ে আনতে ,আল্লাহর মেহেরবানীতে তাকে ছেড়ে দেয় , তার দুইদিন পরে তার বাড়ির ছাগলটি এসে ধরে নিয়ে যায় গার্লস স্কুল ক্যাম্পের দুই সিপাহী ,এবং সেটিকে জবাই করে মহা ধুমধামে অন্যদের নিয়ে খায় ।
আমরা কয়েকজন কৌতুহলী বালক আমি , রহমান , সুলেমান মিলে কিভাবে মানুষ মারে এবং ঐ গার্লস স্কুল ক্যাম্পে কি কি হয় ? কাউকে না জানিয়ে তা দেখতে যাই , তখন ঐ স্কুলের একটি লম্বা টিনের ঘর ছিল আর ছিল বারান্দা , এখনকার মত বাইন্ডারী ঘেরা ছিল না ,সেখানে পাকিস্তানী সেপাহীরা আমাদের কে আমি , রহমান (যুক্তরাজ্য প্রবাসী )ও সুলতান মোল্লা কে , বড় বড় রুটি ও লবনের চাক্কা ছুঁড়ে মারে , আর বলে এই ছোকরা বল , “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” , “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” , আমরা ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসি ।( চলবে )
৭১ এর স্মৃতি -(১১)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
৭১ এর কত কথাই না মনে পড়ছে ?,
লিখি লিখি করে লিখতে ইচ্ছেও করছে অনেক কিছু আবার কি লিখতে গিয়ে ,কি লিখে ফেলি সেই ভয়টাও মনের মাঝে দোলা দিচ্ছে তাই তো অনুরোধ সকলের কাছে ৫০ বছরের আগের ঘটনার বর্ননায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটতে পারে যা অবশ্যই মার্জনীয় ।
তবে কে ,কিভাবে , কি ভাবলো সেটা পরে দেখা যাবে এখন কিছু একটা তো লেখা শুরু করি ?
কুলাউড়ায় আমাদের নানাবাড়ী থেকে বের হলেই রাস্তার পুর্বদিকে ছিল নবীন চন্দ্র হাই স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠ , মাঠের উত্তর পাশ্বেই ছিল স্কুল ঘরটি যেখানে পাকিস্তানী মিলিটারী রা বিভিন্ন গ্রামের নিরিহ লোক জন দের ধরে এনে সারা দিন বেধে রাখতো , এবং নির্যাতন করতো ,তারা থাকতো লমবাকৃত্তির দোচালা টিনের স্কুল ঘরটির কয়েকটি রুমে , টিনের ছাদ ওয়ালা স্কুলের ঐ পাকা দালানটির পশ্চিম অংশে ‘টি ‘আকৃতির দুটি রুমে সম্ভবত স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও অন্যন্যাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বসার রুম ছিল । এখানে দক্ষিন পশ্চিম দিকে একটি চাপ কল ছিল , যে কল থেকে আশে পাশের বাড়ীঘরের লোকজনেরা খাবার পানি সংগ্রহ করতো , এটাই কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ,এই স্কুলের সামনেই ছিল নবীন চন্দ্র হাই স্কুলের বিশাল ফুটবল খেলার মাঠ , মাঠের দুই ধারে ছিল খাই বা লম্বা জলাধার ,পুর্ব পাশ্বে ছিল। শাকিলা খালাদের বাসা , পারভীন আপাদের বাসা ( যদিও উনারা স্বাধীনতার পরপর এসেছিলেন কিন্তু ঐখানে ঐ ঘরটি ছিল , তার পুর্বেই ছিল লুবনা আপা শিপলুদের বাসা ,তাদের দক্ষিন দিকে দুটি কোয়ার্টার ছিল একটিতে পরবর্তীতে তপন ভাই,বীনা’দের বাসা ছিল।
বলছিলাম খেলার মাঠ বা ফিল্ডের কথা ,
অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে মেয়েদের স্কুলের পাশ্বে ছেলেদের খেলার মাঠ কেন ?
নবীন চন্দ্র হাই স্কুল তো অনেক দুরে দক্ষিন দিকে চৌমুহনীতে ।
কেন এটা হলো বিষয়টা জানা উচিত এবং নতুন প্রজন্মের জন্য সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার দায়িত্ত তো কাউকে না কাউকে নিতেই হবে , সেই দায়িত্ব বোধ থেকেই আমার জানামতে ঘটনাটা বলছি ..
আমার নানী মোসাঃ মনিরুন্নেছা খাতুন কুটিবিবি সহ অন্যান্য মুরব্বীদের মুখে শোনাঃ-
৫০ এর দশকের শুরুতে যখন সিলেট জেলা বোর্ড এর উদ্দোগে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমি নির্ধারণের কাজ চলছিল তখন এই উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ির সামনের খোলা জায়গায়টুকুকে কুলাউড়ার সকালের বাজার বা দক্ষিন বাজার করার ঘোষনা প্রায় চুড়ান্ত ,তখন আম্মা ছালেহা বেগম
ছিলেন বাড়ীতে , এমনি সময়ে বড় খালা রওশন আরা বাচচু ঢাকা থেকে আসলেন , তিনিও শুনলেন তাদের এত বড় ঐতিয্য বাহী খান বাহাদুর আমজদ আলীর বাড়ীর সামনে সকাল বেলা বাজার বসবে , নানা ধরনের লোকজনের আনাগোনা হবে এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না , তারা কেউই মানতেও পারছিলেন না , পরদিনই তিন বোন মিলে নানীকে নিয়ে ছুটলেন নানীর খালাতো বোন সিলেট শহরের অন্যতম প্রভাবশালী রশিদ মন্জিলের ‘বেগম সিরাজুন্নেছা রশিদের ‘কাছে । তখন তাদের খালাতো ভাই কায়সার রশিদের স্ত্রী শামসি খানম চৌধুরী ছিলেন সিলেট জেলার স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস , তিন বোন মিলে তাকে বোঝালেন, তাদের বাড়ীর সামনে একটি মেয়েদের স্কুল রয়েছে , এখানে বাজার বসলে , নানা ধরনের লোকজনের আনাগোনা হবে , পরিবেশের ও মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি সহ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে , এই স্হানে বাজারের পরিবর্তে খেলার মাঠ হওয়া টা জরুরী ঐ অন্চলের স্কুল সমুহের খেলার মাঠ নেই , তাদের বাড়ির সামনের জেলা পরিষদের জমিটুকু বাজারের বদলে খেলার মাঠ করলে কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের মেধা বিকাশ ও শরীরগঠনে সহায়তা হবে ,
শামসি খানম চৌখুরী ভীষন আদর করতেন আমার আম্মা ছালেহা বেগম ওরফে ছালুকে , ফেলতে পারেন নি আদরের ননদিনী দের অনুরোধ , এ দাবীতে আরো অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিদের কেও সিলেট পাঠিয়েছিলেন নানী ,যেহেতু মেয়েরা তেমন খেলা ধুলা করে না তবে ঐখানে ছেলেদের ফুটবল মাঠের প্রয়োজনিয়তা ছিল তখন ছেলেদের জন্য ফুটবল খেলাটা ছিল অত্যান্ত জনপ্রিয় সুতরাং এখানে একটি ফুটবল খেলার মাঠ হতে পারে , কিন্তু এটি কারা রক্ষনাবেক্ষন পরিচর্যা করবে ? সেটা ছেলেরা করবে , এবং ছেলেরা স্কুল ছুটির পর এখানে এসে ফুটবল খেলতে পারবে , এতে মেয়েদের স্কুলের পড়াশুনার কোনরুপ বাঁধাপ্রাপ্ত হবে না । সেই চিন্তা থেকেই শামসি খানম চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐ স্হানে বাজার না বসিয়ে বাজারের স্থান অন্যত্র সরিয়ে এই খানে নবীন চন্দ্র স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠের জন্য ঐ জায়গাটি বরাদ্ব দেওয়া হয় । সেই থেকে অদ্যাবধি ঐ মাঠটি এভাবেই নবীন চন্দ্র স্কুলের মাঠ হিসাবে পরিচিতি পেয়ে আসছে ।
এই গার্লস স্কুলের উত্তর দিকের আরেকটি লম্বা বিল্ডিং থেকে এক সময় কুলাউড়া কলেজ পরিচালিত হতো , কলেজ অংশটি পরবর্তীতে গাজিপুর রোডে চলে যায় এবং ঐ বিল্ডিং এ লিলি সিনেমা হল চালু হয় পাশ্বেই ছিল পুবালী সিনেমা হল ও , স্বাধীনতার পর পরই এক সময় এই অন্চলে পাশাপাশি দুইটি সিনেমা হল চালু হয়ে ছিল ।
যাই হোক ঐ স্কুলেই পরবর্তীতে ৭১ সালে মুক্তিবাহিনীরা ক্যাম্প করেছিল , মাঠে শরীরচর্চার ও যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হতো এই মাঠেই এলাকার মুক্তিকামী সাহসী যুবকদের সংগঠিত করে ক্যামপে মুক্তিযাদ্ধা রা নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্তা করেছিল , যার ফলে এই স্কুল ,এই মাঠ, কুলাউড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতিবহুল অংশ এবং স্মৃতিবহুল স্থান ।( চলবে)
৭১ এর স্মৃতি — (৩)
সৈয়দ শাকিল আহাদ
১৯৭১ সালে কুলাউড়াতে ছিলাম তাই কুলাউড়ার কথাই ঘুরে ফিরে আসছে , ছোট্ট একটি একরাস্তার শহর , একটি রেলওয়ে জংশন ,রেল ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পশ্চিমদিকে মাথায় আসলেই ডানদিকে ছিল মোবারক সাহেবের আজম বোডিং ,একটি বাস স্ট্যান্ডও ছিল , সেখান থেকে জুড়ি , ফুলতলা বড়লেখা , বাড়ইপাড়া শাহবাজপুর যাবার দুই তিনটি বাস থাকতো , ঐ দিকটা কিছুটা উন্নত উন্নত মনে হতো ,সি এন্ড বি অফিস ,সি. ও অফিস , সাব রেজিষট্রি অফিস , উত্তর বাজার মসজিদ ,রাবেয়া স্কুল , তহশিল অফিস , টেলিগ্রাফ অফিস , হাসপাতাল ,ইত্যাদি
আর বামদিকে মোড় নিলে ছিল ইউনিয়ন অফিস , ডাকবাংলো সংলগ্ন মোটর ষ্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে যেতো মৌলভীবাজার যাবার গাড়ি ,ঐ রাস্তায় ডানে থানা , আর একটু এগুলে দক্ষিন বাজার , বশিরুল হোসেন প্রাইমারী স্কুল , কালীবাড়ী, মসজিদ , পোস্ট অফিস , পশু ডাক্তার খানা , গার্লস স্কুল ,খেলার মাঠ , পেট্রোল পাম্প , ঈদগাহ ,নবীন চন্দ্র হাই স্কুল , কুলাউড়া কলেজ , ফানাই গাং ,তা ছাড়া দোকানপাট , ফার্মেসি , লাইব্রেরি হোটেল রেস্তোরা ইত্যাদি ও ছিল হাতে গোনা , রেল ষ্টেশনের পূর্বদিকেই ছিল জয়পাশা সাহেব বাড়ি , সৈয়দ শাহ কামালের মাজার ,দক্ষিনপুর্বে গাজিপুর চা বাগান ,গগনটিলা ,চৌধুরীবাজার ,নর্তন রেজওয়ান পীর সাহেবের সৈয়দ বাড়ী ,রবির বাজার ,পৃথ্থীমপাশা নবাব বাড়ি ইত্যাদি ।
আশে পাশে অনেকগুলো চা বাগান ছিল ,বাগানে চলাচল করতো জীপ ও ট্রাক্টর , সাধারনেরা চলতো রিক্সাযোগে , চা বাগান গুলো এখনও আছে , সারা কুলাউড়ায় পাকা রাস্তা ছিল অল্প , বাকি সবই ছিল ইট সোলিং ও পাথরের নুরী দিয়ে তৈরী , কাঁচা রাস্তা , এখনকার মত এত গাড়ি, সি এন জি , কিম্বা ট্রাক বাস অটোর নাম গন্ধ ও ছিল না ,
সর্বত্র কারেন্ট ই ছিল না , সুপেয় খাবার পানির ব্যবস্থা অর্থাৎ টিউবঅয়েল ও ছিল হাতে গোনা কয়েকটি জায়গায় ও সমভ্রান্ত কিছু বাড়িতে । সিলেট অন্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত পাহাড়ি জনগন সম্বলিত , বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্প্রীতিতে আবদ্ধ একটি বড় থানা এই কুলাউড়া ।
১৯৭০ সালের ৭ ই ডিসেম্বর তৎকালিন পাকিস্তান সরকারের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কুলাউড়া থেকে ব্যারিষ্টার আব্দুল মোন্তাকিম চৌধুরী এবং ১৭ ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পৃথ্থিমপাশার নবাব আলী সারোয়ার খান নির্বাচিত হয়েছিলেন ।
ঐ নির্বাচনে সারাদেশে আওয়ামী লীগ নিরংকুষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে । কিন্তু পাকিস্তানী শোষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করেই ২৫ যে মার্চ রাতে হায়েনারা নিরস্র বাঙ্গালীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে , গনহত্যা , নির্যাতন, ধর্ষন ইত্যাদি শুরু করে |
প্রসংগত উল্লখ্য ১৯৭১ এর ২৮ শে ফেব্রুয়ারি কুলাউড়ার ডাক বাংলোর সামনে এক বিশাল জনসভায় তৎকালীন ডাকসুর ভি পি আ.স.ম. আবদুর রব এসে ঘোষনা দেন পাকিস্তান হিসাবে এটাই তার শেষ জনসভা , স্বাধীনতার চুড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তিনি কুলাউড়ার সর্বস্তরের জনগনকে আহ্বান জানান ।
১লা মার্চ আহুত জাতিয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলে ,পরদিন সারাদেশের মত কুলাউড়ায় ও স্থানীয় নেতৃবৃনদের সাথে স্বতস্ফুর্ত সহায়তায় সর্বাত্বক হরতাল পালিত হয়।৩রা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সারাদেশের ন্যায় কুলাউড়া ও গর্জে উঠে ,৭ ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স মাঠে জাতীরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ঐতিহাসিক এক বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে আনুষ্ঠানিক ভাবে বজ্রকন্ঠে বাংলার স্বাধীনতা ও যার যা কিছু আছে তা নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানান ।
পাকিস্তানী ঔপনিবেশকদের শৃঙ্খল ছিন্নকরে , দেশকে স্বাধীনকরার শপথে বাংলার ঘরে ঘরে তখন সাজ সাজ রব , বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষনের পরেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় ।সারাদেশের ন্যায় কুলাউড়ার বিভিন্ন সংগঠনের নেতর্বৃন্দ ও কর্মীরা সভা সমিতির মাধ্যমে কুলাউড়াবাসীদেরকে চুড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করতে থাকেন ।
ইতিমধ্যে তৎকালিন ছাত্রলীগ নেতা গিয়াসউদদিন আহম্মেদ ৮ই মার্চ সকালে ঢাকা থেকে কাগজের তৈরী স্বাধীন বাংলার পতাকা কুলাউড়া য় নিয়ে আসেন ।
সেদিনটি ছিল পাকিস্তান দিবস ,
২৩ শে মার্চ , সেদিন কুলাউড়ার বেশ কিছু ঘরে সৈয়দ জামালউদ্দিনের নেত্বৃত্বে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা , গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি , ঐ সংগ্রাম কমিটির আহব্বায়ক ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল আবেদিন , সদস্য ছিলেন আব্দুল জব্বার , ব্যরিষ্টার মোন্তাকিম চৌধুরী ,জুবেদ চৌধুরী , সৈয়দ জামাল উদ্দিন , মোঃ আজির উদ্দিন খান , আব্দুল মালিক , নূর আহম্মেদ ,আব্দুস সালাম , মমরোজ বক্স,মুকিম উদ্দিন ও আরো অনেকে ।(চলবে )
শীতল পাটি
সৈয়দ শাকিল আহাদ
দাসের বাজার ইউনিয়ন ,
এই এলাকায় অর্থাৎ সিলেট , মৌলভীবাজার কুলাউড়া এলাকায় একটি পরিচিত নাম , দাসের বাজার মুলত বড়লেখা উপজেলার মধ্যে অবস্থিত । স্থানীয় দাস সম্প্রদায় বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিয্যবাহী লোকজ শিল্প নকশাদার মর্যাদাপূর্ণ শীতল পাটি তৈরী করে ,শীতল পাটি এক ধরনের মেঝেতে পাতা আসন বা গালিচা।
এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যগত কুটির শিল্প।
মুর্তা বা পাটি বেত বা মোস্তাক নামক গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের ছাল থেকে এগুলো তৈরি হয়ে থাকে।
হস্তশিল্প হিসাবে এগুলোর যথেষ্ট কদর রয়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র ও ইদানিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচছে ,শহরে শো-পিস এবং গ্রামে এটি মাদুর ও চাদরের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাজসজ্জা দ্বারা সজ্জিত মাদুরকে নকশি পাটিও বলা হয়।উল্লেখ্য জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ২০১৭ সালে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের শীতল পাটি বুননের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।শীতল পাটি বাংলাদেশের অন্যান্য অন্চল যেমন চট্রগ্রাম , টাঙ্গাইল , সিরাজগঞ্জ , ঝালকাঠি , ও মুন্সীগঞ্জ সুনামগন্জ সহ আরো বেশ কিছু স্থানে হয়ে থাকে কিন্তু সর্বোপরি সিলেটের শীতলপাটিই সমাদৃত ও বিখ্যাত ।
৭১ এর স্মৃতিতে কুলাউড়া
“রামগোপাল ফার্মেসী “
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কুলাঊড়ায় অনেক অনেক গুনীজনের জন্ম হয়েছে আমার এই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ সামান্য জ্ঞান দ্বারা তাদের সবাইকে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তবু ও যতটুকু মনে আছে সেই স্বরণশক্তি দিয়েই তাদের কারে কারো কথা কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি , এই মুহুর্তে একজনের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে , চিকিৎসা সেবার যাঁদের অনবদ্য অবদান রয়েছে কুলাউড়ার জনগনের কাছে আমার জানামতে “রসেন্দ্র ভট “ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য একজন ভাল লোক,
তিনি ছিলেন কুলাউড়ার নামকরা “রামগোপাল ফার্মেসির” প্রতিষ্ঠাতা যা এখনো দাড়িয়ে আছে কুলাঊড়া দক্ষিন বাজার মেইন রোডে।
১৯৭১ সালে এই ফার্মেসি সর্বদা খোলা থাকতো এবং সকলের কাছে একটি নিরাপদ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার স্থান , ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সকলেই বিশেষ করে দুর দুরান্ত থেকে আগত খাসিয়া উপজাতীয় নারী পুরুষের বসার জায়গা হিসাবে পরিচিত ছিল , এই ফার্মেসী , ঢুকেই দুই পাশ্বে লম্বা কাঠের হাতল ওয়ালা বেন্চ ছিল , সামনে ছিল তিন চারটি চেয়ারও
রশেন্দ্র ভটের মাগুরাস্থ বসত বাড়িটিকে সবাই “ভটের বাড়ি “ বললে একনামে তখনও চিনতো এখনও চিনে । তিনি ছিলেন খুব মানবিক এবং খুবই সামাজিক। রসেন্দ্র ভট এর সুযোগ্য পুত্র চুনু ভট সবসময় বসতেন ফার্মেসীতে উভয়ের সাথেই আমার নানা মরহুম এ এম আশরাফ আলী (সাব রেজিষ্টার) সাহেব সহ সমগ্র কুলাউড়ার সম্ভ্রান্ত শ্রেনীর ও গরীব দুখী সকলের সাথেই ছিল একটা সুন্দর সৌজন্য সম্পর্ক ,
যা আজও আমাদের সকলের মনকে পোড়ায়। রামগোপাল ফার্মেসীতে একজন রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির খাটোমত কম্পাঊন্ডারও ছিলেন। যাকে খোকন বাবু নামে সবাই জানত। বাড়ীতে কারো ও যে কোন অসুখ হলেই আমরা রামগোপাল ফার্মেসীতে চুনু ভটের কাছে যেতাম।
চুনু ভট তখন অসুখের বিবরন শুনে ঐ খোকন নামের লোকটিকে কি কি যেন বলে দিতেন।খোকন বাবু সেই কথামালা অনুযায়ী পিছনে পর্দা সরিয়ে ল্যাবরেটরীতে ডুকে কাজ করতেন এবং বেশ কিছুক্ষন পরে এসে খাঁজ কাটা ছয় দাগের একটা কাগজ লাগানো তরল ঔষধে ভরা কাঁচের শিশি হাতে দিয়ে বলতেন দিনে তিনবাব খাবে।
আম্মা , নানু সহ বাড়ীর মুরব্বী রা খুউব মনোযোগের সাথে সেই ওষুধ খেতেন এবং খুব তারাতাড়ীই সেরে উঠতেন।
আমি কখনোই এসব ঔষধ ভাল করে খেতাম না। ঐ তরল ঔষধটাকে “মিকচার “বলা হত। আমারও আমার বোনের জ্বর হলে মিকচার দিয়ে যেতেন খোকন বাবু। আমরা কোনরকমে একদুই ডোজ খেয়ে বাকিটা ফেলে দিতাম। এই ছিল আমার মিকচার খাওয়ার দিনগুলি।
তো যাই হোক আমরা রসেন্দ্র ভটের কথায় ফিরে যাই , তিনি সামাজিক ও মানবিক কাজে খুবই উজ্জল একজন মানুষ ছিলেন।
রসেন্দ্র ভটের ছোট মেয়ে অন্জনা ও নাতনী পম্পা র কথাও মনে আছে ,উনারা আমাকে বেশ আদর করতেন , আমার নানাবাড়ী অর্থাৎ উছলা পাড়া খান সাহেবের বাড়ীতে একটি তেঁতুল গাছ ছিল , আর ঐ গাছের তেঁতুল আমি উনাদেরকে বেশ কয়েক বার খাওয়াছিলাম , আমার স্কুল ছিল কুলাউড়া পাঠশালা বলে খ্যাত বি এইচ স্কুল , সেই স্কুলে যাওয়া আসার জন্য আমরা পিছনে খোলা জমিন পেরিয়ে এই রশেন্দ্র ভটের বাড়ীর উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারতাম । সহজ দুরত্ব ও কাছে
থাকায় আমি ভটের বাড়ীর উপর দিয়ে বার বার গিয়েছি। দেখেছি ওদের বাড়ীতে উঠানের চারপাশে অনেক ছোট ছোট ঘর। বাঁশের বেড়া ও ছনের ছাউনি দেওয়া পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।
জানতে চেয়েছি এত ঘরে কে থাকে ? সেই ছোটবেলার কথা অন্জনা দিদির কাছে শুনেছি বয়েজ স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক থাকেন ঐ ঘরগুলোতে ।
বালিকা বিদ্যালয়ের দূর দূরান্তের অনেক ছাত্রীও থাকতেন তাদের কাউকেই থাকা খাওয়া বাবত কোন টাকা দিতে হত না। কোথাও কারো বিপদ হলে রসেন্দ্র ভট দ্রুত ছুটে এসে বলতেল আমি জানলাম না কেন। দেশভাগের পর শিলচর আসাম কাছার ইত্যাদি এলাকা থেকে বদলে আসা মানুষদের পাশে দাড়িয়েছিলেন ভিন্নধর্মী একজন অসাধারন মানুষ । তিনি তার দয়াদ্রতা ও মানবিক মানসিকতা দিয়ে আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষিয়ে গেছেন । উল্লেখযোগ্য কিছু তো দিয়েছেন যা আমরা মনে রেখেছি , রাম গোপাল ফার্মেসির বর্তমান সত্ত্বাধিকারী তারই উত্তরসুরী সৌম্য প্রদীপ ভট্টাচার্য্য সজল ।
কুলাউড়ার নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই গুণীজনদের নাম শুনে থাকবেন কিন্তু বর্তমানে তাদের নিয়ে , তাদের ব্যাপারে কোথাও বিষদ কোন আলোচনা হবে কিনা জানিনা তবে এই গ্রুপ স্মৃষ্টির মাধ্যমে কেউ কেউ অনেক গুণীজনের কথা , সুখের স্মৃতিচারণ করছেন , উল্লেখযোগ্য স্থানের বর্ণনা তুলে ধরছেন দেখে ভাল লাগছে । তথ্য সহযোগীতা ও কৃতজ্ঞতায় – আলেয়া চৌধুরী
আলী আমজদ এর ঘড়ি
সৈয়দ শাকিল আহাদ
কি এক মায়ার টানে বার বার ছুটে যাই সিলেট , যাবো না কেন ? পুর্বপুরুষের ভিটা মাটি , কবর রয়েছে এই সিলেটে , হযরত শাহজালাল (র:) ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে যখন সিলেট বিজয় করেছিলেন তখন তার সাথীদের মাঝে অন্যতম একজন হলেন সৈয়দ হামজা ( সেরসোয়ারী )।, সিলেট শহরের ঝরনার পারে রয়েছে তার মাজার , তারই পরবর্তী এক পুরুষ চলে আসেন ময়মনসিংহের সেকান্দর নগরে তিনি হলেন সৈয়দ আব্দুল হাফিজ যিনি টিলার উপরে থাকতেন বলে তাকে টিলার সাহেব বলা হতো আমার দাদা সৈয়দ আব্দুল হাকাম এর পিতা ,আর নানা বাড়ী কুলাউড়া হওয়ার সুবাদে মায়ের দিকের বিশাল আত্বীয় স্বজন এবং বাবার দিকের আত্বীয় স্বজন দের সিলেটে অবস্তানের জন্য ও আরো বেশী যাওয়া আসার জন্য একটু বেশিই টান রয়েছে সিলেট এর প্রতি , যদিও আমার জন্ম কিশোরগন্জে আমার বাবার নানা বাড়ী হয়বতনগর জমিদার বাড়ীতে ।
সিলেট শহরের অনেক ইতিহাস ঐতিয্য নিয়ে অল্প বিস্তর লেখালেখির সুবাদে এবং কারো কারো উৎসাহে ইদানিং সিলেট এর বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে আনন্দ ও পুলক অনুভব করছি। সম্প্রতি কীন ব্রিজ নিয়ে একটি লেখা পোস্ট করে বেশ আলোচনা সমালোচনার মুখে পডেছি এবং পাঠককুল ও সজ্জনদের উৎসাহ ও অণুপ্রেরনায় বেশ উজ্জিবিত লাগছে নিজেকে , আর তাই ঐ ব্রিজের পাশে চাঁদনীঘাটে সুরমা নদীর উত্তরতীরে এবং কিন ব্রীজের বায়ে আলী আমজদের যে ঘড়িটি অবস্থিত ঐ ঘড়ি নিয়ে কিছু একটা লেখার তাগিদ অনুভব করছি ।
জনশ্রুতি রয়েছে এবং বিভিন্ন লেখক গবেষকের গবেষনালব্ধ বিবরনীতে এসেছে যে, ভারতের দিল্লির চাঁদনীচক থেকে অনুপ্রানিত হয়ে নবাব আলী আহমেদ খান ১৮৭৪ সালে এই ঘড়িটি স্থাপন করেন। তখন নবাব আলী আহমেদ তাঁর পুত্র নবাব আলী আমজদ খানের নামে ঘড়িটির নামকরন করেন ।কিছু কিছু জায়গায় আবার এমনও শোনা যায় যে আমজাদ আলী নিজেই এই ঘড়িটি স্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘড়িটি নির্মাণের সময় কুলাউড়ার নবাব আমজদ আলীর বয়স ছিল মাত্র ৩ বছর।
সিলেটে একটি স্থানীয় প্রবাদ রয়েছে যা এখন ও চালু আছে:
“চাঁদনী ঘাটের সিড়ি,
আলী আমজদের ঘড়ি,
জিতু মিয়ার বাড়ী,
বঙ্কু বাবুর দাড়ি।”
আলী আমজদের ঘড়ি সিলেট শহরে অবস্থিত ঊনবিংশ শতকের একটি স্থাপনা, যা ঘড়িঘর নামে একটি ঘরের চূড়ায় স্থাপিত বিরাটাকায় ঘড়ি।
সিলেট শহরের প্রবেশদ্বারে সুরমা নদীর তীর ঘেঁষে ক্রীন ব্রিজের পার্শ্বে সিলেট সদর উপজেলায় অবস্থিত এই ঘড়িটির ডায়ামিটার আড়াই ফুট এবং ঘড়ির কাঁটা দুই ফুট লম্বা।
স্বাধীনতার পূর্বে যখন ঘড়ির অবাধ প্রচলন ছিল না,
অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে সিলেট মহানগরীর প্রবেশমুখে এই ঐতিহাসিক ঘড়ি ঘরটি তৈরী করেন সিলেটের
লোহার খুঁটির উপর মজবুত ঢেউটিন দিয়ে সুউচ্চ গম্বুজ আকৃতির স্থাপত্যশৈলীর ঘড়িঘরটি তখন থেকেই আলী আমজদের ঘড়িঘর নামে দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করে।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পাক হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে এই প্রাচীন ঘড়িঘরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশ স্বাধীনের পর সিলেট পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ঘরসহ ঘড়িটি মেরামতের মাধ্যমে সচল করলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে যায়।
বিভিন সময়ে বন্ধ ও চালু হওয়ার পরও সর্বশেষ ২০১১ সনে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এই ঘড়িটিকে পূণরায় মেরামত করলে তা এখনও সচল রয়েছে।
মুড়ির টিন
সৈয়দ শাকিল আহাদ
বর্তমানে তিলোত্তমা সিলেট ও ঢাকায় যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের নামী দামী নতুন নতুন কার , জীপ ,গাড়ী , বাস , ভলভো , স্লিপিং বাস ইত্যাদি চলাচল করে তবে এই সকল অত্যাধুনিক বাসের ভীড়ে মুড়ির টিনের কথা কি করে ভুলি ?
ছোটবেলায় যখন প্রথম সিলেট থেকে ঢাকায় আসি সেটাও সত্তরের দশকের শুরুতে , মনে আছে সেই দিনটির কথা , কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে বেবি টেক্সি করে আজিমপুর গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে যাই ওখানে বড় খালার বাড়ীতে উঠি , পরদিনই ফুপুর বাড়ীতে পুরান ঢাকার ৫১ যোগীনগর লেনে গিয়ে উঠি ।যদিও ৬৭-৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে আমরা ঢাকার ৪১ নং আগা মসি লেনে থাকতাম ।পরবর্তীতে সিলেট চলে যাই , ছিলাম কুলাউড়ায় সেখানেও দেখেছি কুলাউড়া মৌলভীবাজার রুটে চলাচল করতো এই জাতীয় মুড়ির টিন বাস , সিলেট -ছাতক , সিলেট মৌলভীবাজার সহ বেশ কয়েকটি রুটে চলতো মুড়ির টিন বাস সার্ভিস ।
তবে রাজধানীতে স্বাধীনতার পরের কথা বলছি ,
ঢাকায় তখন পাবলিক বাসের কথা মনে আছে , যোগীনগর গুলিস্থানের কাছে হওয়াতে ফুলবাড়িয়াতেও আসতে হতো , এখানেই ছিল সারা বাংলাদেশের সড়কপথে যোগাযোগের ঘাঁটি বা মুল বাস স্ট্যান্ড এখন যেখানে গড়ে উঠেছে নগর ভবন ও বংগবাজার , শুনেছি এক সময় এখানেই ছিল ঢাকার মুল রেলওয়ে স্টেশন ।
গুলিস্তান কাছে হওয়াতে প্রথমেই চোখে পড়ে মুড়ির টিন , এই মুড়ির টিন দিয়ে ঢাকা শহরে বাস ভ্রমনের সুত্রপাত ।
নব্বইয়ের দশকে ও মহাখালী টংগী রুটে যখন বাসে উঠতাম তখন ঐ রুটে চলতো বলাকা সার্ভিস। বলাকা সার্ভিসকে ও আমরা বলতাম মুড়ির টিন। বলাকা এখনও চালু আছে তবে রুপ পরিবর্তিত হয়ে চলাচল করছে । মুড়ির টিন নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে আর একটু রোমাঞ্চিত হচছি ঢাকার ঐতিয্য ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে। কেননা আগামীতে কোন এক দিন আসবে যে দিনে মুড়ির টিনে যে চলাচল করেছি
তা বলার ও কেউ ভবিষ্যতে থাকবে না, সেটা নিশ্চিত হয়ে গেছি।বলে রাখা ভাল ঢাকায় পাবলিক বাসের যাত্রা শুরু মুড়ির টিন দিয়ে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে এ অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর ব্যবহৃত ট্রাক ও গাড়ি নিলামে বিক্রি হয়। ট্রাকগুলোর কাঠের বডিতে বাসের আদল দিয়ে তৈরি হয় নাকবোঁচা বাস। বাইরের দিকে কাঠের বডির ওপর মুড়ে দেওয়া হয় টিন।
সেই থেকেই বাসটির নাম হয় ‘মুড়ির টিন’।আবার অনেকের মতে, মুড়ির মতো ভরাট হয়ে অধিক যাত্রী ওঠানোর কারণে নাম হয়েছে মুড়ির টিন।এই বাসটি শুরুতে সদরঘাট, নবাবপুর, ইসলামপুর, চকবাজার, গুলিস্তানের মধ্যে চলাচল করত এই মুড়ির টিন। পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ, মিরপুর, ডেমরা, রামপুরা রুটেও মুড়ির টিন বাস চলাচল করতো । এ ছাড়া গুলিস্তান থেকে কালিয়াকৈর, নয়ারহাট, আরিচায়ও যাতায়াত করত এক ধরনের লম্বাকৃতির মুড়ির টিন ।
মুড়ির টিন বাস মুলত সত্তর ও আশির দশকে বেশি চলেছে। ঢাকায় ঘোড়া আর গরুর গাড়ি থাকলেও গণপরিবহন হিসেবে মুড়ির টিনই ছিল সাধারন যাত্রীদের অন্যতম ভরসা।
ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হতো এর ইঞ্জিন। কাঠের বডি তৈরি করত স্থানীয় মিস্ত্রিরা বিভিন্ন কারখানায় তৈরী করতো এই বাসটি ,ভেতরে চারধারে বেঞ্চের মতো করে সিট বসানো হতো। ২০-২২ জন বসার সুযোগ পেত।
৫০ জনের বেশি যাত্রী দাঁড়িয়েই থাকত। স্টিলের জানালার পুরোটাই খোলা যেত বলে বাতাস চলাচলের সুযোগ ছিল বেশি। প্রথম দিকে হাতে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে হতো। বাসে উঠলেই ড্রাইভারের মুখে হেলপারের উদ্দেশ্য একটি বাক্য শোনা যেত “ হেন্ডেলটা ঘুরা”পরে হ্যান্ডেলের পরিবর্তে আধুনিকতার পরশে চাবি সংযোজন করা হয়। গাড়ির গতি ছিল ১৫ থেকে ২৫ কিলোমিটার। স্টিয়ারিং ছিল শক্ত। পিতলের হর্ন চাপ দিয়ে বাজানো হতো।আর ভাড়া আদায়কারী কন্ডাক্টরের কাঁধের একপাশে থাকত লম্বা ফিতাযুক্ত চামড়ার ব্যাগ।
টাকা-পয়সা ও টিকিট রাখার জন্য আলাদা তিনটি পকেট ছিল তাতে। জগন্নাথ কলেজের যা এখন বিশ্ববিদ্যালয় এর পেছনের গেটে ছিল এই সদরঘাট রামপুরা রুটে চলাচল কারী মুড়ির টিন বাসের স্ট্যান্ড ।সেখান থেকে ছেড়ে কোর্টকাচারী ,চিত্রামহল-নাজিরা বাজার-ফুলবাড়িয়া-গুলিস্তান-পল্টন হয়ে রামপুরা যেত।
প্রতি ট্রিপে ২৫ মিনিট সময় বরাদ্দ ছিল। প্রতি মিনিট দেরির জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা হতো। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে সামনের নাক উঠে গিয়ে গাড়ি বড় হয়। সিটও বাড়ে। ২৫ বছরের পুরনো গাড়ির ফিটনেস বাতিল করা হলে আশির দশকের পর ঢাকা থেকে মুড়ির টিন প্রায় উঠে যায়। তবে মুড়ির টিনের পরবর্তী কাঠের তৈরি বডির গাড়ি ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত থাকে। তখন সর্বশেষ বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে এটি চলাচল করতে দেখা যায়।যে কোন মামলা মোকদ্দমা কাজে বা নৌপথে দক্ষিনান্চলে চলাচল কারী জনগনকে অবশ্যই এই রুটের মুড়ির টিনে চড়তে দেখা যেতো । আজ এই “মুড়ির টিন “ বাস সার্ভিসটি আমাদের কাছে অতীত স্মৃতি ,ঢাকা শহরে চলাচল কারী নামী দামী ব্যক্তিত্ব ,বিভিন্ন শ্রেনীপেশার সর্বস্তরের জনগনই কম বেশী এই মুড়ির টিনের সাথে পরিচিত ছিলেন বলে আমার বিস্বাস । এই মুড়ির টিন অবশ্যই ঢাকার ঐতিয্যের ই একটি অংশ ।
ছোটবেলার কথা – (পর্ব ২ )
সৈয়দ শাকিল আহাদ
ছোটবেলার ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা , কিছু স্মৃতি , কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির অস্তিত্ব জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে যখনই মনে হয় তখনই সুখস্মৃতি ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে হ্রদয় হারিয়ে যাই অতীতে ।
সেই দিনটি ছিল ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন একদিন আমার বয়স তখন ১০ বছর । আম্মা আমাদের নিয়ে রাতের মেইল ট্রেনে করে নানা বাড়ী কুলাউড়া থেকে কিশোরগন্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন ।
বড়মামা আমির আলী তাদের জনৈক বাগীদার চাতলগাও এর কটাই মিয়া কে নিয়ে কুলাউড়া রেল স্টেশনে আম্মাকে সহ আমাদের চার ভাই বোনকে দুইটি সুটকেস সহ সিলেট থেকে ছেড়ে আসা মেইল ট্রেনের একটি ২ য় শ্রেনীর বগীতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, ঐ বগীতে সাথে ছিলেন সহযাত্রী আমাদেরই আর এক আত্বীয় যিনি সম্পর্কে মামা , আমাদের সাথে উঠেছিলেন তিনি ঢাকা যাবেন বলে ,
কথা ছিল তিনি ঢাকাতে যাবেন আর আমরা নামবো ভৈরব বাজার স্টেশন এ , আমাদের ভালভাবে ভৈরবে নামিয়ে দিয়ে তিনি ঐ ট্রেনেই ঢাকা চলে যাবেন ।
মজার ব্যপার ছিলো তখন এই ঢাকা মেইলটি সিলেট থেকে ছেড়ে এসে কুলাউড়ার উত্তর বাজার রেল সিগনালে পৌছে ক্রমশ হুইসেল দিতো আর সেই হুইসেলের শব্দ শুনে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে ষ্টেশনে পৌছে গিয়ে ট্রেন ধরতে পারতাম ।
তার কারন ছিল , ট্রেনটি কুলাউড়া রেল স্টেশনে অনেকক্ষন অপেক্ষা করতো , একই সময়ে আসা লাতুর ট্রেনের যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য এবং পিছনের মাল গাড়ী গুলোতে , বিভিন্ন চা বাগানের চা পাতা , পান সুপারি , ফলমুল , ইত্যাদি কুলাউড়া থেকে ঢাকা সহ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতো এই রেলের মাধ্যমেই , যার ফলশ্রুতিতে এই ষ্টেশনে মেইল ট্রেনটির দেরি হতো আর এই দেরির ফলে আমরাও বাড়ী থেকে ট্রেন আসার শব্দ শুনে স্টেশনে পৌছে স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেন ধরতে পারতাম ।
সেদিন প্রথমে আমাদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বড় মামা তাড়াতাড়ি টিকেট কেটে এনে আম্মার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন “ আফা বাচ্চাইন্তরে লইয়া সাবধানে যাইঅইন , আল্লাহর হাতে সপি দিলাম , পৌছিয়া টেলিগ্রাম দিয়েন । তখন দ্রুত খবর পৌঁছানোর অন্যতম পন্থা ছিল টেলিগ্রাম ।
যাই হোক ট্রেনটি কুলাউড়া ছেড়েছিল রাত প্রায় ১১ টায় , সেই রাতের ট্রেনের সেই স্বরনীয় অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কখনই ভোলার মত নয় কারন ,ঐ যাত্রায় কুলাউড়া থেকে ট্রেনটি ছেড়ে দেবার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা মনে নেই ,মনে আছে মধ্যরাতে হটাৎ ঘুম ভেঙ্গেছিল আখাউড়া ষ্টেশনে হৈ চৈ দৌড়াদৌড়ির শব্দে , কে জানি এসে আম্মাকে বলেছিল যে ট্রেনের এই অংশটুকু ঢাকা যাবে না যাবে চট্রগ্রাম , আর ঢাকা যাবে পিছনের অংশটুকু , তখন আখাউড়া স্টেশনে ট্রেনের কাটাকাটি হতো । চট্রগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনের সামনের অংশ আর সিলেট থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনের পিছনের অংশের নির্দিষ্ট বগী গুলো মিলিয়ে একটি ঢাকামুখী ট্রেন ঢাকা যাবে ।আবার ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মেইল ট্রেনের পিছনের দিকের নির্দিষ্ট বগী গুলি র সাথে চট্রগ্রাম থেকে আসা টেনের একাংশ এক সাথে হয়ে সিলেট যাবে এবং সিলেট থেকে ছেড়ে আসা মেইল ট্রেনের সামনের দিকের বগীগুলোর সাথে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মেইল ট্রেনের নির্দিষ্ট বগীগুলো মিলিয়ে ট্রনটি চট্রগ্রাম যাবে ।
এই জংশনে এই কাটাকাটির অভিজ্ঞতা শুধু রাতের ট্রেনের চলাচল কারী যাত্রীরাই ভাল বলতে পারবেন ।
সেই রাতে আমরা ভুল করে কুলাউড়া থেকেই চট্রগ্রাম গামী বগীতে চড়েছিলাম যা কেউ ই বুঝতে পারি নাই , আর আমাদের সাথে কোন রকম সামর্থবান পুরুষ সহযাত্রী না থাকাতে আমাদের চার ভাইবোনকে নিয়ে এভাবে আম্মা সাহস করে রাতের ট্রেনে রওয়ানা দেবেন তা কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য ছিল না মেনে ও নেওয়া কষ্টকর ছিল ।
যাই হোক স্পষ্ট মনে পড়ে সে রাতে হটাৎ আখাউড়া স্টেশনে তাড়াহুড়া করে সুটকেস হাতে ঐ মামা টার হাত ধরে ঐ বগী থেকে আমরা সবাই নেমে পড়ি ,
মনে আছে আমি ও আমার ছোট বোন দৌড়াছ্ছিলাম ঢাকামুখী বগীতে উঠার জন্য আর সামনে দ্রুত দৌড়াচছিলেন আম্মা , আপা ও ওয়াকিল ,এক সময় খেয়াল করলাম ঐ মামাটা চলন্ত ট্রেনের একটি বগীতে আম্মা , আপা,ও ছোট ভাই ওয়াকিলকে সুটকেস সমেত তুলে দিয়ে দিল , আর পরের দুই তিনটি বগীর দরজা বন্ধ থাকাতে শেষের দিকের একটি বগীতে আমাকে ও আমার ছোট বোনকে কোন রকমে সুটকেস সহ ঐ চলন্ত ট্রেনের ঐ বগীতে তুলে দিয়ে গেইটের পাশের যাত্রীদের বলেছিল এদের একটু খেয়াল করবেন এরা ভৈরব নামবে সামনের বগীতে এদের সাথের লোক রয়েছে ।পরের স্টেশনে এসে এদের নিয়ে যাবে । কি ভয়াবহ লোম হর্ষক সেই অভিজ্ঞতা , অন্ধকার রাতে , অপরিচিত লোকজনদের মাঝে চলন্ত ট্রেনে হটাৎ আমরা সুটকেস সহ ছোট ছোট দুইটি শিশু , ভয়ে কান্না শুরু করলাম , সবাই মিলে আমাদের অনেক সান্তনা দিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করেছিল , এবং কিছুক্ষন পর ট্রেনটি ব্রাম্বনবাড়ীয়া ষ্টেশনে থামলে পরে হন্ত দন্ত হয়ে আম্মা ছুটে এসে ঐ বগীর সকলকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের দুই ভাই বোন কে নিয়ে ঐ বগীতে গেলেন , আমরা ও আমাদের অন্য দুই ভাইবোনদের ফিরে পেয়ে অত্যান্ত আনন্দিত হয়েছিলাম এবং একটু পড়েই ভৈরব ষ্টেশনে ট্রেনটি থামার পর আমরা সবাই নেমে পড়ি এবং ঐ ষ্টেশনে দাড়িয়ে থাকা অন্য একটি লোকাল ট্রেন যোগে পরদিন ভোরে কিশোরগন্জ গিয়ে পৌঁছাই ।
বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার কথা হয়তো অজ্ঞাত ই থেকে যেতো কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা যাবে না এর কারন আমার অতীতের বিভিন্ন প্রকার স্মৃতি চারণ মুলক গল্প ও অভিজ্ঞতা লেখার চেষ্টা ও আমরার সিলোটি আড্ডার মত এত বিশাল ও সৌখিন রুচিশীল পাঠক লেখকের সম্বন্নয়ে সম্বৃদ্ধ একটি প্লাট ফর্মে প্রচারিত হবার সুযোগ তৈরী করে দেওয়ার ফলে ।
এই স্মৃতিচারনের মাঝে কিছু ভয়াবহ বাস্তবতার সন্ধান রয়েছে যা ভেবে আমি বহুবার আহত হয়েছি ,আবার সেদিনের সেই ঘটনাসমুহ এবং সেরাতের দুর্বিসহ যাত্রা আমাকে এবং আম্মার সহনীয় ধৈর্য ও অযাচীত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার অসীম শক্তি আমাকে সর্বদাই অনুপ্রাণিত করে যে আমি একজন সংগ্রামী নারীর সন্তান । আজ আম্মা নেই আমি তার বিদ্বেহী আত্বার শান্তি কামনা করছি । আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমার আম্মা আব্বাকে জান্নাত নসীব করুন । আমিন
প্রাচীন মসজিদের কিছু কথা ।
সৈয়দ শাকিল আহাদ.
সিলেট বিভাগের সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ খুঁজতে গিয়ে জানতে পাই হবিগঞ্জের উচাইল শংকরপাশা শাহী মসজিদ বা গায়েবি মসজিদটি যা বহু পুরাতন
স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন ।
এই মসজিদটি সুলতানি আমলের স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। হবিগন্জ সদর উপজেলার রাজিউরা ইউনিয়নের উচাইল গ্রামে প্রায় ৬ একর জমির ওপর কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে ঐতিয্যবাহী মসজিদটি।
ইতিহাসবিদদের দেয়া তথ্য মতে জানা যায়, এই মসজিদটির কারুকাজ আর নির্মাণশৈলী অত্যন্ত চমৎকার ।উন্নতমানের প্রলেপহীন পোড়া ইট কেটে সেঁটে দেওয়া হয়েছে ইমারতে। দেয়ালের বাইরের অংশে পোড়া ইটের ওপর বিভিন্ন নকশা এবং অলঙ্করণ সহজেই মুসল্লি ও দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
মসজিদটি লাল বা রক্তিম বলে অনেকে এই মসজিদটিকে “লাল মসজিদ” হিসাবে গন্য করে থাকেন। আবার টিলার বেশ উপরে বলে ‘টিলা মসজিদ’ও বলা হয়। দু’টি মিলিয়ে ‘লালটিলা মসজিদ’ও বলেন কেউ কেউ এটিকে “গায়েবি মসজিদ” ও বলে থাকেন।
এবার আসি রাজধানী ঢাকা শহরে ,এই ঢাকায় ছয় হাজার এর বেশি মসজিদ রয়েছে এবং সমগ্র শহর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহাসিক মসজিদের প্রাচুর্যের কারণে একে মসজিদের শহর বলা হয়ে থাকে এই মসজিদগুলোর স্থাপত্য সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ঢাকার সুনাম বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখে। বলছি পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তারা মসজিদ নিয়ে কিছু কথা। পুরান ঢাকা বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মসজিদের জন্যও পরিচিত। পুরান ঢাকার অনেক এলাকায় এরকম অনেক মসজিদ আছে যেগুলো শত বছরের পুরনো কিন্তু ইতিহাস কে সাথে নিয়ে টিকে আছে বছরের পর বছর। আরমানিটোলায় অবস্থিত তারা মসজিদও এরকম একটি পুরান মসজিদ।
১৯ শতকের প্রথম অর্ধাংশে ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি মীর আবু সায়ীদ ‘র নাতি মির্জা গোলাম পীর আঠার শতকের শুরুতে ঢাকায় আসেন এবং এই মসজিদের নির্মাণ করান। যে কারণে এটি মির্জা সাহেবের মসজিদ হিসেবে বেশ পরিচিতি পায়। ১৮৬০ সালে তিনি মারা যাওয়ার পরে ১৯২৬ সালে সেই এলাকার এক স্থানীয় ব্যবসায়ী আলী জান বেপারী মসজিদটির সংস্কার কাজ করান এবং বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন।
মসজিদটি যেহেতু আঠার শতকের পর পর নির্মিত, সেকারনে মসজিদের গঠনশৈলীতে মোঘল স্থাপত্যবিদ্যার ছোঁয়া নজরে পরে। আরমানিটোলার তারা মসজিদ ছাড়াও কসাইটুলীর মসজিদগুলোতেও মোঘল স্থাপত্যশৈলী দেখা যায়।
মির্জা গোলাম যখন মসজিদটির নির্মাণ করান, তখন মসজিদটি ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল, যার মধ্যে মধ্য গম্বুজটি ছিল সবচেয়ে বড়। পরবর্তী সংস্কারের সময় মসজিদটিকে পঞ্চগম্বুজ বিশিষ্ট করা হয় এবং সাথে যোগ করা হয় একটি আধুনিক নকশার বারান্দা। ৩৩ ফুট আয়তন থেকে সংস্কার পরবর্তী আয়তন দাড়ায় ৭০ ফুট। মসজিদটি শ্বেতপাথর দ্বারা নির্মিত এবং বাড়তি সৌন্দর্য যোগ করতে মসজিদের গায়ে আঁকানো হয়েছে নীলরঙা তারকারাজি। পুরাতন মসজিদের একটি মেহরাব ভেঙ্গে যোগ করা হয় আরও ৩টি মেহরাব। সংস্কার কাজের আরেকটি বিষয় ছিল মেঝের মোজাইকে জাপানি চিনি – টিকরির ব্যবহার। এই চিনি টিকরির ব্যবহারের কারনেই এই মসজিদটি চিনি টিকরির কয়েকটি টিকে থাকা নিদর্শনগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত।
পুরান ঢাকার প্রাচীন মসজিদ গুলোর মধ্যে নিম্নের মসজিদ গুলি উল্লেখযোগ্য:~যেমন –
বিনত বিবির মসজিদ ,
চক বাজার শাহী মসজিদ ,
কর্তালাব খান মসজিদ ,
তারা মসজিদ ,
মুসা খান মসজিদ ,
হাজী শাহবাজ মসজিদ ,
লালবাগ শাহী মসজিদ ,
খান মহম্মদ মৃধার মসজিদ ইত্যাদি
মসজিদগুলি শহরের বৈচিত্র্যময় এবং ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য ইসলামিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করে।
১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান চিশতি ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। প্রথমবারের মত ঢাকা রাজধানী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। তখন তিনি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর।ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেওয়া তথ্য অনুসারে রাজধানী ঢাকা, মুলত মসজিদের শহর হিসাবে পরিচিত।এক সময় মনে প্রশ্ন জাগতো, ঢাকাকে কেন মসজিদের শহর বলা হয়?
এই প্রশ্নের সহজ উত্তরে জানা যায় , ‘অনেক মসজিদ আছে এই শহরে, এজন্যই এই শহরকে মসজিদের শহর বলা হয়ে থাকে তবে এই শহরের বিশেষণ হিসেবে ‘মসজিদের শহর’তো আর একদিনে হয়নি।
ঠিক কত আগে এই জনশ্রুতি হয়েছিল?
এই প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া মুশকিল ।
তবে বায়ান্ন হাজার আর তেপান্ন গলির এই ঢাকায় সকাল আর সন্ধ্যা নামে আজানের সুরে।
অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে এই মসজিদের শহর ঢাকার প্রথম মসজিদ টি কোনটি?’
তাদের আশ্বস্ত করছি চলুন একটু ঢাকার প্রথম মসজিদ কোনটি খুঁজে বের করি,
ঢাকার অধিকাংশ প্রাচীন মসজিদগুলো কিন্তু মোগল আমলে তৈরি। মোগলদের দৃষ্টিনন্দন নির্মাণশৈলী তেমনটাই সাক্ষী দেয়। তবে ঠিক কবে বা কোন আমলে ঢাকায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ হয়েছিল সেই তথ্যই দেবার চেষ্টা করছি ।ইতিহাসবিদদের বর্ননায় জানা যায় , সুবেদার ইসলাম খাঁ ঢাকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানী ঘোষণা করেন ১৬১০ সালে। ১৬১০ এর আগের ইতিহাস তেমন একটা আমাদের কারোরই জানা নাই ,সুলতানী আমলে কেমন ছিল আজকের এই ঢাকা ? বা এর আগে সেন বংশ কিম্বা পাল বংশের সময়কালে কেমন ছিল এই জনপদ তাও সঠিক ভাবে উল্লেখ করা এই মুহুর্তে সম্ভব নয় । প্রথম মসজিদ হিসেবে যে মসজিদটির কথা আমরা বিভিন্ন সুত্রে জেনেছি , এর জন্য ঢাকার প্রথম মসজিদের খোঁজে আমাদেরকে যেতে হবে পুরান ঢাকার নারিন্দা এলাকায়। ধোলাইখাল মোড় থেকে দয়াগঞ্জ যেতে মাঝামাঝি নারিন্দা মোড়। ৬ নম্বর নারিন্দা রোডের অতি প্রাচীন ‘হায়াৎ বেপারী’র পুলের উত্তর দিক থেকে ৫০ গজ পেরোলেই দেখা মিলবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রাচীন মসজিদের।যার নাম বিনত বিবির মসজিদ। এই মসজিদের সম্পর্কে একটু জানা দরকার ।
এটি হচ্ছে রাজধানীর ৫৬৪ বছরের পুরনো মসজিদ। ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ হিসেবে পরিচিত এটি। মসজিদে খোদাই করা শিলালিপি থেকে জানা যায়, এটি পাঠান রাজা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে ১৪৫৬ সালে নির্মাণ করা হয়।
ইতিহাসবিদগণ নারিন্দার বিনত বিবি বা বখত বিবির মসজিদকে ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ বা প্রথম মসজিদ হিসেবে মনে করেন। মসজিদটির গায়ে রক্ষিত শিলালিপি অনুসারে ৮৬১ হিজরি সালে, অর্থাৎ ১৪৫৭ সালে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। তখন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসন চলছে। ইসলাম খানের আগমনের প্রায় ১৫০ বছর আগে মসজিদটি নির্মিত।
এই কথা বলা খুব কঠিন যে বিনত বিবির মসজিদ নির্মাণের আগে ঢাকায় কোনো মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। কেননা, বাংলার সুলতানরা মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সে যাইহোক, এখন স্বভাবতই প্রশ্ন চলে আসে কে ছিল বিনত বিবি? আর কেনই বা তার নামে এই মসজিদ!
বিনত বিবির খোঁজে নামার পর প্রথমেই আমাদের বিভ্রান্ত হতে হয় একেক জায়গাতে একেক রকম তথ্য দেখে। উইকিপিডিয়াতে গেলে দেখতে পাই বিনত বিবিকে বলা হয়েছে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যা। ড. মুনতাসীর মামুন এর ‘ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বিনত বিবি ছিলেন মারহামাতের কন্যা। কিন্তু এই মারহামাত কে ছিলেন সেটা জানা যায় নি তবে অন্য একটি প্রবন্ধে জানতে পাই বিনত বিবির পরিচয়ে লেখা হয়েছে তিনি জনৈক হার্মাদের কন্যা। এই তথ্য আমাদের অনুসন্ধানটি আরো সহজ করে দেয়। মারহামাত আর হার্মাদ শব্দযুগল যে একই ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারি। সেই সাথে বিনত বিবি যে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যা ছিলেন না সেটাও পরিষ্কার হয়ে যায়।
পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের বলা হতো হার্মাদ। সেই অনুপাতে আমরা ধরে নিতে পারি এখানে জনৈক হার্মাদ বলতে জনৈক ব্যবসায়ী বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ বিনত বিবির বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু পর্তুগিজরা কি মুসলমান ছিল? হিসাব মিলে না ঠিকঠাক। মূল ইতিহাস আমরা জানতে পারি ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন’এর অফিশিয়াল ওয়েব সাইটে।মসজিদটি নির্মাণ করেন মূলত বিনত বিবির বাবা আরকান আলী। সে সময় পারস্য উপসাগরের আশেপাশের লোকজন প্রায়ই জলপথে এ অঞ্চলে বাণিজ্যে আসতেন। পুরান ঢাকার এই এলাকা অর্থাৎ নারিন্দা থেকে ধোলাইখালের উপর দিয়ে তখন বয়ে যেত বুড়িগঙ্গার একটি শাখা যা বুড়িগঙ্গা হয়ে শীতলক্ষ্যায় সাথে সংযুক্ত হয়। আরাকান আলী নামক এক সওদাগর সে সময় এ এলাকায় বাণিজ্যের জন্য আসেন এবং এখানে বসবাস শুরু করেন। তিনিই নামাজ পড়ার সুবিধার্থে এখানে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।
এখানে বসবাসকালীন আরাকান আলীর মেয়ে বিনত বিবির আকস্মিক মৃত্যু হয়। এই মসজিদের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় এবং আরাকান আলীর মৃত্যু ঘটলে তাকেও এখানেই কবর দেয়া হয়। পরবর্তীতে মসজিদটির নামকরণ করা হয় বিনত বিবির নামে।
মসজিদটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— এর বিশেষ আকৃতির স্তম্ভ, বর্গাকার কক্ষের ওপর অর্ধ বৃত্তাকার গম্বুজ, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে খিলানের ব্যবহার, সাদামাটা অলঙ্করণ, প্লাস্টারে ঢাকা, বাঁকানো কার্নিশ । ছয়-সাত কাঠা জায়গায় গড়ে ওঠা মূল মসজিদটি বর্গাকৃতির এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট।
এর ভেতরের দিকের পরিমাপ প্রতিদিকে ৩.৬৬ মিটার। মসজিদটির ছাদ গোলাকার গম্বুজ দিয়ে ঢাকা এবং গম্বুজটি সরাসরি ছাদে স্থাপিত। মসজিদের দেওয়ালগুলো ১.৮৩ মিটার পুরু। এর পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে মোট তিনটি প্রবেশপথ আছে। পশ্চিম দেওয়ালের পেছনের দিকে একমাত্র মিহরাবটি প্রসারিত করা। আগে চার কোণে প্লাস্টারবিহীন বক্রাকৃতির ‘ব্যাটেলমেন্ট’যুক্ত অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ ছিল।
মসজিদটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো- শিলালিপি সম্ভবত ঢাকায় প্রাপ্ত শিলালিপিগুলোর মধ্যে বিনত বিবির মসজিদের শিলালিপিটিই ছিল প্রথম মুসলিম শিলালিপি। শিলালিপিটি মূল মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথে লাগানো ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটা উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয় প্রবেশ পথের মাথায় রয়েছে।বারবার সংস্কার এবং পরবর্তী সময়ে সংযোজনের ফলে বর্তমানে মসজিদের বাইরের প্রকৃত অবয়ব একেবারেই পাল্টে গেছে। তবে সঠিক ভাবে মসজিদটির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হলেও এতে প্রাক-মোঘল সালতানাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বারবার পুরু আস্তরণের ফলে মসজিদের পোড়ামাটির অলঙ্করণ এখন আর দেখা যায় না।
বিভিন্ন মুরব্বী ও প্রবীণ ঢাকাইয়াদের কাছ থেকে জানতে পারি যে বাংলা ১৩৩৭ সালে এই মসজিদটির দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয় এবং দ্বিতীয় গম্বুজটি স্থাপন করা হয়।প্রায় ২০০ বছর ধরে এলাকাবাসী একটি কমিটির মাধ্যমে এ মসজিদটির দেখাশোনা করে আসছেন।
বিনত বিবির মসজিদের মত ঢাকা শহরের প্রতিটি প্রাচিন মসজিদের রয়েছে গৌরবময় নির্মান ইতিহাস এবং ঢাকা শহর ছাড়াও সমগ্র দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন মসজিদের ইতিহাস জানা যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জানা প্রয়োজন
৭১ এর স্মৃতি – ১ সৈয়দ
সৈয়দ শাকিল আহাদ
সিলেটের একটি বিখ্যাত ফল সাতকরা।এই সাতকরা নিয়ে কিছু লিখতে পারবো ভেবে আনন্দ অনুভব করছি , খাবারের তালিকায় আমার অত্যান্ত প্রিয় একটি খাবার হচ্ছে সাতকরার তরকারী ।
সাতকরা যা সিলেট বাসীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ফল হলেও অন্যান্য জেলার মানুষের কাছে তেমন পরিচিতি নেই।ইদানিং অন্যান্য জেলার লোকেরা ও সাতকরা খাওয়া শিখছে ।
সাতকরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস ছোট মাছ দিয়ে, টক রান্না করে খাওয়া হয় এমন কি আচার ও তৈরী হয় যা খুবই সুস্বাদু ।
সাতকরা মুলত একটি গোলাকৃতির কমলা লেবুর মতো দেখতে লেবু জাতীয় ফল যা বৃহত্তর সিলেট এবং ভারতের আসাম ও মেঘালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলের স্থানীয়।
সাতকরার বৈজ্ঞানিক নাম ‘Citrus macroptera Montrouz var annamensis Tanaka’ এবং এই ফলটির আকৃতি প্রায় ৬-১০ সেমি।
সাতকরা গাছ উচ্চতায় ২-৩ মিটার হয় এবং প্রস্থ ২-৪ মিটার।
ফলের রং প্রথমে সবুজ এবং পেকে সবুজাভ হলুদ হয়।
সাতকরার প্রাকৃতিক ফলন সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে।
কিন্তু ব্যাপক চাহিদার কারণে সারাবছরই হিমাগারে সংরক্ষণ করে এটি বাজারে বিক্রি করা হয়।
সাতকরা ফলের পুরু খোসাই একমাত্র অংশ যা ভোজ্য এবং খাওয়ার আগে ভেতরের শাঁস ও বীজ অবশ্যই ফেলে দিতে হয়।
সাতকরা বেশিরভাগই বিক্রি হয় সিলেট শহরের বন্দর বাজার , দরগাহ গেইট , স্টেশনরোড ,আম্বর খানা সহ বিভিন্ন কাঁচাবাজারে , শ্রীমঙ্গলে, মৌলভীবাজার , কমলগঞ্জ, কুলাউড়া , জুড়ি , বিয়ানীবাজার সহ সিলেট বিভাগের উল্লেখযোগ্য বাজার সমুহে এবং কিছু জনপ্রিয় পর্যটন স্পটের সামনে ও বিভিন্ন দোকানপাটে।
অন্যান্য এলাকার তুলনায় সিলেট নগরীর বন্দরবাজার এলাকায় রাস্তার পাশে বেশ কয়েকজন বিক্রেতা তুলনামূলক ভালো মানের সাতকরা বিক্রি করেন।
অন্যান্য লেবু জাতীয় ফলের মতো সাতকরা কাঁচা খাওয়া যায় না। তবে গরু বা খাসির মাংস, বোয়াল মাছ কিংবা ডাল এ দিয়ে রান্না করা হয় সাতকরা ।
তবে জানা দরকার যে কেন এই অনন্য ফলটির স্বাদ আস্বাদন করতে হবে কিংবা কীভাবে সাতকরা রান্না করা হয়।
সাতকরা যদি ভালো মানের না হয়, তাহলে রান্না করে স্বাদ পাওয়া যায় না। আর তাই সিলেটের প্রবীণ গৃহিনীরা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।
তাদের মতে, সাতকরা কেনার সময় হলুদ-সবুজ রঙের ও মসৃণ ত্বক দেখে কিনতে হবে। কেনার সময় একটার পর একটা সাতকরা হাতে নিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটার ওজনের তারতম্য বিবেচনা করে সবচেয়ে ভারীগুলো কিনতে হবে। ভারী সাতকরার খোসা মোটা হবে এবং ভারী খোসা রান্নার জন্য সেরা।
এছাড়াও যতটা সম্ভব কালো বা বাদামী দাগহীন, কিংবা যতটা সম্ভব কম দাগযুক্ত সাতকরা পাওয়া যায়, সেগুলো কেনার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকেই বিশেষ করে মহিলা মুরব্বীরা ।
বোয়াল মাছ ও বিভিন্ন প্রকার মাছের তককারীতে সাতকরা :-
প্রথমে মাছ হালকা ভেজে তুলে রাখতে হয় ।তারপর পেঁয়াজ-রসুন ও অন্যান্য মসলা দিয়ে যেভাবে বোয়াল মাছ ভুনার জন্য গ্রেভি তৈরি করা হয়, সেখানে সেইভাবে গ্রেভি তৈরি করে তাতে সাতকরার টুকরো দিলেই হবে । কষিয়ে প্রায় সিদ্ধ হয়ে এলে ভাজা মাছ দিতে হয় এবং সামান্য কষিয়ে পরিমিত পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হয় । কিছুক্ষণ পর সাতকরা পুরোপুরি রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে সুস্বাদু খাবার হিসাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে ।
সাধারণত গরু বা খাসির মাংসের ভুনা যেভাবে রান্না হয়, সেভাবেই মেরিনেট করে রান্না শুরু করতে হবে। মাংস কষানোর সময় অর্ধেকটা সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে আগে থেকে টুকরো করে রান্না সাতকরা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ও ঢাকনা লাগিয়ে মাংস পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না চালিয়ে যেতে হবে।
সাতকরার তৈরী ডাল:
মসুর ডাল রান্নার সাধারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং রান্নার শুরুতে ডালের সঙ্গে সাতকরা দিয়ে ডাল ও সাতকরা সিদ্ধ হয়ে এলে সাতকরা আলাদা করে তুলে ফেলে তারপর পেঁয়াজ, রসুন, শুকনা মরিচ ও পাঁচফোড়ন দিয়ে বাগাড় দিয়ে আবারও তুলে রাখা সাতকরার টুকরোগুলো দিয়ে দিতে হয় ।
সাতকরার আচার:
অত্যান্ত সুস্বাদু এই আচার তৈরী করতে হয় একটি পাত্রে সরিষার তেল গরম করে তাতে আস্ত রসুন ও কাটা আদা দিয়ে রসুন ও আদা সিদ্ধ হয়ে এলে সাতকরার টুকরো দিয়ে পরিমাণমতো লবণ ছড়িয়ে দিয়ে ও কষাতে হয় ।সাতকরা তেলে ভাজা ভাজা হয়ে সিদ্ধ হয়ে এলে সামান্য সাদা ভিনেগার দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নামিয়ে রাখতে হয় । তারপর ঠাণ্ডা হলে কাঁচের পাত্রে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে খাদ্য তালিকায় আচার হিসাবে সাতকরা খাওয়া হয়ে থাকে ।
বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বানিজ্যিক ভিত্তিতে সাতকরার আচার বাজারজাতকরণ এর ফলে সারাদেশে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বর্তমানে সাতকরার আচার সুলভে পাওয়া যাচ্ছে । যার দ্বারা অত্যান্ত স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ আহরন সম্ভব হচ্ছে । আগামীতে আরো ব্যাপক আকারে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ আমেরিকাতে বাংলাদেশী অন্য রপ্তানীযোগ্য পন্যের মত সাতকরাও রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বহু লোকের কর্মসংস্হান সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ ।
মণিপুরী রাজবাড়ি
সৈয়দ শাকিল আহাদ
বাংলাদেশের আদি সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি জনগোষ্ঠি হচ্ছে মনিপুরী ।এই সিলেট শহরের মির্জাজাঙ্গালে অবস্থিত মণিপুরি রাজবাড়ীটি মনিপুরীদের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম একটি নির্দশন।
এই ভবনটির নির্মাণশৈলী সিলেট অঞ্চলের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ।
এককালের প্রভাবশালী রাজা গম্ভীর সিং এর স্মৃতিধন্য এই বাড়িটি আজ অবহেলিত ও বিলীন প্রায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে প্রকৃত ভবনটি হারিয়েছে তার স্বকীয়তা। বাড়ীর সু প্রাচীন প্রধান ফটক, সীমানা দেয়াল, মনোহর কারুকাজের সিড়ি ও বালাখাঁনার ধ্বংসাবশেষই বর্তমান মণিপুরী রাজবাড়ীর স্মৃতির সম্বল।
এখনও ধ্বংসস্থুপের মতো কোনরকমে টিকে থাকা স্থাপনাটি এ বাড়ীসহ সিলেটে বসবাসরত মণিপুরি সম্প্রদায়ের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তির স্থান।
বিভিন্ন গবেষকদের অনুসন্ধানে জানা যায়,
ঊনবিংশ শতাব্দীতে সিলেট শহরের মির্জাজাঙ্গালে রাজবাড়ীটি তৈরী হয়।
তৎকালীন মণিপুরি রাজ্যের
তিন সহোদর রাজা চৌর্জিৎ সিং, মার্জিত সিং ও গম্ভীর সিং এই রাজবাড়ীটি তৈরী করে এখানে বসবাস করেন।
পরে চৌর্জিৎ সিং ও মার্জিত সিং কমলগঞ্জের ভানুগাছ এলাকায় বসতি স্থাপন করলেও রাজা গম্ভীর সিং থেকে যান মির্জাজাঙ্গালের রাজবাড়ীতে।
১৮২৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় বার্মার সাথে যুদ্ধ করে মণিপুর রাজ্য পুরম্নদ্ধারের আগ পর্যন্ত রাজা গম্ভীর সিং সপরিবারে এখানেই অবস্থান করেন।
ইতিহাসে মণিপুরিদের কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয় ১৮১৯-১৮২৬ সাল পর্যন্ত ।
১৮২২ সালে মণিপুরি রাজ্যের সাথে বার্মার যুদ্ধ হয়।
এ যুদ্ধে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।
অসংখ্য মণিপুরি পরিবার নিজ আবাসভূমি ছেড়ে বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যায়।
তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজা চৌর্জিৎ সিংও কাছাড়ে পালিয়ে যান।
রাজ্যভার গ্রহণ করেন তার সহোদর মার্জিত সিং। এক পর্যায়ে মার্জিত সিং বার্মিজদের কাছে পরাস্থ হন। পরিশেষে চৌর্জিৎ, মার্জিত ও গম্ভীর তিন ভাই একত্রে পুনরায় চলে আসেন মির্জাজাঙ্গালের এই রাজবাড়ীতে। তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসকদের আশ্রয়ে এখানেই বসতী স্থাপন করেন। ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে সিলেটে খাসিয়াদের দমনে মণিপুরি লেভী (সৈন্যবাহিনী) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিকে, সিলেটে দীর্ঘদিন অবস্থানের সুবাদে মণিপুরিদের সাংস্কৃতিক সম্ভারের নানা দিক এ অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
যা এখনো প্রতীয়মান হয় মণিপুরি নৃত্য, গান ও পোষাক ছাড়াও সিলেটের কৃষ্টি সংস্কৃতিতে।
মণিপুরি সম্প্রদায়ের ইতিহাস-আবেগ-অনুভূতির অন্যতম স্থান মির্জাজাঙ্গালের রাজবাড়ীর সংস্কারের জন্য আজ অবধি তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। রাজা কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদের তিন চতুর্থাংশের কোনো অস্তিত্ব নেই। উপরন্তু রাজবাড়ীর সামনে অপরিকল্পিতভাবে মন্দির নির্মাণ করে রাজবাড়ীর পুরাকীর্তি ঢেকে রাখা হয়েছে।
বর্তমানে মণিপুরি ঠাকুর ও ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকজন বংশ পরম্পরায় বসবাস করছেন এ রাজবাড়ীতে। পূর্বসুরী রাজার রেখে যাওয়া নানা বস্তুকে স্বর্ণালী স্মৃতি হিসেবে ধারণ করে আছে পরিবারগুলো। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- একমণ ওজনের মন্দিরের একটি ঘন্টা যার গায়ে মণিপুরি ভাষায় লেখা আছে, ‘‘শ্রীহট্ট কুনোঙ্গী শ্রী মহা প্রভুদা শ্রীলশ্রী পঞ্চযুক্ত মণিপুরে স্বরচন্দ কীর্ত্তি সিংহ মহারাজন্য কৎখিবী সরিকনি ইতিশকাব্দা ১৮০০ তারিখ ১৮ জৈষ্ঠ্য’’।
মণিপুরি সংস্কৃতি সিলেটের সাংস্কৃতির ই একটি অংশ ।
“মহারাস লীলা “মনিপুরী সম্প্রদায়ের আড়ম্বরপূর্ন্য অনুষ্টানের অন্যতম। সম্প্রতি সিলেট নগরীর মির্জাজাঙ্গালস্থ মনিপুরী রাজবাড়ি শ্রী শ্রী মহাপ্রভূ মন্ডপে বাংলাদেশ মণিপুরী ছাত্র সমিতি(বামছাস) কেন্দ্রীয় কমিটি ও একাডেমী ফর মণিপুরী কালচার এন্ড আর্টস(এমকা), সিলেট এর উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মহারাসলীলার অংশ বিশেষ পরিবেশন ও মনিপুরী ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী একটি অংশ খুবাক ঈশৈ বা নুপী-পালা অনুষ্টিত হয়।
দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষার্থে এই সু প্রাচীন, ঐতিহাসিক রাজবাড়ির সংস্কার ও পুরাকীর্তির সংরক্ষণে অনতিবিলম্বে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে করেন সকলে ।
।( কৃতজ্ঞতায় সত্যেন দা ও সৈয়দ জাহাঙ্গীর সাদেক
NB ২য় , ৩য় ও ৪র্থ ছবি তিনটি জৈন্তা রাজবাড়ির , জৈন্তা রাজবাড়ির অংশটুকু নিয়ে অন্য পর্বে লেখার ইচ্ছা রয়েছে )
খাসিয়া উপজাতি ।
সৈয়দ শাকিল আহাদ
ছোটবেলা কুলাউড়াতে ছিলাম , এই ছোট্ট শহরটি মুলত তৎকালিন সিলেট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার অত্যান্ত্য সম্ভ্রদ্ধ এক রাস্তার একটি থানা শহর ।কুলাউড়ার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রধান এই রাস্তাটি কুলাউড়া,জুড়ি বাজার, দক্ষিণভাগ , কাঁঠালতলী পেরিয়ে বড়লেখা হয়ে সিলেট গিয়ে পৌছেছে ।
কুলাউড়াতে প্রায় প্রতিদিনই দলবেধে বাহারী পোশাক পরে ছেলেমেয়ে এক সাথে রিক্সাযোগে পানের বহর নিয়ে , পান বিক্রির জন্য গাজিপুর , কালুটি, কর্মধা প্রভৃতি পাহাড়িয়া এলাকা থেকে কুলাউড়ায় আসতো , এরাই খাসিয়া উপজাতি ।” কুবলাই “ বললে ওরা ও কুবলাই বলতো , তার মানে অদের ভাষায় “স্বাগতম “ ।তাদের সাথে একজন মুরব্বী ধরনের লোক থাকতো , উনাকে সবাই মন্ত্রী বলে সম্বোধন করতো । তাদের দলের মেয়েদের পিঠে একটি লম্বাকৃতির ঝুড়িঁতে একটি বাঁকাচাদের মত আজব ধরনের ধারালো দা থাকতো , বন্য পশু ও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমন থেকে নিজেদেরকে আত্বরক্ষার জন্য এরা এই দা সাথে রাখতো।
সিলেট জেলা ও ভারতের আসামে এই খাসিয়া জনগোষ্ঠী বাস করে।
সিলেটের খাসিয়ারা সিনতেং (Synteng) গোত্রভুক্ত জাতি। তারা কৃষিজীবী। ভাত ও মাছ তাদের প্রধান খাদ্য। তারা মাতৃপ্রধান পরিবারে বসবাস করে। তাদের মধ্যে কাঁচা সুপারি ও পান খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি। খাসিয়াদের উৎপাদিত পান বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়।
খাসিয়া (বা খাসি) বাংলাদেশে বসবাসরত একটি মাতৃতান্ত্রিক নৃগোষ্ঠি। এরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। এদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ, নাক-মুখ চেপ্টা, চোয়াল উঁচু, চোখ কালো ও ছোট টানা এবং খর্বকায়। খাসিয়ারা প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর আগে আসাম থেকে বাংলাদেশে আসে। তারা আসামে এসেছিল সম্ভবত তিববত থেকে। এক কালে এ উপজাতিরা ছিল যাযাবর। তাদের সে স্বভাব সাম্প্রতিক কালেও লক্ষণীয়। তাদের প্রধান আবাসস্থল উত্তর-পূর্ব ভারত। তবে পার্বত্য খাসিয়াদের বাসভূমি পশ্চিমে গারো পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে এরা নেমে এসেছিল চেরাপুঞ্জি ও শিলং খাসিয়া অঞ্চলে। পাহাড়-টিলা, ঝোপজঙ্গল এদের পছন্দনীয় পরিবেশ। কাঠ বা বাঁশের মঞ্চের উপর বারান্দাসহ এরা কুঁড়েঘর বানায়। বারান্দাই বৈঠক ঘর হিসেবে ব্যবহূত হয়। ইদানিং
অধুনা বাঙালিদের মতো গৃহও দালান নির্মাণ করে বসবাস করছে , এদের বসত ঘরের সঙ্গেই রন্ধনশালা এবং সন্নিকটে থাকে পালিত শূকরের খোয়াড়। খাসিয়ারা গ্রামকে পুঞ্জি বলে। অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বীয় সীমানায় ও সাংস্কৃতিক বলয়ে গ্রামগুলি পুঞ্জীভূত। জীবিকার তাগিদে দলেবলে স্থান ত্যাগ করে এরা নতুন পুঞ্জি রচনা করে।
বাংলাদেশে তাদের আদি নিবাস বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী সুনামগঞ্জ জেলায়, ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে যা সমুদ্র সমতল থেকে ৯/১০ মিটার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এককালে এখানে কয়েকটি পরগনা দখল করে কোনো খাসিয়া সর্দার একটি রাজ্যও গঠন করেছিলেন। তবে পরে তিনি বিতাড়িত হন। বর্তমানে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, ছাতক ও সদর থানায় খাসিয়ারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। খাসিয়া অঞ্চলে সিন্টেং, গারো ও লালং উপজাতিরও বসতি আছে। তবে তারা সংখ্যালঘু, খাসিয়াদের চোখে হেয়, যদিও ওরা গারো ছাড়া খাসিয়া বংশোদ্ভূত।
খোদ খাসিয়াদের মধ্যেও একাধিক গোত্র আছে, যেমন খোংতা, পলং, সুরং ইত্যাদি।
হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার সীমান্তে ৫টি, মৌলভীবাজারে ৬১টি এবং বর্তমান সিলেট জেলায় ৭টি খাসিয়া পুঞ্জি রয়েছে।
এদের অধিকাংশই সীমান্ত অঞ্চলে বাস করে। গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর এবং জোয়াই ও জৈন্তাপুরের মাঝখানে অনেক খাসিয়া বসতি রয়েছে। কুলাউড়ার চা বাগানে বহু খাসিয়া চাকরি করে। বাংলাদেশে খাসিয়া জনসংখ্যার সঠিক হিসাব নেই। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ১২,৩০০ জন খাসিয়া আছে।
কিন্তু ‘বাংলাদেশ খাসিয়া সমিতি’ তাদের সংখ্যা ৩০,০০০ বলে দাবি করে। খাসিয়াদের জন্মহার অনেক বেশি।
পুঞ্জি প্রধানকে সিয়েম বলা হয়। মেঘালয়ে কিছু পুঞ্জি প্রধানের বিচার ক্ষমতা আছে।
বাংলাদেশেও পুঞ্জি প্রধানগণই নিজেদের বিচার-আচার করে থাকে। এদের মন্ত্রী বলা হয়।
এরা বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক। বর্গাদার এদের জমিতে বাগবাগিচা তৈরি ও চাষাবাদের কাজ করে। বর্গাদার ঠিকমতো চাষাবাদ করছে কিনা, তা তদারকের জন্য বেতনভোগী কর্মচারী আছে। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদি মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে উদযাপিত হয়। স্বজাতিবোধ এদের মধ্যে প্রবল। খাসিয়ারা এককালে পার্বত্য জাতি ছিল। মুগল আমলের পূর্ব থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত পার্বত্য খাসিয়ারা নিম্নাঞ্চল আক্রমণ করে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকান্ড চালাত।
এরা ১৭৪৪-এ এক সামন্ত রাজার রাজধানী লাউড় পুড়িয়ে দিয়েছিল। মুগলরা খাসিয়াদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সীমান্ত পরগনাগুলিতে সৈন্য মোতায়েন করেছিল। ইংরেজকেও তাই করতে হয়। সীমান্ত পাহাড়গুলি চুনাপাথরের ভান্ডার।
চুনাপাথরের ব্যবসা নিয়ে ১৭৭৪-১৭৯৫ পর্যন্ত অহরহ সংঘাত ঘটেছে। ঐসব পাহাড় ছিল খাসিয়া সর্দারদের নিয়ন্ত্রণে। ১৭৮৭ সালে খাসিয়ারা পাঁচটি পরগনা আক্রমণ করে প্রায় ৩০০ লোক হত্যা করে। বিষাক্ত তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি এদের শিকার ও যুদ্ধাস্ত্র।
তাদেরকে দমন করতে ইংরেজদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে।
স্থানীয় জমিদারের সঙ্গেও খাসিয়াদের সংঘর্ষ বাঁধত। জমিওয়ালা স্বল্পসংখ্যক লোকই জুমচাষ ও বাগবাগিচা করে। অনেকেরই জমিজমা নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে কলা, আনারস, কমলা, তেজপাতা, গোলমরিচ, পান ইত্যাদি উৎপাদনে তারা অভ্যস্ত।
চা বাগানের কাজ ছাড়াও বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত এলাকার এপার ওপারে এরা অবাধে পান, কমলা, মাছ, চাল ইত্যাদির ব্যবসা করে। খাসিয়াদের সীমান্ত ব্যবসা সুদূর অতীত থেকে শুরু এবং আজও তা অব্যাহত। এপার ওপার সীমান্ত ব্যবসা ও বেচাকেনার জন্য নির্দিষ্ট বাজার রয়েছে। খাসিয়া মহিলারা সেসব বাজারে মালামাল আনা নেওয়া ও বেচা-কেনা করে। এদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ ব্যবসায়ীরা পুঞ্জি থেকেই কিনে নিয়ে যায়। মহিলারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য পাহাড় থেকে স্থানীয় হাটবাজারে নেমে আসে। ভাত ও মাছ এদের প্রধান খাদ্য।
খাসিয়া যুদ্ধ নৃত্য ,খাসিয়া ধর্ম অতি প্রাচীন, কিন্তু কালে কালে বিবর্তিত। প্রথা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসই এদের ধর্ম। খাসিয়াদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। খাসিয়া সম্প্রদায়ের পরিবর্তনটা তাদের ধর্মেই বেশি ঘটেছে। দেড় শতাধিক বছর পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারিরা খাসিয়াদের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিল।
বর্তমানে ৮০%-৯০% খাসিয়াই খ্রিস্টান। প্রায় প্রতি পুঞ্জিতেই গির্জা আছে। প্রতি রোববারে খ্রিস্টান খাসিয়ারা গির্জায় প্রার্থনা এবং পুঞ্জির বিষয়াদি নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে।
খ্রিস্টান যাজকগণ অনেক সময় পুঞ্জির বিচার-আচারেরও দায়িত্ব পালন করেন। খাসিয়ারা গোড়া থেকেই একেশ্বরবাদী। তাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টির পর পৃথিবীতে একজোড়া নর-নারী সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর, বিশ্বের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি দেব-দেবী সৃষ্টি করেন। গ্রাম-দেবতাতেও এরা বিশ্বাসী। তাছাড়া, এরা প্রেতবাদী, সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতি-পূজারী। এরা কোনো কোনো জীবজন্তু পূজাও করে থাকে। এ ছাড়াও তারা অনেক প্রকার ধর্মীয় ব্রত-পার্বণাদি পালন করে। এদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। খাসিয়া ভাষাও অনক্ষর ও অলিখিত। কিংবদন্তি আছে, এক সময়ে তাদের লিখিত ধর্মশাস্ত্র ছিল, দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায়। এরা দ্বিভাষী, খাসিয়া ও কিছু বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় অনর্গল বাক্যালাপ করতে পারে।
এক সময়ে, খাসিয়া ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হতো। বাইবেলের কিছু অংশ প্রথমে খাসিয়া ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা অক্ষরে লেখা হয়েছিল। শিক্ষিত খাসিয়ারা নিজেদের মধ্যে আজও বাংলা অক্ষরে খাসিয়া ভাষায় চিঠিপত্র লেখালেখি করে থাকে।
বর্তমানে সীমান্তের ওপারে ভারতে খাসিয়া ভাষা রোমান হরফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
বাংলাদেশে খাসিয়া ভাষার কোনো সর্বজনীন রূপ নেই।
সম্প্রতি কিছু খাসিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষার ফলে খাসিয়াদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটাই বদলে গেছে।
খ্রিস্টান খাসিয়ারা প্রোটেস্টান্ট।
এরা শব দাহ করে কিন্তু হাড়গুলি কবর দেয়। মৃতের সৎকারের সময় খাসিয়া ধর্মগুরু প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করে, যার বঙ্গানুবাদ, ‘বিদায়, বিদায়, বিধাতার রাজ্যে গিয়ে তুমি পান খাবে’।
বর্তমানে এদের ধর্মানুভূতি, সংস্কার, পোশাক ও আচরণে আধুনিক ছাপ লক্ষিত হয়।
এদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে শিরে চূড়াবাঁধা পাগড়ি পরিধান করা। আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে ঐতিহ্য-এর প্রতি অনুরাগ লক্ষণীয়। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য তারা বিভিন্ন নামে সারা বছরই ব্রত ও পর্ব-পার্বণ পালন করে। ফসল বপনের সময় খিয়াখাং ব্রত পালন করে। অন্যান্য ব্রত হচ্ছে খিয়া পিস্থল, পিরদোং স্ট্রোং, খিয়া ক্লাম ইত্যাদি। বিবাহ খাসিয়াদের নিকট একটি ‘ফরজ’ কাজ।
তাদের ধারণায় এটি ভগবানের নির্দেশ এবং বিয়ে না করা পাপ, অন্যথায় অভিশপ্ত হতে হয়।
এদের অনুষ্ঠানাদি বেশ জমজমাট। বিবাহ ও নানারকম সাংবাৎসরিক উৎসবে ওরা দলবদ্ধ হয়ে নৃত্যগীত করে থাকে।
জন্ম-মৃত্যুর অনুষ্ঠানাদিও এভাবে পালন করে। তাদের নাচ-গান দৃষ্টিনন্দন।
খাসিয়া প্রবাদ মতে, নারী থেকেই সভ্যতার সূচনা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দরুন মেয়েরা অন্য গোত্রের পছন্দসই কোনো যুবককে বিয়ে করে ঘরজামাই করে রাখে। স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ।
স্বগোত্রে কোনো ছেলে-মেয়ে বিয়ে করলে তারা সম্পত্তির অধিকার হারায়, গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং মৃত্যুর পর এদের কবর দেওয়া হয় না। অধিকাংশ বিবাহই হয় মেয়েদের অগ্রভূমিকায় পূর্বানুরাগের ভিত্তিতে। মেয়েটি ভালবাসার পাত্রকে স্বগৃহে দাওয়াত করে। কখনও কখনও ২/৪ দিন একসঙ্গে বসবাস করে। উভয়ের মধ্যে অনুকূল মত বিনিময়ের পর অভিভাবককে জানানো হয়। উভয়পক্ষের বৈঠকে বিবাহ দিবস স্থির হয়।
পুরুষ বরযাত্রীরা বরকে সাদা ধুতি, চাদর, পাগড়ি পরিয়ে কনের বাড়িতে রওনা হয়। যাওয়ার সময় মাতৃস্থানীয় নারীরা ছেলেকে আশীর্বাদ করে। কনে পক্ষ, অগ্রগামী হয়ে এদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়। খাসিয়া ধর্মগুরুর মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং নবদম্পতিকে ‘ধনে-জনে অদৈন্য’ প্রার্থনা করে, তারপর সুস্বাদু আহার পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং বরকে রেখে মধ্যরাতে বরযাত্রী বিদায় নেয়।
এ সময় দেবতাকেও মদ ও শুঁটকি মাছ দিয়ে ‘ভোগ’ দেওয়া হয়। কনের ভাইবোনরা বরের আপন ভাইবোনের মতো বিবেচিত। পূর্বানুরাগ ছাড়াও, অভিভাবকদের আলোচনায় বিয়ে হয়ে থাকে। বিয়ের পর কন্যার মাতৃগৃহের পাশেই নবদম্পতির জন্য নতুন কুঁড়েঘর তৈরি করে দেওয়া হয়।
তা সম্ভবপর না হলে মাতৃগৃহের পাশেই তারা বাস করে। কোনো কোনো পুঞ্জিতে তা বাধ্যতামূলক। কনিষ্ঠ কন্যার জন্য আলাদা ঘর নির্মাণ করা হয় না।
কারণ সে মাতৃগৃহ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। সংসারে টাকা পয়সার লেনদেন হয় স্ত্রীর হাত দিয়ে।
খাসিয়া সমাজে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে কৃষি ও সংসারের কাজকর্ম করে। এদের মধ্যে মতান্তর কমই দেখা যায়। পুরুষরা নারীদের সমীহ করে। বিপত্নীক বৃদ্ধ পিতার লালন-পালনের ধর্মীয় দায়িত্ব সন্তানদের। স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হলে তারা মাতৃনামেই পরিচিত হয়। পুরুষটি অন্যত্র বিবাহ করে চলে যেতে পারে। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও খাসিয়ারা মাতৃনাম পরিত্যাগ করে না। সম্পত্তির মালিক কনিষ্ঠ কন্যা কিন্তু অন্য বোনরাও ভাগ পায়, তবে তাদের সম্পত্তি বিক্রয় করার অধিকার নেই। পারিবারিক পূজা-অর্চনা ও অনুষ্ঠানাদির দায়িত্ব ছোট বোনের উপর অর্পিত। এক বিবাহই খাসিয়াদের রেওয়াজ। তবে স্বামীর অক্ষমতা, স্বামী পছন্দ না হওয়া কিংবা মিলনের জন্যও স্ত্রীরা একাধিক বিবাহ করতে পারে। পুরুষদের বহু বিবাহ বিরল। তবে স্ত্রীর সন্তান না হলে তার অনুমতিক্রমে পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। বিভিন্ন পুঞ্জিতে তাদের বিবাহ প্রক্রিয়ায় ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কিছু পার্থক্য আছে। বিবাহের পর যদি দম্পতি আলাদা খানায় থাকে, তবে তাদের আয়ও হয় নিজস্ব। এতে মায়ের অধিকার থাকে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা, অসততা, স্বামীর অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে উভয়ের তালাক দেওয়ার অধিকার আছে। তালাকের পূর্বে উভয়কে কিংবা যে কোনো একজনকে তাদের তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পুঞ্জির মাতববর এবং বিবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জানাতে হয়। তারা স্থির চিত্তে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য দম্পতিকে একটা নির্দিষ্ট সময় দেয়। তারপরও যদি মত পরিবর্তন না হয়, তবে বৈঠকে বিবাহ ভেঙ্গে গেল বলে ঘোষণা দেয় এবং পুঞ্জিতে ঢোল পিটিয়ে তা প্রচার করা হয়। তালাক যদি একতরফা হয়, তবে স্ত্রীর বেলায় আট আনা ক্ষতিপূরণ ও পুরুষের বেলায় পরিত্যক্ত স্ত্রীকে দু প্রস্থ কাপড় দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালাক সংঘটিত হয় স্ত্রীদের দ্বারা। সামান্য কারণেও অনেক সময় তালাক হয়ে যায়। তালাকের পর ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গেই থাকে। তালাকের পর আবার এরা অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তালাক অসিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পর স্ত্রী পুনর্বিবাহ করতে পারে। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে খাসিয়া সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও ক্রমশ শিথিল হচ্ছে।
।আমার দেখায় কুলাউড়া ছাড়াও আশে পাশের অনেক পাহাড়ীয়া এলাকায় খাসিয়াদের অবস্তান উল্লেখযোগ্য যেমন শ্রীমংগল সংলগ্ন মাগুরছড়া পুঞ্জি
খাসিয়ারা বলে মাগুরসরা পুঞ্জি, পুঞ্জি হচ্ছে খাসি ভাষায় গ্রাম ।বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। এখানে মূলত খাসি জনগোষ্ঠীর বাস।
গ্রামটি সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার কমলগঞ্জ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডভুক্ত। শ্রীমঙ্গল–কমলগঞ্জ সড়কের পাশে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত।
২০০৬ সালের হিসাব অনুসারে মাগুরছড়া পুঞ্জিতে প্রায় ৪০টি গৃহ ছিল। বর্তমানে তা শতাধিক পেরিয়েছে ।
লাউয়াছড়া উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত দুইটি পুঞ্জির মধ্যে লাউয়াছড়া পুঞ্জি ও মাগুরছড়া পুন্জি এর মধ্যে মাগুরছড়া পুন্জিই বৃহত্তম।
গ্রামে প্রায় ১৫৫ জন লোক বাস করে।কুলাউড়া সংলগ্ন প্রকৃতির এক অনিন্দ রুপে সজ্জিত অপরূপ পাহাড়ে বেস্টিত স্হান “ মাধবকুন্ড জলপ্রপাত “ এলাকা , এই এলাকায় মাধবকুন্ড ঝরনার পাশ্বেও রয়েছে ছোট বড় বেশ কয়েকটি খাসিয়া পুন্জি । মোটকথা বৃহত্তর সিলেট বিভাগের পাহাড়ীয়া এলাকায় কমবেশি অনেক খাসিয়া পুন্জি রয়েছে ।
আমাদের সমাজের সর্বস্তরের জনগন ও এলাকাবাসীদের কে সর্বত্রই এই খাসিয়া উপজাতি দের সম্মান ও সমীহ করতে দেখা যায় ।
উল্লেখ্য যে আমার নানার বাবা কুলাউড়ার সন্তান খান বাহাদুর মৌলবী আমজদ আলী ছিলেন খাসিয়া ভাষায় কবিও
এবং খাসিয়া ভাষায় অভিধানের লেখক ।
লেখাটি তৈরীতে তথ্য দিয়ে
সহযোগীতা করেছেন অনেকেই , এজন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই সত্যেন দা, জয়ন্ত আচার্য্য , সৈয়দ আব্দুল হাকাম এবং বাংলাপিডিয়াকে ।
গল্ফ ।
সৈয়দ শাকিল আহাদ
আজ একটি খেলা নিয়ে আলোচনা করবো , ইদানিং এই খেলাটি জনপ্রিয়তা লাভ করছে ধীরে ধীরে , হ্যা , খেলাটির নাম “গল্ফ “বর্তমানে গলফ বিশ্বব্যাপী খুব জনপ্রিয় একটি খেলা।
এটি সব বয়সী লোকেরা খেলতে পারে। পরিচ্ছন্ন এই খেলাটি পরিবারের সকলকে নিয়ে খেলা যায় , যদিও তা একটু ব্যয় বহুল
এই খেলা স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এই লেখায় আমরা গলফের নানান স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে জানবো।
একটি স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মানুষের। আর এটি অর্জনে রয়েছে বিভিন্ন উপায়। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে খেলাধুলা। মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য কারী “গলফ”স্ট্রেস কমানোর একটি দুর্দান্ত উপায়। গলফ খেললে মস্তিষ্ক থেকে শক্তিশালী প্রাকৃতিক, মেজাজ বাড়ানোর হরমোন নিসৃত হয়, যাকে বলা হয় এন্ডরফিন।
এটি চাপ কমাতে বেশ উপকারী। বিশেষ করে যারা বয়স্ক তাদের মানসিক চাপ দূর করতে বেশ সাহায্য করে গলফ।
কেননা বার্ধক্যের সঙ্গে মানসিক সতর্কতা আরও দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। গলফ খেলা তাদের একাগ্রতা শক্তি এবং মানসিক তীক্ষ্ণতা অনুশীলনে সহায়তা করে। এটি তাদের মানসিক অসুস্থতা যেমন ডিমেনশিয়াকে দূরে রাখে।
গল্ফের উদ্ভব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। কোনো ঐতিহাসিকে মতে প্রাচীন রোমান খেলা পাগানিকা, যাতে অংশগ্রহণকারীরা একটি বেঁকানো লাঠি দিয়ে চামড়ার বল মারতে হত, সেখান থেকে গল্ফের উদ্ভব। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমানদের সাথে এই খেলা গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ও আস্তে আস্তে আজকের গল্ফের চেহারায় রুপ নেয়।
অন্যদের মতে, অষ্টম ও চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে চীনের চুইওয়ান “থেকে ই এই খেলার সুত্রপাত “ চুই” মানে মারা ও “ওয়ান” মানে ছোট বল , সেই খেলাই গল্ফের পূর্বসূরি।
মধ্যযুগে এই খেলা ইউরোপে আসে। ইংল্যান্ডের ক্যাম্বুকা বা ফ্রান্সের ক্যাম্বট আর একটি প্রাচীন খেলা যার সাথে গল্ফের সাযুজ্য আছে।
পরে এই খেলা “পেল মেল” নামে ছড়িয়ে পড়ে। কারো কারো মতে পারস্যের চুঘান থেকে গল্ফের সৃষ্টি। ওদিকে হল্যান্ডের লোনেনে পঞ্চম ফ্লোরিসের খুনির ধরা পড়ার দিনটি মনে রাখতে কোলভেন নামে বাঁকা লাঠি ও বলের একটি বার্ষিক খেলা প্রচলিত ছিল ১২৯৭ সাল থেকে সেই খেলাটির ই আধুনিক রূপ হচ্ছে গল্ফ ।
তবে বহুল স্বীকৃত মত অনুযায়ী, আজকের গল্ফের উদ্ভব দ্বাদশ শতাব্দীতে স্কটল্যান্ডে।
সেখানে আজকের সেন্ট অ্যান্ড্রূজের পুরোনো মাঠে মেষপালকেরা খরগোশের গর্তে পাথর লাঠি দিয়ে মেরে ঢোকাতো।
গল্ফ একটি ইংরেজি শব্দ ( Golf)ক্লাব ও বলের একটি খেলা, যাতে খেলোয়াড়েরা ক্লাবের সাহায্যে বলটিকে নির্দিষ্ট গর্তে (hole ) এ ফেলার চেষ্টা করেন। গল্ফ খেলোয়াড়দের বলা হয় গল্ফার।
আর দশটি বলের খেলার মত গলফ মাঠের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে না। গল্ফ খেলা হয় খোলা মাঠে, যাকে গল্ফকোর্স বলা হয়। একটি গলফ কোর্সে সাধারণত
৯ থেকে ১৮ টি গর্ত থাকে। প্রতিটি গর্তের জন্য একটি করে টি বক্স থাকে, যেখান থেকে খেলা শুরু হয়।
সুনির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ১৮টি গর্তে খেলে একটি গল্ফ খেলা সম্পূর্ণ হয়। যে গল্ফক্ষেত্রে ৯টি গর্ত আছে সেখানে দুবার খেলা হয়।
একটি গর্তের জন্য খেলা শুরু হয় টি-এলাকা থেকে গল্ফদন্ড দিয়ে বল মেরে। এই বল মারার সময় যদি বল অনেক দুরে মারতে হয় তখন অনেক সময় বলটি টি-এর উপর রাখা হয়।
গল্ফের একটি খেলা একক এবং দলগত দুই রকমই হতে পারে। একক খেলায় যে খেলোয়াড় সবচেয়ে কম সংখ্যক আঘাতে বা stroke এ সকল গর্ত জয় করতে পারেন, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এটিকে বলা হয় স্ট্রোক প্লে (stroke play)।
অপরদিকে দলগত খেলাকে বলা হয় ম্যাচ প্লে (match play)
যাতে সবচেয়ে বেশি গর্ত জয় করা দল বিজয়ী ঘোষিত হয়।
সুনির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ১৮টি গর্তে খেলে একটি গল্ফ খেলা সম্পূর্ণ হয়। যে গল্ফক্ষেত্রে ৯টি গর্ত আছে সেখানে দুবার খেলা হয়। একটি গর্তের জন্য খেলা শুরু হয় টি-এলাকা থেকে গল্ফদন্ড দিয়ে বল মেরে। এই বল মারার সময় যদি বল অনেক দুরে মারতে হয় তখন অনেক সময় বলটি টি-এর উপর রাখা হয়। এই টি আসলে মোটা পেরেকের মত দেখতে, যা সাধারণতঃ কাঠের তৈরি হয়। অনেক সময় কিছুটা ঘাস বা ধুলো জড়ো করেও বল উঁচু করা হয়, মারার সুবিধার্থে।
দুরের বল মারার জন্য লম্বা আর কাছে মারার জন্য সাধারণত ছোট দন্ডের ব্যবহার হয়। গল্ফার বলটি গর্তে ফেলার জন্য বল থামার পর যতবার খুশি মারতে পারেন। এই ধরনের মারগুলিকে লেআপ (lay-up), অ্যাপ্রোচ (approach), পিচ বা চিপ (chip) বলে।
বল সবুজ অঞ্চলে পৌঁছাবার পরের মারকে বলে পাট। গল্ফারের মূল লক্ষ্য থাকে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে যথাসম্ভব কমবার মেরে বল গর্তে ফেলা।
খেলোয়াড়েরা হেঁটে বা স্বয়ংক্রিয় যানে চেপে মাঠে চলাচল করতে পারেন। একক বা দলবদ্ধভাবে বা ক্যাডির সাথে খেলা যায়। ক্যাডি, গল্ফারের সরঞ্জামের দেখভাল করা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট গল্ফারকে খেলা নিয়ে নানান উপদেশ দিতে পারেন।.
গল্ফের নিয়মকানুন নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে ,
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয় R&A ও United States Golf Association (USGA)।
সাধারণভাবে গল্ফ খেলায় সততাই মূলধন।
সরকারি নিয়মাবলীর পিছনের পাতায় যা লেখা আছে তা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, “বল যে ভাবে পড়ে আছে সে ভাবে খেলুন, মাঠের গঠন অনুযায়ী খেলুন আর যদি তা না পারেন তো অন্ততঃ সৎভাবে খেলুন।”
একজন গল্ফারের পেশাদারিত্বের নিয়ম ভীষণ কড়া।যদি কোনো ব্যক্তি কখনো খেলা শেখানোর জন্য বা গল্ফ খেলার জন্য অর্থগ্রহণ করেছে তাহলে সেই ব্যক্তিকে পেশাদার বিবেচনা করা হবে ও তিনি আর কোনো অপেশাদার খেলায় অংশ নিতে পারবেন না। অপেশাদার গল্ফারেরা কখন কত মূল্যের পুরস্কার পাবেন তার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে।
ছাপার অক্ষরের গল্ফের নিয়মাবলী ছাড়াও গল্ফারেরা আরও কিছু অলিখিত নিয়ম মেনে চলেন, যাকে গল্ফ এটিকেট বলে। এই নিয়মগুলি সাধারণতঃ নিরাপত্তা, সততা, খেলার গতি বা মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত।
এই নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক না হলেও বৃহত্তর স্বার্থে সব গল্ফার এই নিয়ম গুলি মেনে চলেন।
পেনাল্টি কি ? জানা দরকার ।
গল্ফ খেলায় পেনাল্টি মানে একজন খেলোয়াড়ের বল মারার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া।
বল হারিয়ে ফেললে বা মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলে একটি মার ও দুরত্বের পেনাল্টি হয়
যা গল্ফ আইনের ধারা ২৭-১ ।
যদি খেলোয়াড়ের সরঞ্জাম বা আলগা ঘাস সরাতে গিয়ে বল সরে যায় তাহলে একটি মার পেনাল্টি হয় (ধারা ১৮-২)।
যদি ভুল বল মারা হয় (ধারা ১৯-২)
বা অন্য গল্ফারের বল মারা হয় (ধারা ১৯-৫)
তাহলে আবার দুটি মার পেনাল্টি হয়। এছাড়া অসৎপন্থার জন্য খেলা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত হতে পারে।
গল্ফ বল মারার জন্য গল্ফ দন্ড লাগে। প্রতিটি দন্ডের এক প্রান্তে ধরার জন্য হাতল থাকে।
আর অন্য প্রান্তে মারার জন্য মাথা থাকে। লম্বা দন্ডের ক্ষেত্রে মাথা দন্ডের সাথে প্রায় সমকোণে থাকে। ছোট দন্ডের ক্ষেত্রে এই কোণ কিছু বেশি হয়।
ড্রাইভার দন্ডটি সবচেয়ে বড়।
এর থেকে একটু ছোট হল উড। ফেয়ারওয়েতে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
মজার ব্যপার হল, আজকাল উড তৈরি হয় ধাতু দিয়ে।
তাই আজকাল একে ফেয়ারওয়ে মেটাল-ও বলে। এর থেকেও ছোট মাপের দন্ডকে বলে আয়রন।
এর রকমফের সবচেয়ে বেশি। হাইব্রিড দন্ডগুলি আবার উডস ও আয়রনের উভয়েরই গুণ সংবলিত হয়। তাই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে। পাটার দন্ডগুলি ব্যবহৃত হয় সবুজ অঞ্চলে বল মেরে গর্তে ফেলার জন্য।
একজন খেলোয়াড় অনধিক ১৪টি দন্ড একটি খেলায় ব্যবহার করতে পারে। দন্ডের পছন্দ খেলোয়াড়ের হলেও সেগুলি নিয়মানুসারে নির্মিত হতে হয়।
নচেৎ খেলা থেকে বহিষ্কারের সম্ভাবনা থাকে।
গল্ফ বলের আকার গোলাকার, সাধারণতঃ সাদা (যদিও অন্যান্য রঙেরও হয়) এবং গায়ে অনেক ছোট ছোট টোলের মত গর্ত থাকে, যে গুলি বাতাসে ঘর্ষণ কমাতে সাহায্য করে যাতে বল উড়ে বেশিদুর যেতে পারে।
বলটিকে টি শুধুমাত্র টি-এলাকা থেকে প্রথমবার মারার জন্য ব্যবহার হয়।
অনেক গল্ফার গল্ফের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি গল্ফ জুতা ব্যবহার করেন।
এই জুতার তলায় ধাতু বা প্লাস্টিকের তৈরি কাঁটা থাকে যা পা’কে ঠিক জায়গায় রেখে নিখুঁত ভাবে বল মারতে সাহায্য করে। মাঠে গল্ফ দন্ড বহন করার জন্য গল্ফ ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। এতে অনেক পকেট থাকে যেখানে টি, বল বা দস্তানা রাখা যায়।
এই ব্যাগ দুচাকার ঠেলা গাড়িতে বহন করা যায় বা গল্ফকার্টেও বহন করা যায়। এই ব্যাগ হাতে বা কাঁধেও ঝোলানো যায়। আবার কখনো প্রয়োজন হলে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য পায়াও আছে।
একটি গল্ফ ক্ষেত্র আসলে অনেকগুলি পরপর গর্ত ও টি-এলাকার সমাহার।
আর এই গর্ত ও টি-এর মাঝে থাকে ফেয়ারওয়ে বা ভালপথ, রাফ বা জঙ্গল, হ্যাজার্ডস বা প্রতিবন্ধকতা আর পাটিং গ্রিন বা সবুজ যা কিনা পতাকা দন্ড দেওয়া গর্তের চারদিকে থাকে। গোটা ক্ষেত্রে ঘাসের উচ্চতার তারতম্য খেলোয়াড়ের দক্ষতার পরীক্ষা নেয়। অনেক সময় টি এলাকা থেকেই গর্ত সরাসরি দেখা যায়।
আবার অনেক সময় ক্ষেত্রের নকশা এমন ভাবে করা হয় যে কুকুরের হাঁটুর মত গর্ত টি এলাকা থেকে ডান দিকে বা বাম দিকে বেঁকে থাকে।
কখনো কখনো এই বাঁক দুবার থাকে, যাকে বলে, “double dogleg”।
সাধারণতঃ গল্ফ ক্ষেত্রে ১৮টি গর্ত থাকে। তাই ৯ গর্তের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়কে দুবার পাক দিতে হয়।
শুরুরদিকের স্কটিশ ক্ষেত্রগুলির মাঝে বালিয়াড়ি বা ঘাস ছাড়া ন্যাড়া জমি থাকত।
সেই ধারাতেই আজকের গল্ফ ক্ষেত্রগুলি নির্মিত।
ডানহাতি বা বাঁহাতি খেলোয়াড় লক্ষ্যের যথাক্রমে বাঁদিক বা ডানদিক ফিরে এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে শরীর ও দন্ড লক্ষ্যরেখার সমান্তরাল হয়। পা সাধারণতঃ কাঁধের সমান দুরত্বে ফাঁক থাকে যদি মাঝারি দৈর্ঘ্যের আয়রন বা পাটার ব্যবহৃত হয়।
আর যদি ছোট দৈর্ঘ্যের আয়রন ব্যবহৃত হয় তাহলে পায়ের ফাঁক কম এবং লম্বা দৈর্ঘ্যের আয়রন ও উডের ক্ষেত্রে আরও বেশি হয়। ছোট আয়রন ও পাটারের ক্ষেত্রে বলের অবস্থান খেলোয়াড়ের দাঁড়ানোর ভঙ্গির মাঝে হয় এবং ক্রমশঃ সামনের দিকে যেতে থাকে যত দন্ডের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। লক্ষ্যের দুরত্বের ওপর নির্ভর করে গল্ফার দন্ড কি ভাবে ধরবে, বা কি দন্ড ব্যবহার করবে, বা কত জোরে মারবে।
ড্রাইভ ব্যবহার হয় টি-ক্ষেত্র থেকে লম্বা দূরত্বে মারার ক্ষেত্রে।
অ্যাপ্রোচ ব্যবহার হয় লম্বা থেকে মাঝারি পাল্লার মারের ক্ষেত্রে।
চিপ ব্যবহৃত হয় তুলনামূলক ছোট দূরত্বে সবুজের চারপাশে মারার জন্য, যাতে বল সবুজে এসে পড়ে ও যথাসম্ভব গর্তের কাছে যায়।
পাট খুব ছোট দূরত্বে সবুজের উপরে মারার জন্য, যাতে বল গর্তে পড়ে।
পারের হিসাবে গর্তের শ্রেণীবিভাগ হয়। পার মানে কতবার মেরে একজন দক্ষ গল্ফার টি থেকে গর্তে বল ফেলতে পারে তার হিসাব।
যেমন একটি পার-চার গর্তে একজন খেলোয়াড়ের দুবার মেরে সবুজে পৌঁছানো উচিত (একে Green in Regulation বা GIR বলে)।
একবার টি থেকে “ড্রাইভ” মেরে আর একবার, “অ্যাপ্রোচ” মেরে সবুজে ও সবশেষে দুবার “পাট” মেরে গর্তে। গল্ফের গর্ত পার-তিন, -চার, -পাঁচ, কখনো কখনো -ছয় ও কদাচিৎ -সাতের হয়।
আসলে টি থেকে গর্তের দূরত্বই পার এর সংখ্যা ঠিক করে। সাধারণতঃ পার-তিনের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ২৫০গজ (২২৫মিটার), পার-চারের ক্ষেত্রে এটাই ২৫১ থেকে ৪৭৫গজ (২২৫-৪৩৪মিটার), আবার পার-পাঁচের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ৪৭৫গজের(৪৩৫মিটার) বেশি।
সচরাচর যদিও পার-ছয় ও -সাত দেখা যায় না; তবে তাদের দৈর্ঘ্য বিরাট – ৬৫০গজেরও বেশি হয়। গল্ফক্ষেত্রের ঢালের (চড়াই না উৎরাই) উপরেও পার সংখ্যা নির্ভর করে। যদি টি থেকে সবুজের পথ মূলতঃ উৎরাই হয় তবে পার সংখ্যা কম হবে, যদিও দূরত্ব অনুযায়ী পার সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত।
আবার উল্টোটাও সত্যি। এছাড়া পার সংখ্যা টি থেকে সবুজের মাঝে বাধা-বিপত্তির উপরেও নির্ভর করে। কারণ বাধা বেশি হলে বল বেশিবার মারতে হবে সেই বাধা কাটানোর জন্য।
১৮গর্তের গল্ফক্ষেত্রে চারটি পার-তিন, দশটি পার-চার ও চারটি পার-পাঁচ গর্ত থাকতে পারে। তবে এই বিভাজন অন্য রকমও হতে পারে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা খেলা হয় ৭০,৭১ বা ৭২ পারের ক্ষেত্রে।
কোনো কোনো দেশে আবার গল্ফক্ষেত্রের বিভাজন নির্ভর করে সেখানে খেলা কতটা কঠিন তার ওপর।
যাকে গল্ফারের সেই গল্ফক্ষেত্রে খেলার প্রতিবন্ধকতা বা হ্যান্ডিক্যাপ বলে।
স্কোরিং
সম্পাদনা
সব ধরনের গল্ফ খেলার মূল উদ্দেশ্য হল যথাসম্ভব কমবার বল মারা। “হোল ইন ওয়ান” বা “এস” হল যখন একজন গল্ফার টি থেকে বল মেরে একবারে গর্তে ফেলে। বিভিন্ন স্কোরের বিভিন্ন প্রতিশব্দ আছে।
সংখ্যাগত প্রতিশব্দ
কথ্য প্রতিশব্দ সংজ্ঞা
−৪ কন্ডর পারের চেয়ে চারটি মার কম
−৩ অ্যালবাট্রাস পারের চেয়ে তিনটি মার কম
−২ ঈগল পারের চেয়ে দুটি মার কম
−১ বার্ডি পারের চেয়ে একটি মার কম
E পার পারের সমান
+১ বোগী পারের থেকে একটি মার বেশি
+২ ডাবল বোগী পারের থেকে দুটি মার বেশি
+৩ ট্রিপল বোগী পারের থেকে তিনটি মার বেশি
+৪ কোয়াড্রুপল বোগী পারের থেকে চারটি মার বেশি
গল্ফ নিয়ে অনেক বিস্তর আলোচনা চলতে পারে তবে আমাদের যাদের সামর্থ রয়েছে তাদের উচিত নিজেকে ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে গল্ফ কে উপভোগ করা ।
(প্রতিবেদন তৈরীতে তথ্য সহযোগীতা ও কৃতজ্ঞতায় মেজর নুরুল মান্নান চৌধুরী (অবঃ) এবং উইকিপিডিয়া)
৭১ এর স্মৃতি- পর্ব ৩৭ (কুলাউড়া -২ )
আমি অতি সাধারন একজন লেখক , স্মৃতির সাগর থেকে তুলে এনে কিছু কথা , আনন্দ , বেদনা লিখে যাচ্ছি ।
ছোটবেলায় কখনই ভাবিনি বড় হয়ে সেই ছোটবেলার কথা লিখে নিজেকে লেখক হিসাবে আবিষ্কার করবো । করোনা কালিন সময়ে হটাৎ মনে হলো কিছু লিখি , শুরু করে দিলাম , তখন বেশ কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছিলাম যা বিভিন্ন স্থানে , পেইজে প্রকাশ করার পর লোকনাট্যদলের আজাদ রহমান নামের আমার প্রিয় এক ছোট ভাইের পক্ষ থেকে “ বিশ শব্দের গল্প “ নামক একটি গ্রুপে গল্প লেখার দাওয়াত পাই , এবং সেই দাওয়াত মোতাবেক ঐ গ্রুপে গল্প লেখা শুরু করি , সেখানেও ৭০০ এর উপর “ বিশ শব্দের গল্প” লিখেছি যার ভিতর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পাঁচশোরও বেশি গল্প রয়েছে । এত গল্প লিখেছি শুনে একদিন এক কবি বন্ধু , চৌধুরী নুরুল হুদা কিছুটা ভৎসর্না ছলে বললো “ বিশ শব্দে কি আবার কোন গল্প হয় ? সে অনুরোধ করলো বড় করে যা খুশি লিখতে , তা যেভাবেই হোক , সেটা বা সেই গল্প যেন ২০০০-২২০০ শব্দে হয় ।তার পর থেকেই চেষ্টা অব্যাহত আছে এবং আমরার “সিলোটি আড্ডা নামক “ একটি ফেইসবুক গ্রুপে বড় বড় লেখা লিখতে শুরু করলাম , লেখাগুলো একটু বড় হচ্ছে বলে কোন কোন পাঠকের অসন্তুষ্টি যে হয় না , তা কিন্তু নয় তবে অধিকাংশ পাঠকেরাই বড় লেখা পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন এবং মন্তব্য ও করেছেন “ তোমার লেখা তো অনেক বড় হয় , আমরা তো পড়তেই ধৈর্য্যহারা হয়ে উঠি , তুমি এত বড় বড় পর্ব বড়লেখার ধৈর্য্য পাও কৈ ?
আমি নিজেও জানি না কি করে পাই আমি এত বড় বড় লেখার ধৈর্য্য !!তবে এটা ঠিক লিখতে লিখতে কোন এক সময় একটা কিছু হয়ে যায় , যার জন্য
শুকরিয়া জানাই মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট , তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন ।তাইতো ভুলতে পারি না ছোটবেলার সেই মধুর দিন গুলোর কথা ।
যাই বলেন না কেন “ ছোটবেলার সেই দিনগুলো কি সহজে ভোলা যায় ?
আবারও মনে পড়ছে কুলাউড়ার কথা , ১৯৭১ সালে এই কুলাউড়া গার্লস স্কুলে পাকিরা ক্যাম্প করেছিল , তখন আঁশে পাশের বাড়ী ঘর গুলোতে যারা সাহস করে রয়ে গেছিল তাদের মধ্যে আমাদের নানা বাড়ী অর্থাৎ উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ী উল্লেখযোগ্য , আঁশে পাশের অনেক পরিবারই তখন আস্রয় নিয়েছিল দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় , তাদের দুর্বিসহ জীবন যাপনের কথা মনে হলে শীহরীত হই ,তাইতো বার বার ঘুরে ফিরে সেই সময়ের কথা মনে পরে , মনে পরে রামগোপাল ফার্মেসীর কথা , রসেন্দ্র কুমার ভট্টের কথা । রসেন্দ্র কুমার ভট্টের সাত মেয়ে ছিল এবং এর বাইরে তিনি এক মেয়েকে পালক এনেছিলেন , যার নাম ছিল খুকু , খুকুকে তিনি নিজের মেয়ের মতই আদর করতেন । বিয়ে দিয়েছিলেন আরান ভট্টাচার্য নামে কমলগঞ্জের মুন্সী বাজারের একজন শিক্ষকের নিকট । তিনি অবশ্য কুলাউড়া গার্লস স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন , সকলেই তাকে পন্ডিত স্যার বলেই জানতো ।তাকে উত্তর বাজার এলাকায় একপোয়া জমি কিনে বাসা করে দিয়েছিলেন ভট্ট বাবু ।ভট্ট বাবুর আর একটি পালক পুত্রও ছিল যার নাম ছিল মনেন্দ্র নাথ ।
আমাদের বাড়ীর পুর্বদিকে ফুটবল খেলার মাঠের দক্ষিন কোনে একটি খাই বা ডোবা ছিল , সারা বছর কচুরীপানায় আবৃত থাকতো , সেই খাই এর পুর্বে একটি বাসা ছিল , যেখানে থাকতেন শাকিলা আপা , উনার ছেলের নাম ছিল লিটন , শাকিলা আপা ছিলেন একজন অত্যান্ত্য সুন্দর মনের শিক্ষিকা একটু লম্বাটে এবং শ্যামলা কালো ,তিনি ও যতেষ্ট গাম্ভির্য্য ও আত্ব প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষকতা করতেন । প্রধান শিক্ষিকা হওয়ার যতেষ্ঠ সক্ষমতা ও সম্ভাবনা ছিল শাকিলা আপার । উনার বাসার পুর্বে রেল লাইন সংলগ্ন একটি ছিমছাম বাসা ছিল । যা হলো লুবনা আপাদের বাসা , শিপলু নামে লুবনা আপার একটি ভাই ছিল যার সাথে আমার সখ্যতা ছিল অনেক ।
শাকিলা আপাদের বাসার দক্ষিনে আর একটি বাসা ছিল যা হলো লাইলী আপা এ লিলি আপাদের বাসা ওদের বাসাটিও অনেক সুন্দর পরিপাটি ছিল ।রেল লাইনের দিকে মুখ করা একটি বারান্দা ছিল , যে বারান্দায় গোল গোল দুটি বেতের চেয়ার ছিল । দুই বোনই খুবই সুন্দরী ছিলেন । , লাইলী আপা খুউব সুন্দর করে শাড়ী পড়তেন ।উল্লেখ্য উনাদের বাবা লন্ডনে থাকতেন । উনাদের ভাইয়ের কথা মনে আছে উনার নাম ছিল শিপার ।( চলবে)
(তথ্য স্বরণ ও কৃতজ্ঞতায় – আলেয়া আপা )
৭১ এর স্মৃতি -কুলাউড়া-২
সৈয়দ শাকিল আহাদ
৭১ সালের কথা কোন ভাবেই ভোলার মত নয় , মে মাসে যখন কুলাউড়াতে পাকিস্তানী মিলিটারীরা এলো ,ঢাকা সহ সারাদেশেই পাকিস্তানী মিলিটারীরা ঢুকে পড়েছিল আগেই এবং ঢুকেই ঐ সকল এলাকার মুক্তি কামী বীর সেনাদের ধরে ধরে ক্যাম্পে এনে নির্মম ভাবে হত্যা করতো , যেহেতু যুদ্ধের বছর তখন সকলেই ছিলেন সতর্ক ,
প্রয়োজন ছাড়া কেউই তেমন কারো বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন না , তবে আমাদের কুলাউড়ার উছলাপারা নানা বাড়ীতে প্রায়শই কৌলা থেকে আসতেন আমাদের এক মামা খুউব সুন্দর চেহারা , চোখে চশমা থাকতো ,ছিম ছাম গড়ন , তার ছিল একটি সুন্দর সাইকেল ও তিন ব্যাটারীর টস লাইট , তিনি ঐ সাইকেল যোগে কুলাউড়া শহরে আসার প্রাক্কালে বটগাছের নীচ থেকেই টিং টিং শব্দ করে এসেই ডাক দিতেন , ফুফু ফুফু বলে , আমার নানা বাড়ীর সামনে অর্থাৎ কুলাউড়ার ফিল্ডের পশ্চিম দিকে বাড়িতে ঢুকার মুখেই ছিল একটি বিরাট বট গাছ ,সেই রাস্তার মুখেই যখন সাইকেলটি ঢুকতো কৌলার জুনেদ মামা তখন রিং বাজাতেন ,সাইকেলের ঐ রিংয়ের শব্দ শুনেই নানী দৌড়ে বেরুতেন , ব্যস্ত হয়ে পরতেন কৌলার মামাতো ভাইয়ের বড় ছেলে আব্দুল মুসাবিবর চৌধুরী ওরফে জুনেদ চৌধুরী কে দেখতে উনাদের মূল বাড়ী কানিহাটিতে , কৌলা উনাদের নানা বাড়ী ,জুনেদ মামা নিয়ম করেই আত্বীয় স্বজনদের খেয়াল রাখতেন , আমাদের বাড়িতে সকলের খোঁজ খবর শেষে যেতেন তাদের মাগুরাস্ত বাসায় , জুবেদ মামার বাসায় ,সময় কাটাতেন হেসাম ভাই , তাহরাম , তারাজ দের সাথে , আরো সময় কাটতো তার কুলাউড়ার অন্যান্য অনেক আত্বীয় স্বজন দের সাথে ,রামগোপাল ফার্মেসী র উপরে ঐ দোতালা বিল্ডিং এর উপরের তলায় চেয়ার ফেলে কুলাউড়ার তৎকালীন তার সমসাময়িক স্বজনদের নিয়ে আড্ডা মারতেন , তার পকেটে থাকতো বনেদী লোকদের মত ক্যাপস্টেন সিগারেটের সিগার ও ছোট্ট কাগজের বক্স ,তিনি সেই প্যাকেটটি খুলে একহাতে সিগারেট তৈরী করে মনের সুখে টান দিতেন , কি যেন মিষ্টি একটা ধুয়ার গন্ধে আসে পাশে ছড়িয়ে যেত তার উপস্থিতি।হাফ হাতা শার্ট পড়তেন হাতে একটি দামী ঘড়ি , ছোট বড় সকলের খোঁজ নিতেন ।
আমার নানী ছিলেন ভানুগাছের
করিমপুর চৌধুরী বাড়ীর কমরুল হাসান চৌধুরী ,কমরু মিয়া চৌধুরীর ছোট মেয়ে মনিরুন্নেছা খাতুন ওরফে কুটি বিবি ,
নানী সব সময় একটু গর্ব করেই বলতেন আমরা ভানু নারায়নের বংশধর ,আর তার মামাতো ভাই ছিলেন কানিহাটির এক প্রতাপ শালী “আব্দুল মান্নান চৌধুরী “উনার আর এক চাচাতো ভাই ছিলেন নাম করা ,তিনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরী ,যিনি মৌলভীবাজার মহকুমার তথা সিলেট জেলার রাজনীতির উজ্জলতরদের মধ্যে অন্যতম। তার কিছু বিশেষত্ব ছিল।যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা ।
কুলাউড়ার উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের কানিহাটিতে জন্ম নেয়া এই প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হজরত শাহ্ জালালের (রঃ) ঘনিস্ট সহযোগী হজরত শাহ্ হেলিম উদ্দিন নারলুলী (রঃ) এর বংশধর ।
ইটার রাজবংশের সাথে তার আত্মীয়তা ছিল।
তার পিতা খান বাহাদুর তজমুল আলি আমার জানা মতে প্রথম মুসলিম বাঙালি জেলা প্রশাসক। তিনি প্রথম জীবনে মৌলানা ভাসানির একজন ঘনিস্ট জন ছিলেন। তার সাথে হুসেন শহীদ সোরওয়ারদির যোগাযোগ ছিল খুবই অন্তরঙ্গ।
১৯৬২ সালে তিনি প্রথম কুলাউড়া বড়লেখা ও শ্রীমঙ্গলের একাংশ নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকার এম এন এ নির্বাচিত হন।
মৃত্যুপূর্বে সোহরোয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে পরামশ দেন যাতে মুন্তাকিম চৌধুরীকে তার দলে অন্তরভুক্ত করেন। ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু তাকে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু যোগ্য লোকদের তখন দলীয় নেতা হিসাবে নির্বাচন করছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি পুনরায় এম এন এ হিসাবে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ৪ নং সেক্টরের রাজনৈতিক সমন্বয়কের ভুমিকা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব জোনের অফিস পরিচালনা ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।
১৯৭২ সালে প্রথমে তিনি সংবিধান কমিটির গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন । পরে জাপান ও জার্মানির রাষ্ট্রদুত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী কালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। তিনি বহুদিন সৌদি আরব ও অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী জীবন যাপন করেন ।তার ঘনিস্ট রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন জনাব আজিজুর রহমান একসময় মৌলভী বাজারের জেলা পরিষদ প্রশাসক ছিলেন ,
আরো ছিলেন নবাব সফদর আলী খান রাজা সাহেব ,জয়নাল আবেদিন, লতিফ খান, আব্দুল জব্বার, নওয়াব আলী সরওয়ার খান চুন্নু , জুবেদ চৌধুরি, মুকিমুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ জামালুদ্দিন সহ আরো অনেকেই ..
বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই ভুলতে বসেছে তাদেরকে ইদানিং , কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে কে এই এই ব্যারিষটার মুন্তাকিম চৌধুরী ?
অথচ সকলেরই জানা উচিত তার কথা , জুবেদ চৌধুরীর কথা, এম. পি জব্বার মামার কথা , জয়নাল আবেদিনের কথা, সৈয়দ জামালের কথা,আকমল হোসেনের কথা , আলাউদ্দিন চেয়ারম্যানের কথা, রাজা সাহেবের কথা , আব্দুল গফুরের কথা , নাগেন্দ্র মালাকারের কথা, অনুপম কান্তির কথা , রসন্দ্র ভট্টের কথা , মুক্তিযুদ্ধে যাদের বলিষ্ঠ অবদানের কথা , যোগ্য নেতৃত্বর কথা , যাই হোক বলছিলাম তার ভাতিজা জুনেদ চৌধুরীর কথা যিনি প্রায়শই সকালে অথবা বিকালে তার ফুপুরবাড়ি উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ীতে আসতেন এবং ছোটবড় সকলের খোঁজ খবর নিতেন সখ্যতা ছিল বড় মামা আমির আলী ও ছোট মামা মুনির আলমের সাথে , আমাদের নানা বাড়ীর সামনের ঘরটি ফটিক বা বৈঠক খানা , ঐ ফটিকের সামনে ছিল শতবর্ষী বিরাট দিঘী আকৃতির একটি পুকুর যা এখন একজন বিতর্কিত জনপ্রতিনিধির লোলুপ কুদৃষ্টির ফলে পনবিহীন জাল দলিল ও জালিয়াতির মাধ্যমে একজন বিপথগামী বংশধরের সহায়তায় বিক্রিত জমি দেখিয়ে প্রশাসন ও স্থানীয় জনগনের চোখের সামনেই বিলীন হওয়ার পথে ‘এজমালী ‘ঐ পুকুরটি যে পুকুরটির স্বচ্ছ পানি পান করেছেন মুক্তি যোদ্ধারা , তা ছাড়াও যে কোন ফুটবল খেলা হলেই ঐ পুকুরে গোসল করতে দেখেছি , স্থানীয় ও আশে পাশের দুর দুরান্তের অনেক খেলোয়ার দের ,ঐ সময় অনেক বিশাল ব্যক্তিত্ব রাও ঐ পুকুরের পানি পান করেছেন তা পূর্বাবস্তায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং এই ব্যাপারে কুলাউড়া বাসীর সকলের সহায়তা চাচ্ছি ।
বলছিলাম জুনেদ মামাদের কথা উনারা ছিলেন তিন ভাই , জুনেদ মামা , জুবেদ মামা ও জিন বিজ্ঞানী আব্দুল মুসাকাব্বির চৌধুরী বা আবেদ মামা । জুবেদ মামা বা আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী ছিলেন কুলাউড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠকদের অন্যতম , মুক্তি যোদ্ধাদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষন কালে তিনি ভারতের কৈলাশটিলা ও ধর্মনগরে অবস্তান করে , রাজা সাহেব , জব্বার মামা , সৈয়দ জামালসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, সংগঠিত করতেন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ,কিভাবে কুলাউড়াকে শত্রু মুক্ত করা যায় , তার পরিকল্পনা করতেন ,যুদ্ধের সময় সংরামী একজন অগ্রনায়ক ছিলেন এই মুকতাদির চৌধুরী বা জুবেদ মামা , তার একটি ল্যানডরোভার জীপ ছিল , আর একটি জীপ পোস্ট অফিসের গেট পার হয়ে ,দক্ষিন বাজার মসজিদের প্রবেশপথের আগখানেই বহুবছর পরিত্যাক্ত অবস্তায় পরে ছিল । ঐ জীপে চড়ে আমরা ছোটবেলায় আমি , সাফি ,তহশীলদার সাহেবের ছেলে , (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ), রহমান ( বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী )ও ডাকবাংলোর লিটন ( বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ) উত্তর বাজারের বুলন , মতিন সহ অনেকেই বি এইচ স্কুলে পড়ার সময় , আসা যাওয়ার পথে খেলতাম ,বন্ধ জীপের স্টিয়ারীং ঘুরিয়ে গাড়ী চালাতাম । আহা কি দারুন স্বরনীয় ছিল ৭১ এর সেই ছোট বেলার দিন সহ পরবর্তী সময়ের স্মৃতিময় গুলির কথা । (চলবে )
“৭১ এর স্মৃতি – ১৯ ( মনসুর)
সৈয়দ শাকিল আহাদ ।
অনেক কথাই মনে হচ্ছে লিখি
কিন্তু কোনটা রেখে কোনটা লিখবো ভাবছি , তবে মুক্তিযুদধ চলাকালে উছলাপাড়াতে আমার নানা বাড়ির পশ্চিমের দেওয়াড়ে উঠলেই দেখা যেত যে গ্রাম তা হচ্ছে মনুর বা মনসুর , এই গ্রামের দক্ষিন পাশে ঈদগাহ ও গোরস্তান , উত্তর পাশে কাদিপুর যাবার রাস্তা মাঝে গাং বা খাল বা মরা গুগালী গাং , বর্ষার সময় পানি থাকতো ,শীতকালে বা শুকনা মওসুমে আইলের উপর দিয়ে হেঁটেই আসা যাওয়া করা যেতো ।এই খালটি বা গাংটি এখন মৃত এর কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই তবুও মরা গুগালী গাং এর কথা মনে আছে তাই লিখছি ।
খান সাহেব বাড়ীর পশ্চিমে বেশ কয়েকটি বাড়ি ছিল “রাইয়ত বাড়ী “, এই খান বাহাদুর আমজদ আলী সাহেব ছিলেন বৃটিশ আমলে আই জিপি ( ইন্সপেক্টর জেনারেল ওব পোস্টেজ ) বাড়ীর পশ্চিমে অনেকের বাড়ী ছিল যারা এই মুল বাড়ীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল , নানু সহ ঐ বাড়িতে তেমন একটা যাওয়া আসা হতো না বরং ওরা আসতো আমাদের বাড়িতে এবং তিনি আমাদেরকে তেমন একটা যোগাযোগ করতে ও দিতেন না তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মেরা বর্তমানে বিত্তশালী ,অসীম ক্ষমতাধর ও সমাজে প্রতাবশালী ।
ঐ বাড়ীগুলোর পরেই ছিল ধানী জমি , এবং তার পর ধানী জমি পেরুলেই গ্রাম ,
বাড়ির পশ্চিমের গ্রামগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে মনুর বা মনসুর ,
মনসুরের আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো মনুর অন্যটা বাদে মনুর , মনুর বা মনসুর এর পর যে গ্রাম গুলো আসে সেগুলো হচ্ছে ,আমতৈল , ভাগমতপুর , সাদেকপুর ,মৈন্তাম, গুপ্তগ্রাম ,তিলকপুর,কিয়াতলা,
হাসিমপুর , কাদিপুর , কৌলারশী,গোবিন্দপুর,ফরিদপুর,রফিনগর,গোপীনাথপুর ,ছকাপন,তিলকপুর,
হোসেনপুর ,,লক্ষীপুর ,উছাইল , নিংগিরাই,কাকিচার ,নয়াগাও,
অলিপুর , সুলতানপুর ,চুনঘর ,চাতলগাওয়ের একাংশ ইত্যাদি মিলে হয়তো আরও দুএকটি গ্রাম রয়েছে যা মিলে হলো কাদিপুর ইউনিয়ন।
এই কাদিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অনেক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন , যাদের বীরত্ব গাথা আমাদের ৭১ সালে ঘটে যাওয়া মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসকে সম্বৃদ্ধশালী করে রেখেছে , তেমনি একজনের কথা মনে পড়ছে ,
তিনি হলেন ,মনসুর গ্রামের ছমসুদ্দিনের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নং হচ্ছে ০৫৪০৪০২৮২ । পাকিস্তানী আর্মিরা কুলাউড়াতে এসে ক্যাম্প করার পর তিনি অন্যান্যদের সাথে গিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে এসে কর্মধা ,শিলুয়া , ফুলতলা প্রভৃতি স্থানে করেন সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহন নিয়েছিলেন ।
তা ছাড়া বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে ,আমতৈল গ্রামের মোঃ খালেদুর রব , তার পিতা ছিলেন মোঃ আব্দুর রব তিনি অত্যানত সাহসীকতার সাথে যুদ্ধের সময় তবিশেষ ভুমিকা পালন করেন । তাদের কুলাউড়ার বাসায় বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্তান করতো এবং তিনি তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন । যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীনের পর তাদের বাসা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত অস্র থানায় জমা দেওয়া হয় ।আমতৈল জন্ম নেওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদুর রবের ভাই এম এম শাহীন , সাংবাদিকতা ও পত্রিকা ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কুলাউড়ার রাজনীতির সাথে জড়িত হন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন ।প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা দের তালিকায় খালেদুর রবের নাম্বার হচ্ছে ০৫০৪০৪০৩১৬ ।
কাদিপুর ইউনিয়নের কৌলারশী বা মিনার মহল গ্রামে জন্ম নেওয়া আর এক বীর মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছেন আজির উদ্দিন । তার কথা কেউ মনে করবে কিনা জানিনা তবে , প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তার নং ঃ- ৫০৪০৪০৩৭১ বিভিন্ন কারনে এই আলোচনায় তার নাম এসে যায় , তার পিতার নাম আমির উদ্দিন ,তার ভাষ্যমতে ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর থেকেই তারা বুঝতে পারেন পাক শোষকদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সকলকে সংগ্রামে নামতে হবে এবং তখন থেকেই প্রস্তুতি নেন , মোজাহিদ সদস্য ছিলেন , শেরপুরের প্রতিরোধ ভাঙ্গার পর তার ভাই কবির উদ্দিন কে নিয়ে ভারতে চলে যান , ট্রেনিং নেন , ৪ নং সেক্টর এর অধীনে থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে যুক্ত থেকে সাহসীকতার সাথে সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন ।দুই ভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করার কারনে
কয়েক জন রাজাকারোর প্ররোচনায় তাদের বাবা আমির উদ্দিনকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানী মিলিটারীরা নির্মম ভাবে হত্যা করে ।
আমাদের উছলা পাড খান সাহেব বাড়ীর পশ্চিমের কাদিপুর ইউনিয়নের
মনুর বা মনসুর এবং বাদে মনুর বা বাদে মনসুর
গ্রামের ইতিহাস ঐতিয্য কুলাউড়ার ইতিহাসকে সম্বৃদ্ধশালী করে রেখেছে ।
যে ব্যক্তিটির নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম তিনি হচ্ছেন সিলেট অন্চলের কিংব্দন্তী “মামন্দ মনসুর” বা দেওয়ান মোহাম্মদ মনসুর , তিনি ছিলেন অত্যান্ত প্রতাপশালি জমিদার , তার পিতা দেওয়ান ইউসুফ ছিলেন ৮ নং তালুকের অধিকর্তা বা মালিক ।
তার নামঅনুসারে ইউসুফপুর বা ইছবপুর গ্রামের নামকরন করা হয়েছিল এই গ্রামটি বর্তমানে মনসুর গ্রামের সাথে একত্রিত হয়ে আছে ।
মামন্দ মনসুরের প্রপিতামহ মোহাম্মদ আনছফ বা মামন্দ আনছফ অত্যান্ত সাহসী, বলিষ্ঠ ও দুর্দান্ত দাপটি এক মহান পুরুষ ছিলেন ।
প্রবাদ ও জনশ্রুতি আছে তিনি সামান্য একটি ছুরি হাতে নিয়ে হিংস্র বাঘের উপর সরাসরি ঝাপিয়ে পড়তেন , লড়াই করতেন বাঘের সাথে , হার মানতো বনের হিংস্র বাঘ ,মামন্দ আনছফ নিজের জমিদারীর সীমানা নির্ধারণকল্পে উত্তর সীমানায় একটি খাল বা পরিখা খনন করান কুলাউড়া অন্চলে তখন এত জনবসতির নাম গন্ধ ছিল না , পাহাড় , জংগলে ঘেরা ছিল , বাঘ ভাল্লুক সহ বন্যপ্রাণীর আনাগোনা ছিল নিয়মিত ।তাদের পুর্বপুরুষ ছিলেন বাবা শাহজালাল (রঃ) এর অন্যতম সাথী হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী মামন্দ মনসুর হলেন তার চৌদ্দতম পুরুষ ।
ছোটবেলায় কুলাউড়ার প্রবাদ শুনেছি
লোকমুখে ঃ-
বেটা কইলে মামন্দ মনসুর
আর যত পুয়া ,
হাওর কইলে হাকালুকি,
আর যত কুয়া ।
দেওয়ান মোহাম্মদ মনসুর বা মামন্দ মনসুর সম্পর্কে , তার জীবনীতে ঘটে যাওয়া কৃতকর্মের অনেক গল্প , অজানা কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে , ও বইয়ে প্রচলিত আছে ।
তার পিতা মামন্দ ইউসুফের অসুস্ততার জন্য অল্প বয়সেই তিনি জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান ।
তিনি পৃথ্বীমপাশার জমিদার গৌছ আলী খাঁর সমসাময়িক ছিলেন ।
ছোট বেলা থেকেই একটু রাগী ও জেদী স্বভাবের
ছিলেন কিন্তু জ্ঞানী এ পন্ডিত দের সম্মান করতেন । কাদিপুর ইউনিয়নের মনসুর গ্রামের বাড়ি ছাড়াও মামন্দ মনসুরের আর একটি বাড়ী ছিল কর্মধা ইউনিয়নের মনসুরপুর গ্রামে ।
উভয় গ্রামের উভয় বাড়ীই একই রকম ভাবে নয় খন্ডে বিভক্ত , কর্মধার মনসুরপুর গ্রামের বাড়ীটি “ন-খন্ডী” বাড়ী নামে পরিচিত আর কাদিপুরের বাড়িটি “মান-মনসুরের বাড়ী “ নামে পরিচিত ।
ঐ বাড়ীগুলো মাটির দেয়াল দিয়ে নয় ভাগে ভাগ করা ছিল ।মামন্দ মনসুরের কোন ছেলে সন্তান ছিল না ,
তার তিন মেয়ে ছিল যথাক্রমে নজিফা বানু , সিতারা বানু ও খতিজা বানু ।
বড় মেয়ে নজিফা বানুর বিয়ে হয়েছিল সিলেটের মজুমদারীর আহমেদ আলী মজমাদারের সাথে ।আহমেদ আলী মজমাদারের পুর্বপুরুষ ছিলেন ভারতের কৈলাশশহরের জমিদার ।
দ্বিতীয় মেয়ে সিতারা বানুর বিয়ে হয়েছিল কুলাউড়ার কৌলা গ্রামের জমিদার আব্দুল আলীর সাথে , তৃতীয় মেয়ে খতিজা বানু অবিবাহিত ছিলেন এবং বাবার বাড়ীতেই মারা যান ।
উল্লেখ্য মামন্দ মনসুরের বড় মেয়ে নফিজা বানুর দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে হয় সিলেটের মজুমদারীর মোহাম্মদ হাদী বখত মজমাদারের সাথে এবং দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয় সিলেট শহরের কুমারপারা ঝরনার পাড়ের আমার পুর্বপুরুষ সৈয়দ আব্দুল করিমের সাথে ।এই দ্বিতীয় মেয়ের অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন আশরাফ আলী মজুমদার , তার নাম অনুসারে
এই কাদিপুর ইউনিয়ন ভুক্ত মনসুর গ্রামের মুলবাড়ীর সামনে “ আশরাফিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা “ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ।
আমাদের বাড়ির পুর্বপাশ্বে ছিলেন এই মান মনসুরের অন্যতম বংশধর তপন ভাই , তপন ভাইয়ের ছোট বোন বীনার সাথে সম্প্রতি ফেসবুকের কল্যানে যোগাযোগ , তার দেয়া তথ্য মতে
৩৬০ আউলিয়া এর একজন হলেন সুদূর ইয়ামেন থেকে আসা শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী উনি প্রথম পূর্ব পুরুষ উনার ছেলে তাজউদ্দীন কুরেশি প্রথম মনসুর গ্রামে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বিয়ে করে বসবাস শুরু করেন উনার ছেলে মান মনসুর ۔۔ মান মনসুর এর ভাতিজি উনার চাচাতো বোনের বিশাল সম্পত্তি উনার সম্পত্তির সাথে সাথে পান উনার কোলে থাকা সন্তান আদিল চৌধুরী ( মান মনসুর এর যে মেয়ের বিয়ে হয়নি উনার ভাগ এর অংশ ) আদিল চৌধুরী এর মা ব্রিটিশ আমলে জমিদারি তালুক নিলাম হয় যথাক্রমে আট ও নয় তখন ওদের কাছে প্রজা হয়ে থাকতে হবে বিধায় রাতারাতি ছেলে আদিল চৌধুরী কে নিয়ে ঘাগটিয়া তে বাড়ি বানিয়ে পাড়ি জমান যার জন্য এই বাড়ি কে হাজমা বাড়ি ও বলতো লোকেরা এবং খাজনা দিতে হতো যারা তপন ভাইদের প্রজা বা রাইয়ত । এদেরকে সরকার বাড়ি ও বলতো আমরা ও ছোটবেলাতে শুনসি সরকার ও জাইরাম বলতে আদিল চৌধুরী এর দুই ছেলে সন্তান নাদির চৌধুরী ও হাশিম চৌধুরী হাশিম চৌধুরীর ছেলে সন্তান আমিনুজ্জামান চৌধুরী অর্থাৎ তপন ভাই ও বীনার আব্বার দাদা উনার তিন সন্তান দুই ছেলে মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী ও তপন ভাইয়ের দাদা কামরুজ্জামান চৌধুরী আর তাদের দাদি দাদাদের বোন ,উনার বিয়ে হয় পাথাড়ি বড়লেখা তপন ভাইয়ের আব্বা রা এক ভাই এক বোন , তার বড়ো দাদার চার ছেলে এক মেয়ে বড় জন মারা গেছেন পুলিশ হেডকোয়ার্টার এ জব করতেন ,তাদের মেজোচাচা রেলওয়ে তে জব করতেন সেজো চাচা স্কটল্যান্ড এ আছেন আর ছোট চাচা মিশিগান এ আছেন তপন ভাইরা সাত ভাই বোন
,সবার বড় ভাই শরিফুজ্জামান চৌধুরী তপন ,মেজভাই সেলিমুজ্জামান চৌধুরী ছোট ভাই অমরুজ্জামান চৌধুরী নবাব
আলী আমজাদ এর নানী আদিল চৌধুরীর মেয়ে নাম সৈয়দা অমরুন্নেসা আর এক মেয়ে কৌলা বড়ো বাড়িতে বিয়ে হইসে আতিয়া চৌধুরী দের পূর্ব জেনারেশন শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এর ফুপু আতিয়া চৌধুরী ও
নাদেল ভাইয়ের এর বাবা শামসুল আলম চৌধুরী এবং ওই বাড়ি আতিয়া বেগমের বাবা সৈয়দ বদরুল হোসাইন চৌধুরী উনার বাবা বশিরুল হোসেইন এর নামেই “বি এইচ প্রাইমারী স্কুল “নামে দক্ষিণ বাজারে একটি স্কুল আছে । আর উনার দেয়া স্কুল ঘাগটিয়ার সম্পত্তি মৌরসী সম্পত্তি
নাজিফা বানুর দেড়শো কিয়ার বা এক হাজার একর বিঘা টি গার্ডেনটি তপন ভাইদের সম্পত্তি যা ইস্পাহানি গাজীপুর এর সাথে এবং এই সম্পত্তি দখল করে ফল্স কেইস এ তপন ভায়েরা জিতেছিল কিন্তু লোকাল মাস্তান বাহিনী দিয়ে টাকা খাইয়ে তারা দখলে নিয়ে নিয়েছে ۔۔
তপন ভাইয়ের বড় চাচা মরহুম নাজিরুজ্জামান চৌধুরী
মেজো চাচা নাজিমুজ্জামান চৌধুরী
সেজো চাচা বদরুজামান চৌধুরী
ছোট চাচা ফখরুজ্জামান চৌধুরী ফকু ।
এবার কুলাউড়ার সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়ার
প্রয়োজন অনুভব করছি ,
বর্তমান কুলাউড়া উপজেলার উত্তরে ফেঞ্চুগঞ্জ ও জুড়ি উপজেলা, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে রাজনগর উপজেলা।
পাহাড়, টিলা সমতল ও জলাভূমির সমন্বয়ে কুলাউড়ার ভূমি গঠিত। এখানকার পাহাড়, টিলা গুলো বনজ সম্পদে ভরপুর। তার মধ্যে অন্যতম চা বাগান। বাংলাদেশের মোট ১৫৩টি চা বাগানের মধ্যে, কুলাউড়া উপজেলায় ১৯ টি চা বাগান রয়েছে। কুলাউড়া উপজেলায় মোট ১৭টি ইউনিয়ন ছিল। ২০০৪ সালের ২৬ আগষ্ট, ৪টি ইউনিয়ন জায়ফরনগর, গোয়ালবাড়ী, সাগরনাল ও ফুলতলাকে আলাদা করে জুড়ী উপজেলা গঠন করা হয়।বর্তমানে ১৩ টি ইউনিয়ন রয়েছে কুলাউড়াতে, সেগুলি হচ্ছে ঃ-
১)বরমচাল ইউনিয়ন
২)ভূকশিমইল ইউনিয়ন
৩)জয়চন্ডী ইউনিয়ন
৪)ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন
৫)কাদিপুর ইউনিয়ন
৬)কুলাউড়া ইউনিয়ন
৭)রাউৎগাঁও ইউনিয়ন
৮)টিলাগাঁও ইউনিয়ন
৯)শরীফপুর ইউনিয়ন
১০)পৃথিমপাশা ইউনিয়ন
১১)কর্মধা ইউনিয়ন
১২)ভাটেরা ইউনিয়ন
১৩)হাজীপুর ইউনিয়ন
কুলাউড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সর্ম্পকে প্রাচীনকালের তাম্রলিপিতে কিছু তথ্য পাওয়া যায় বলে জানা যায়।
কুশিয়ারা নদীর দক্ষিন তীরে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত,দ্বাদশ শতাব্দিতে “ইটা” নামে একটি সামন্ত রাজ্য ছিল।
“নিধিপতি শর্মা” নামে জনৈক ব্রাক্ষণ ইটা রাজ্যের রাজা ছিলেন। এক কালে এই রাজ্য
“ইটা মনুকুল” প্রদেশ নামেও অভহিত হতো।
প্রাচীন ইটারাজ্যের রাজধানী ছিল ‘ভূমিউড়া’ গ্রাম।
প্রাচীন নিদর্শন ভাটেরার তাম্র ফলকদ্বয়ের কুলাউড়া নামের কোন উল্লেখ নেই। তবে প্রাচীন একটি শ্লোকাংশে ‘‘লংলাইস্য কুলাউড়া, ইটাস্য নন্দিউড়া’’ কথাটির উল্লেখ রয়েছে।
এ থেকে বোঝা যায়, পরগণা ভিত্তিক শাসনামলে কুলাউড়া নামটি ছিল এবং ইটা পরগণা নন্দিউড়ার ন্যায়, লংলা পরগণার কুলাউড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান।
“হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী” নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মনসুর গ্রামের প্রখ্যাত দেওয়ান, মোহাম্মদ মুনসুর বা “মামন্দ মনসুরের” পিতামহ মামন্দ মনোহরের ভাই “মামন্দ কুলাঅর “ কুমার থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।
মামন্দ মনোহর ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে নিজ জমিদারির পূর্বাংশে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করে নাম রাখেন “কুলঅরার বাজার’’। কালক্রমে “কুলঅরার বাজার থেকে কুলাউড়া’’নামকরণ করা হয়েছে।কুলাউড়া নামকরনের আরো কিছু জনশ্রুতি রয়েছে তবে সঠিক তথ্যের অভাবে নামকরনের সুত্রের পক্ষে কোন গবেষকই অতীতে তোমন জোড়ালো দাবী রাখতে পারেন নাই ।
সিলেট বিভাগের অন্যান্য উপজেলোর চাইতে কুলাউড়া অনেক অগ্রসর ও উন্নত সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। অনেক কৃতি সন্তানের জন্ম এই কুলাউড়ায় যাদের দুই এক জনের কথা না বললেই নয় ,
সিলেট অঞ্চলের প্রথম দৈনিক পত্রিকা ‘বলাকা’র সম্পাদক শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি এই কুলাউড়ায় আরেক প্রখ্যাত সাংবাদিক- শ্রী গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি কুলাউড়া সদরে ।
প্রাচীনকালে কুলাউড়ার বিভিন্ন এলাকা জাহাজ ও যুদ্ধাস্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল।
সতের শতকে কুলাউড়ার
“জনার্দ্ধন কর্মকারের” খ্যাতি ও সুনাম ছিল সমগ্র উপমহাদেশব্যাপি।
জনার্দ্ধন কর্মকার ঢাকার
“কালে জমজ” (সদরঘাটের কামান বলে খ্যাত) ও “বিবি মরিয়ম “নামের লোহার দুটি কামান তৈরী করেন এবং এর ফলে কামান তৈরীর কারিগর হিসাবে ইতিহাসের খাতায় তার নাম অংকিত হয়ে আছে ,
যিনি কুলাউড়ার সন্তান । তার কোন বংশধরেরা এখন জীবিত আছেন কিনা বা থেকে থাকলে কোথায় আছেন , কেমন আছেন তা আমাদের অজানা , হয়তো এই লেখাটি পড়ে কেউ “জনার্দ্ধন কর্মকার” এর বংশধর দের তথ্য দিয়ে আমাদের কে সহায়তা করবেন ।
(চলবে
© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত -২০২৫, আমাদের প্রকাশিত সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ।